ভারতের ইতিহাস
ভারতবর্ষে প্রতিবাদী ধর্মসমূহের উত্থান
খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমণ ও পরিব্রাজকদের উদ্ভব
খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ের ভারতের ইতিহাসে দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন অনুসন্ধান ও সংস্কার দেখা যায়। দর্শনের ক্ষেত্রে এই নতুন অনুসন্ধানস্পৃহা বৈদিক যুগের শেষ দিকে উপনিষদে প্রতিফলিত হয়েছিল। উপনিষদ বৈদিক ধর্ম এবং জীবণযাপন-পদ্ধতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে, তত্ত্বগত দিক থেকে তাদের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সেখানে নবীন প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছিল। প্রথম দিকের উপনিষদ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবমুক্ত নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তীকালে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা খুব বড় হয়ে দেখা যায়। পরিব্রাজক এবং শ্রমণ নামে পরিচিত একদল সন্ন্যাসী এই নতুন চিন্তার অগ্রদূত ছিলেন। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগ সূত্রযুগে চতুরাশ্রমের প্রথা ছিল। এই চতুরাশ্রমের শেষ দুটি আশ্রমে, অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস পর্বে উচ্চতর বর্ণের লোকেরা অভ্যস্ত পরিবার ও সমাজবন্ধন এবং গতানুগতিক চিন্তার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তায় মগ্ন হয়। বাসামের মতে তাই তখন ভারতের বৌদ্ধিক জীবনে বৃষ্টির পর অরণ্যের মত সজীব প্রাণের সমারােহ দেখা গিয়েছিল।

শ্রমণদের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতা ও শাসকদের সমর্থনলাভ
শ্রমণেরা সংসার ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তারা বেদের অধিকার ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করেছিলেন। সেসময় সমাজে পশুবলির মাধ্যমে যজ্ঞানুষ্ঠান খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাকে তারা অনুমােদন করেননি। ব্রাহ্মণরা বেদকে চরম সত্যের একমাত্র বাহক হিসেবে দাবি করতেন, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা অধিকাংশই অব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের দাবিও অগ্রাহ্য করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণভেদ ব্যবস্থাও তারা মানেন নি। দেবদেবীর অস্তিত্বে তারা অবিশ্বাসী ছিলেন। তাই মানুষের জীবনে স্বর্গীয় দাক্ষিণ্যের উপযােগিতাও তারা অস্বীকার করেছিলেন। সমাজ এবং প্রকৃতিতে মানুষের স্থান কোথায়, এই প্রশ্নের মুখােমুখি হয়ে তারা সৎ আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের মতে, একমাত্র এর দ্বারাই মানুষ সংসার ও কর্মের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। অহিংসা এই সৎ আচরণের অন্তর্গত।

ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে তখন ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব ছিল, এবং ক্ষমতা কেবল রাজার কাছে না থেকে অনেকটাই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে ছিল। অনেক শাসকই তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং নিজেদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ চাইতেন। শ্রমণেরা কোন সামাজিক কর্মসূচী ঘােষণা করেননি। কিন্তু তাদের ভাবধারা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ তাদেরকে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের সম্ভাব্য মিত্র করে তুলেছিল। এই শাসকগণ তখন ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষাপুষ্ট জাতি ও বর্ণভিত্তিক অনৈক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে কেন্দ্রীকরণের নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই শ্রমণদের ভূমিকাও একই রকম ছিল। তারা তাদের ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে কয়েকটি সমভাবাপন্ন গােষ্ঠী গঠন করেছিলেন। এভাবে ধর্মে ও রাজনীতিতে সামান্তরাল দুটি ধারা, পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল।
প্রতিবাদী ধর্মসমূহের উত্থানের পেছনে সমাজ-অর্থনৈতিক বাস্তবতা
খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যের এই নতুন বৌদ্ধিক বিপ্লবের একটি বাস্তব পটভূমি ছিল। ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ তখন উপজাতি-জীবন অতিক্রম করে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেছিল। অর্থনীতিতে তখন পশুপালন পর্বের পর কৃষিভিত্তিক জীবন শুরু হয়েছিল। অনেকগুলো নগর গড়ে ওঠায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীরা তখন বৈদিক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মধ্যদেশ অতিক্রম করে পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করে। এই প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রধানত অব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উদ্ভব হয়।
এই প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন আদিম ধর্ম বিশ্বাস সমন্বিত, জটিল যজ্ঞকেন্দ্রিক, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এবং বর্ণবৈষম্য-নির্ভর বৈদিক ধর্ম ও জীবনযাপন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছিল। তবে বাস্তব দিক থেকে এদের আন্দোলনে মুল বিষয় ছিল বৈদিক যজ্ঞ-প্রথার বিরোধিতা। এই যজ্ঞ সমাজের দই উচ্চবর্ণ, ব্রহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধকে তাদের জীবনের একমাত্র অঙ্গীকার বলে মনে করতেন। ব্রাহ্মণদের কাছে এই যজ্ঞ ছিল জীবনের প্রধান কর্তব্য এবং জীবিকার্জনের মুখ্য উপায়। সমাজের অন্য দুই শ্রেণী, বৈশ্য ও শূদ্রদের কাজ ছিল উদ্বৃত্ত উৎপাদন করা।
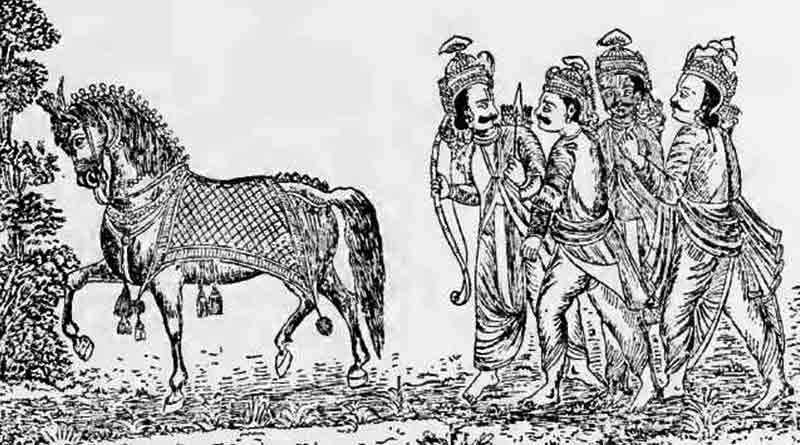
যে উদ্বৃত্ত সম্পদ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা প্রথম দিকে উপজাতির এবং শেষের দিকে নিজেদের কল্যাণের জন্য তাদের জন্মগত অধিকার বলে নিয়ে নিতেন। এই বৈদিক যজ্ঞ, পশুপালনের যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, কারণ সেই যুগে গরুর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, বরং সমষ্টির মালিকানা ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজব্যবস্থার সাথে যজ্ঞ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলনা। এছাড়া ক্রমবর্ধমান পশহত্যা, যুগপৎ উৎপাদন ও উৎপাদকের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বৈশ্যদের কাছ থেকে ক্রমাগত গোসম্পদ নিয়ে যাওয়া হত, অথচ বিনিময়ে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হত না। এভাবে সম্পদ হারানাের ফলে বৈশ্যদের বাণিজ্য-সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়েছিল। অন্যদিকে মহাভারতে থেকে সেইসময় অবিরাম যুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এই যুদ্ধের ফলেও তাদের বাণিজ্য বিপন্ন হবার কথা। তাই প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়গুলো এই যজ্ঞের বিরোধিতা করেছিলেন।
প্রতিবাদী ধর্মসমূহের ধারাগুলো
বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়ার দুটি ধারা ছিল। একটি ধারা ছিল নাস্তিক্যবাদী। এই ধারাটি বৈদিক দেবদেবী এবং ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রয়ােজনীয়তা সরাসরি অস্বীকার করেছিল। অপর ধারাটি ছিল আস্তিক্যবাদী ও একেশ্বরবাদী। এই ধারায় ব্যক্তিগত দেবতার সন্তোষ বিধানের জন্য, ভক্তিকেই একমাত্র উপায় বলে মনে করা হত। এই দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব এবং বৈষ্ণব, এই চারটি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এরা সবাই আধ্যাত্মিক সত্যের উৎস্য হিসেবে বেদের অব্যর্থতার এবং মুক্তির উপায় হিসাবে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম- বৈদিক দেবতা শিব এবং বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাই এদের সংস্কারবাদী বলা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধমসমূহ বৈদিক দেবদেবীকে অস্বীকার করেছিল, তাই এদের প্রচলিত ধর্মমত বিরােধী বলা হয়।
আজিবিক ধর্ম
বিরােধী ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে জৈন এবং বৌদ্ধরাই প্রধান। কিন্তু তাদের কিছুকাল আগে একইরকম আর একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এরা আজিবিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে অজিবিক সম্প্রদায় প্রাচীনতম। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গােশাল। তার জীবনকাহিনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সামান্য একটি পরিবারে তার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি মহাবীরের বন্ধু ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর কিছুকাল আগে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ অব্দে তার মৃত্যু হয়েছিল।
আজিবিকদের ধর্ম পুরােপুরি নাস্তিক্যবাদী। তারা কঠোর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করতেন। মানুষ সৎকাজ অথবা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই মতবাদে তারা আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা মনে করতেন যে সমগ্র বিশ্ব, এমনকি এর সামান্যতম বস্তু পর্যন্ত নিয়তির দ্বারা পূর্ব থেকেই নিদিষ্ট। তাই এক দিক থেকে মানুষ খুবই অসহায়। সব মানুষকেই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, তার আগে চুরাশি লক্ষ জন্ম অতিক্রম করতে হবে। এ বিষয়ে জ্ঞানী ও মুর্খের মধ্যে কোন ভেদ নেই। তারা আরও মনে করতেন যে তাদের কঠোর তপশ্চর্যা নিয়তির অভিপ্রেত। অজিবিকদের কোন ধর্মগ্ৰহ পাওয়া যায়নি। তাই এ সম্পকে যাকিছু ধারণা, তা তাদের বিরোধীপক্ষীয় বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য থেকে সংগৃহীত।

প্রথম দিকে আজিবিকদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল অবন্তী ও তার মধ্যবর্তী অঞ্চল (তদকালীন অবন্তী বর্তমান ভারতের মধ্য প্রদেশ রাজ্যে)। পরে মৌর্য সম্রাট অশােক এবং তার পৌত্র দশরথ এই ধর্মের পৃষ্ঠপােষকতা করেন। অশােকের লেখতে আজিবিকদের জন্য মূল্যবান দানের উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত মিলিন্দ পঞহো গ্রন্থেও আজিবিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বানভট্টের হর্ষচরিতেও তাদের উল্লেখ আছে।
ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমালােচনার জন্য আজিবিকগণ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গােশালের শ্রেণীকাঠামাে-সমালােচনা এবং কর্মফলবাদের নতুন ব্যাখ্যা নিম্নশ্রেণীর মানুষ এবং সদ্যধনীদের মনােযোগ আকর্ষণ করেছিল। এই ধর্মের আপাত সারল্যও একে জনপ্রিয় করেছিল। এমনও অনুমান করা হয় যে প্রথম দিকে হয়ত বৌদ্ধদের তুলনায় আজিবিকদের সংখ্যা বেশি ছিল। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে এদের অনুচরদের মধ্যে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যরাও ছিল।
সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈনরা, বিশেষভাবে বৌদ্ধরা, আজিবিকদের বিরােধিতা করেছিল। প্রথম দিকে এই বিরােধ তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে অনেক সময় তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই যুদ্ধে অজিবিকরা পরাজিত হয় ও বৌদ্ধরা জয়ী হয়। এদের পরাজয়ের কারণ হল তারা ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রত্যাখ্যান করলেও তার পরিবর্তে তৎকালীন মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য কোন স্পষ্ট ও নিশ্চিত মতবাদ প্রচার করতে পারেনি। সর্বব্যাপী অদৃষ্টবাদ অন্য সব সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছিল। এছাড়া তারা হিন্দুধর্মের অনেক কিছুকে আত্মস্থ করে নেয়। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ১৪শ শতকে নবজাগ্রত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই ধর্ম বিলীন হয়ে গিয়েছিল।
জৈন ধর্ম
জৈনদর্শন ভারতের প্রাচীনতম অসনাতন নাস্তিক্য ধর্মদর্শনের অন্যতম। ‘জিন’ শব্দ থেকে জৈন শব্দের উৎপত্তি। ‘জিন’ অর্থ বিজয়ী। জৈন মতে, যিনি ষড়রিপুকে জয় করেছেন, যথার্থ সাধনার বলে রাগ, দ্বেষ, কামনা বাসনা জয় করে যারা মুক্তি বা মোক্ষলাভ করেছেন তারাই জিন। জৈন ঐতিহ্যে এরকম চব্বিশজন মুক্ত পুরুষের কথা উল্লেখ করা হয়, যাদের তীর্থঙ্কর বলা হয়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ হলেন বর্ধমান বা মহাবীর। মহাবীর গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।
জৈনদর্শনের মূল কথা হলো, সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগতকে যেভাবে জানি তাই সত্য ও যথার্থ। জগতে বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে কোনো এক বা অদ্বিতীয় পরমসত্তার কল্পনা করা নিরর্থক। এই বস্তুগুলো জীব এবং অজীব নামে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। দেহ যেমনই হোক, প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর মধ্যেই জীব বা আত্মা আছে। এই আত্মা অবিনাশী, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করা, সমস্ত জীবের প্রতি ঐকান্তিক অহিংসাই জৈনধর্মের অপরিহার্য মূলনীতি।
আজিবিক ধর্মের তুলনায় জৈন ধর্ম ভারতে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের স্মৃতি এই ধর্মের সঙ্গে বিজড়িত। এদের মধ্যে শেষের দুজন অর্থাৎ পার্শ্ব এবং বর্ধমান মহাবীরকেই ঐতিহাসিক বলে মনে করা হয়। পার্শ্বের জীবন সম্পর্কে শুধু এটুকুই জানা যায় যে তিনি কাশীর রাজপুত্র ছিলেন এবং মহাবীরের প্রায় আড়াইশাে বছর আগে তার আবির্ভাব হয়েছিল (কাশী বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বারণস বা বেনারস)। তাই ঐতিহাসিক দিক থেকে বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মের প্রথম না হলেও, প্রধান প্রতিষ্ঠাতা।
জৈনদর্শনের উত্থানভূমি
প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিকধর্ম ও এর ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্মকাণ্ডের প্রভাবে উদ্ভুত অস্থির সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের উদ্ভব হয়। তবে কালানুক্রমের হিসাবে জৈনদর্শন বৌদ্ধদর্শননের থেকে প্রাচীন। বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী এই জৈন ধর্ম সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদভাবনার সাথে কম-বেশি সাদৃশ্য বহন করে। তবে চার্বাকদের মতো জৈনরাও বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু জগতের চারটি মূল উপাদানের (ভূতচতুষ্টয়) থেকে অতিরিক্ত জীবাত্মার স্বীকার করেন। এক্ষেত্রে নাস্তিক হয়েও জৈনরা অনাত্মবাদী বৌদ্ধদের থেকে আলাদা। তাই অধ্যাপক হপকিন্সের (Hopkins) মতে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যবর্তী তাত্ত্বিক সোপানরূপে জৈনদর্শনের অবস্থান।
বেদ ও উপনিষদে বিবৃত কিছু সিদ্ধান্তের সাথে জৈনমতের মিল আছে, যেমন জৈনরাও পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসী ও তাদের মতে কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী জীবের জন্ম হয়। জন্মান্তরে আত্মা ইতর প্রাণী, মানুষ, দেবতা বা দৈত্যের দেহ ধারণ করতে পারে। কঠিন তপশ্চর্যা, সর্বত্যাগ ও আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করা যায়। এই দর্শনে সিদ্ধপুরুষকে ‘অর্হৎ’ নামে অভিহিত করা হতো বলে জৈনদর্শনকে আর্হতদর্শনও বলা হয়। পরবর্তীকালে এই দর্শনের নাম হয়েছে জৈন দর্শন। ‘জিন’ দ্বারা প্রবর্তিত বলে এই ‘জৈন’ নামকরণ। জৈনমতের প্রচারকদেরকে ‘তীর্থঙ্কর’ বলা হয়। জৈনবিশ্বাস মতে, এই তীর্থঙ্কররা সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ করে সকল তত্ত্ব জয় করেছেন বলে তারা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সমুদয় জ্ঞান এবং দর্শনকে জানেন। একারণে এই মতকে সর্বজ্ঞাতাবাদীও বলা হয়।
জৈনমত অনুসারে, তাদের ধর্ম সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকেই প্রচলিত। প্রত্যেক উৎসর্পণকারী (=উত্থানকারী) ও অবসর্পণকারী (=নীচে অর্থাৎ ভূলোকে আবির্ভূত) তীর্থঙ্করের সংখ্যা চব্বিশ। তাদের মধ্যে শেষ অবসর্পণকারী প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব, যাকে খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দির ভারতীয়রা আদিনাথ হিসেবে পূজা করতো। ভাগবতপুরাণে তাকে জৈনদর্শনের প্রতিষ্ঠাপক বলা হয়েছে এবং তিনি বিষ্ণুর চব্বিশটি অবতারের মধ্যে অন্যতম বলে পরিচিত। তিনি মনুবংশীয় নাভিরাজের পুত্র এবং তার মায়ের নাম হচ্ছে মরুদেবী। এছাড়া যজুর্বেদে ঋষভ, অজিতনাথ ও অরিষ্টনেমি এই তিনজন তীর্থঙ্করের নাম উল্লেখ রয়েছে বলে জৈনদর্শনের অতীব প্রাচীনতার দাবী করা হয়। এদের মধ্যে অরিষ্টনেমি হচ্ছেন বাইশতম তীর্থঙ্কর, যার অন্য নাম হচ্ছে নেমিনাথ।
জৈনদর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না বলে তীর্থঙ্করগণই জৈন দর্শনে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত। জৈনগণ তাই ঈশ্বরের পরিবর্তে তীর্থঙ্করদের পূজা করেন। জৈনরা মনে করেন, এই তীর্থঙ্করেরা প্রথম জীবনে বদ্ধ জীব ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তারা নিজের চেষ্টায় পূর্ণ, মুক্ত ও সর্বজ্ঞ হয়েছেন। জৈন বিশ্বাস মতে, তীর্থঙ্করদের মতো যে কোন জীবই নিজের চেষ্টায় পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি এবং পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হতে পারে। মুক্ত, পূর্ণ ও সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্করগণ জৈনধর্মে ‘জিন’ নামে পরিচিত।
জৈন ঐতিহ্যে যে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পারম্পর্য উল্লেখ করা হয়, তাদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব আদিনাথ ও চব্বিশতম বা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান। এ দুয়ের মধ্যবর্তীরা হচ্ছেন- ২.অজিতনাথ, ৩.সম্ভবনাথ, ৪.অভিনন্দ, ৫.সুমতিনাথ, ৬.পদ্ম, ৭.প্রভু, ৮.সুপর্শ্বনাথ, ৯.চন্দ্রপ্রভু, ১০.সুরিধিনাথ, ১১.শিতলনাথ, ১২.শ্রেয়োনাথ, ১৩.বসুপুজ্য, ১৪.বিমলনাথ, ১৫.অনন্তনাথ, ১৬.ধর্মনাথ, ১৭.শান্তিনাথ, ১৮.কুন্থুনাথ, ১৯.অমরনাথ, ২০.মল্লিনাথ, ২১.মুনিসুব্রত, ২২.নেমিনাথ, ২৩.পার্শ্বনাথ। আদিনাথ ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী তীর্থঙ্করদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক সত্যতা দাবী করা হয়।
তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ (৮১৭-৭৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব) হলেন কাশীরাজ অশ্বসেনের পুত্র। তার মায়ের নাম বামদেবী। জনশ্রুতি অনুযায়ী, পার্শ্বনাথ প্রচুর ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে কৈবল্য লাভ করেন এবং সত্তর বছর বয়সে ছোটনাগপুরের পরেশনাথ পাহাড়ে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। পার্শ্বনাথের দুই শতকেরও অধিককাল পর চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের আবির্ভাব। মহাবীর বর্ধমানকেই জৈনমতের প্রধান প্রবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়। তীর্থঙ্কর বর্ধমানকে জৈনরা বলেন মহাবীর এবং বৌদ্ধরা বলেন নিগণ্ঠ নাতপুত্ত (নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র)। গ্রন্থিহীন বা নির্গ্রস্থ বা নগ্ন অবস্থায় থাকতেন বলে মহাবীর বর্ধমানকে বৌদ্ধ ত্রিপিটকে পালি পরিভাষায় নিগণ্ঠ বলা হতো।
বৌদ্ধধর্মে যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। সে তুলনায় জৈনধর্মে পরিবর্তনের পরিমাণ অনেক কম। বৌদ্ধধর্ম ভারতের জাতিভেদ প্রথা এবং আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপােষ করেনি, কিন্তু জৈনধর্ম এই আপোষ করেছিল। এরফলে জৈনধর্ম ভারতে এখনও টিকে আছে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ২০১১ সালের ভারতে বর্তমানে জৈনদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চুয়াল্লিশ লক্ষ। একই কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেও জৈনধর্ম কোথাও বিস্তৃত হতে পারেনি, তা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকেছে।
মহাবীর
বাসাম বলেছেন, গৌতম বুদ্ধের তুলনায় বর্ধমান মহাবীরের জীবন কাহিনী অনেক কম আকর্ষক এবং অনেক বেশি অবিশ্বাস্য। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তাকে বুদ্ধের অন্যতম প্রধান বিরােধী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তার ঐতিহাসিকতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর জ্ঞাতৃপুত্র ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। জ্ঞাত্রিক অর্থ ক্ষত্রিয়। জ্ঞাতৃপুত্র মানে ক্ষত্রিয়-পুত্র। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে পালি পরিভাষায় তাকে বলা হয় নাতপুত্ত বা নাথপুত্ত। নাথ মানে প্রভাবশালী বা প্রভুস্থানীয়। বুদ্ধের জন্মের কিছু আগে প্রাচীন বজ্জী (মজঃফরপুর, বিহার) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বৈশালীতে (বর্তমান বসরা, পাটনার নিকটবর্তী) লিচ্ছবিদের একটি শাখার জ্ঞাতৃবংশে মহাবীরের জন্ম। ঐতিহাসিকভাবে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে, আর ঐতিহ্যগতভাবে আনু. ৫৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাবীরের জন্ম হয়। তার পিতা সিদ্ধার্থ কুন্দপুরের জ্ঞাতৃক গােষ্ঠীর নেতা ছিলেন। মা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবিদের নেতা চেতকের বােন। যুবরাজের যােগ্য শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন। যশােদা নামে এক নারীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। তার এক কন্যাও হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মুক্তির উপায় অনুসন্ধানই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তদকালীন প্রজাতন্ত্রগুলি গণসংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হতো বলে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে মহাবীরের পিতা সিদ্ধার্থ গণসংস্থার একজন সদস্য ছিলেন।
মাতা-পিতার দেহত্যাগের পর আটাশ বছর মতান্তরে ত্রিশ বছর বয়সে তিনি গৌতম বুদ্ধের মত সংসার ত্যাগ করে তপশ্চর্যায় ব্রত হন। প্রথমে তিনি পার্শ্বনাথের প্রবর্তিত নির্গ্রন্থ তপস্বিসঙ্ঘের যতিধর্ম (=সন্ন্যাস) গ্রহণ করেন। এভাবে তার বারাে বৎসরের ভ্রাম্যমান জীবন কঠোর কৃচ্ছসাধনের মধ্যে অতিবাহিত হয়। এই সময় একটিমাত্র পােষাক সম্বল করে তিনি তের মাস কাটান। পরে তিনি সেটিও বর্জন করেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলেন। এই বারো বছরের তপশ্চরণকালে প্রথম ছয় বছর মক্ষলি গোশাল নামে অন্য একজন তাপসের সাথে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করতে থাকেন। গোশালও গ্রন্থিহীন বা নগ্ন তাপস ছিলেন বলে জানা যায়। এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ হলে মক্ষলি গোশাল বর্ধমানকে ত্যাগ করে আজীবক নামে স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, যার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী ছয়টি বছরও এই নির্গ্রন্থ বা গ্রন্থিহীন বা বাঁধহীন অবস্থায় তপস্যা করার পর সত্যজ্ঞান লাভ করে কেবলী বা সর্বজ্ঞ, জিন বা জিতেন্দ্রিয় ও মহাবীর নামে খ্যাত হন। নিজের বীর্যের দ্বারা রাগদ্বেষ প্রভৃতি জয় করায় তিনি এই মহাবীর আখ্যা পান। এই বারো বছর তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করে নিদিধ্যাসন ও নানা প্রকার তপশ্চরণের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে বেড়ান।

এরপর মহাবীর পরবর্তী ত্রিশ বছর মধ্যপ্রদেশের গাঙ্গেয় সমতলভূমির রাজ্য বিশেষ করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে নিজের ধর্মমত ও উপদেশ বিতরণ করেন। মগধের রাজধানী পাবা নগরীতে (কুশীনগরের উত্তরে বর্তমান গোরক্ষপুর) কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীর অমাবস্যা রাতে তার দেহান্ত হয়। মহাবীর সত্তর বছরের বেশি বেঁচেছিলেন। অনেকে মনে করেন, তার আয়ুষ্কাল আশি বছরের বেশি। প্রচলিত ধারণা অনুসারে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি মগধের অন্তর্গত রাজগৃহের নিকটবর্তী পাবা নগরীতে স্বেচ্ছাবৃত অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর তারিখটি বহু বিতর্কিত। বর্ধমান মহাবীরের জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ৫৯৯ সালে জন্মে ৫২৭ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে বর্ধমান মহাবীরের জন্ম ৫৬৯ খ্রীষ্টপূর্ব ও মৃত্যু ৪৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব। আবার কেউ বলেন জন্ম ৫৪০ খ্রীষ্টপূর্ব ও মৃত্যু ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্ব। তবে গৌতম বুদ্ধের (৫৬৩-৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্ব) সময়কালের বিবেচনায় নিলে তার ৫৪০-৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের জীবনকালকে গ্রহণ করতে হয়, কারণ এটা স্বীকৃত যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরই মহাবীরের দেহান্ত হয়।
জৈন ধর্মপ্রসার
প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরায় এ বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ ছিলো যে, কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা দৈহিক কামনা-বাসনার দমনের মাধ্যমে সাধারণ মানবিক স্পৃহা ও দুর্বলতা দূরীকরণ এবং মনঃসংযোগের শক্তিবৃদ্ধি করতে হয়। এ ধারাতেই মহাবীর সন্ন্যাস জীবনে শরীরকে কঠোরভাবে ক্লিষ্ট করা তপস্যা এবং তার মাধ্যমে ধ্যানমগ্ন হয়ে নতুন ধর্মমত দানা বাঁধতে থাকেন। কেবলপদ লাভ করে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সেই নীতি প্রচার করতে থাকেন। প্রথম দিকে শুধুমাত্র বিহারে তার ধর্মের বিস্তার ঘটে এবং তিনি বহু প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক পেয়েছিলেন। পরে তা ভারতের বিভিন্ন অত্যন্ত-প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতে নির্গ্রন্থ এ তপস্বী ‘মহাবীর’ ও ‘জিন’ (=বিজয়ী) নামে পরিচিত হয়ে উঠলে তার ধর্মমত জৈনধর্ম দর্শন নামে খ্যাত হয়। মহাবীর প্রবর্তিত জৈন ধর্ম ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যে সব রাজা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপােষক ছিলেন, তারা তার ধর্মেরও পৃষ্ঠপােষকতা করেছিলেন। এই ধর্মমত যারা গ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলেই বিহারবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না, অনেক গৃহীও ছিলেন। এই গৃহীদের সংসার অথবা সম্পত্তি, কিছুই ত্যাগ করতে হয়নি। গার্হস্থ্য জীবনযাপন করে এরা জৈনধর্ম নিদিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতেন মাত্র। ফলে পরবর্তীকালে এ ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। তাই সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম-দর্শন হিসেবে বৌদ্ধ ত্রিপিটকে এই জৈনমতের সরব ও কটাক্ষপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে জৈনধর্ম প্রধানত মগধ, কোসল, বিদেহ এবং অঙ্গ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন জৈনদের সংখ্যা আজিবিকদের তুলনায় কম ছিল। মৌর্যযুগে জৈনদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তার আগে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই ধর্মের পৃষ্ঠপােষকতা করেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তার জীবনের শেষ দিকে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কলিঙ্গরাজ খারবেলও জৈন ছিলেন।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বের শেষ দিকে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, তার ফলে অনেক জৈন সন্ন্যাসী গঙ্গাতীর ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন। তাদের এই অভিপ্রয়াণকে কেন্দ্র করে জৈনদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই অভিপ্রয়াণের নেতা ভদ্রবাহু মহাবীরের অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতে চান এবং জৈনদের সম্পূর্ণ নগ্নতা সমর্থন করেন। এর ফলে তিনি এবং তার অনুচরগণ দিগম্বর নামে পরিচিত হন। অন্যদিকে উত্তর ভারতে যে সব জৈন থেকে যান, তাদের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র। তিনি মহাবীরের পূর্ববর্তী পার্শ্বের অনুশাসন অনুসরণ করে জৈনদের শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার সমর্থন করেন। এভাবে তিনি ও তার সমর্থকগণ শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিভেদ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেনি। ও এ কথাও সত্য যে বহিরঙ্গ বিষয়ে এই মতভেদ সত্ত্বেও, ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। জৈনদের মধ্যে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জৈন ধর্মশাস্ত্রেরও পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে। মৌখিক পবিত্র জৈন সাহিত্যের সঙ্গে শুধুমাত্র ভদ্রবাহুর পরিচয় ছিল। তার মত্যুর পর স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে পার্শ্বের চৌদ্দটি অনুশাসনেরর পরিবর্তে বারোটি অনুশাসন গৃহীত হয়। এগুলো দ্বাদশ অঙ্গ নামে পরিচিত। শ্বেতাম্বর জৈনগণ এই অঙ্গগুলো মেনে নেয়নি। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত বলভীতে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলো চুড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত এবং লিপিবদ্ধ করা হয়। তখন মূল অনুশাসনের সঙ্গে নতুন বিষয় যুক্ত করে দ্বাদশ উপাঙ্গ রচিত হয়।

মৌর্য এবং গুপ্তযুগের মধ্যবর্তী সময়ে জৈনধর্ম মােটামুটিভাবে পূর্বে ওড়িশা থেকে পশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। পরবর্তীকালে এই ধর্ম প্রধানত কাথিয়াবাড়, গুজরাট এবং রাজস্থানের অংশবিশেষে কেন্দ্রীভূত হয়। এই অঞ্চলে শ্বেতাম্বরদের প্রাধান্য ছিল। অন্যদিকে, দাক্ষিণাত্যে মহীশূর এবং দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে প্রাধান্য ছিল দিগম্বরদের। খ্রিস্টীয় ১২শ শতাব্দীতে চালুক্য বংশীয় নৃপতি কুমারপালের রাজত্বকালে পশ্চিম ভারতে শ্বেতাম্বর জৈনগণ বিশেষ গুরত্ব অর্জন করেছিল। প্রখ্যাত জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র তখন এই ধর্মের সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। তার মত্যুর পর এই সম্প্রদায়ের মর্যাদা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে রাজাদের অনুকূল্যে দাক্ষিণাত্যে দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জৈনদের প্রভাব দ্রুত ক্ষুণ্ণ হয়। এভাবে জৈন ধর্মের অবনতি ঘটলেও ভারতবর্ষ থেকে এই ধর্ম কখনও লোপ পায়নি। দুহাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের জনসমষ্টির একটি উল্লেখযােগ্য অংশ জৈন থেকে গেছে। এর একটি কারণ হল জাতিভেদ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জৈন ধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে আপােষ করেছে। জন্ম, মত্যু এবং বিবাহ সপর্কিত আচার-অনুষ্ঠানে উভয় ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। এছাড়া জৈনধর্ম গৃহী ভক্তদের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছে। একদিক দিয়ে বৌদ্ধধর্ম যা পারেনি, জৈনধর্ম তাই করতে পেরেছে। অধিকতর সঙ্কল্পের সঙ্গে এ নিজেকে রক্ষা করেছে এবং মূল বিষয়, নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে কোন দিন কারও সঙ্গে আপােষ করেনি। তাই এই ধর্মে মহাযানের মত কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়নি। বাসাম বলেছেন, একমাত্র কঠোর অনুশাসনই জৈনধর্মকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে।
ভারতের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে জৈনধমের অবদান আছে। বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও বাণিজ্যিক গুণাবলী, সততা এবং মিতব্যয়িতাকে উৎসাহ দিয়েছে। এর ফলে এই ধর্ম দ্রুত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। অহিংসার উপর বিশেষ জোর দেয়ায় কৃষকশ্রেণী এই ধর্ম গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ কৃষিকাযের সময় অনেক কীটপতঙ্গের প্রাণনাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। জৈনধর্মে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে, কিন্তু এই নিষেধ শধুমাত্র ভূসম্পত্তি সম্পর্কে প্রযােজ্য, এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জৈনরা তাই ব্যবসা এবং শিল্পকাত দ্রব্যাদি বিনিময়ের ক্ষেত্রেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং তৎসংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন তাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এভাবে জৈনধর্ম ভারতের নগর সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
মধ্যযুগে জৈন সন্ন্যাসীগণ প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক টীকা ভাষ্য রচনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে শেষ বড় কবি, নয়চন্দ্র জৈন সন্ন্যাসী ছিলেন। কালিদাসের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথও একজন জৈন। জৈনদের সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহ এত বেশি ছিল যে, যে কোন বিষয়ের পুঁথি নকল করাকে তারা পুণ্যকর্ম মনে করতেন। তাই পশ্চিম ভারতের প্রাচীন জৈন বিহারগুলো অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য জৈন ও অজৈন পুঁথির ভাণ্ডার হয়ে আছে। জৈন দর্শনের সহজাত বাস্তবতাবােধ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও জৈনরা পিছিয়ে থাকে নি। সােমনাথ লুণ্ঠনের দুশাে বছর পরে মাউন্ট আবুতে নির্মিত অপূর্ব জৈন মন্দিরটি তাদের সৃষ্টি। এটি এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণ বেলগােলার মন্দিরটি মধ্যযুগের জৈন গৃহীদের সম্পদ ও ধর্মবােধের চিরন্তন নিদর্শন হয়ে আছে।
জৈনধর্মের কিছু দার্শনিক দিক ও বৌদ্ধদের কটাক্ষ
কঠোর তপস্যা, সংযম ও অহিংসাই বর্ধমান মহাবীরের মূল শিক্ষা ছিলো। তার প্রধান শিক্ষাকে বৌদ্ধ ত্রিপিটকের দীঘনিকায়ে এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে – “নিগণ্ঠ (জৈন সাধু)-গণ চার প্রকার সম্বর (সংযম) দ্বারা নিজেদের সংবৃত্ত রাখেন –
- (১) নিগণ্ঠগণ জল ব্যবহারে নিষেধ করেছেন (যাতে জলের প্রাণী না নিহত হয়);
- (২) তারা সমস্ত পাপ কর্ম থেকেই বিরত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন;
- (৩) সকল পাপের নিষেধ করায় তারা পাপরহিত হন;
- (৪) নিগণ্ঠ সমস্ত পাপের বিপক্ষে থাকেন। …যদি নিগণ্ঠ এই চতুর্সংযমে সম্বৃত থাকেন তবে তাঁকে …গতাত্মা (অনিচ্ছুক), যতাত্মা (সংযমী) এবং স্থিতাত্মা বলা হয়।” (দর্শন-দিগদর্শন/ রাহুল সাংকৃত্যায়ন)
বৌদ্ধ ত্রিপিটক অনুযায়ী জৈনমতে তীর্থঙ্করকে সর্বজ্ঞ বলে জোর দেওয়া হয়েছে- ‘তীর্থঙ্কর সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সমুদয় জ্ঞান এবং দর্শনকে জানেন। চলনে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে সদা নিরন্তর জ্ঞান উপস্থিত থাকে।’ এই সর্বজ্ঞতাকে বিদ্রুপ করে বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ বলেন- “…(তবুও) তাঁরা শূন্য ঘরে যান, সেখানে ভিক্ষাও পান না, কুকুরও তাড়া করে, উন্মত্ত হস্তী …অশ্ব …ভয়ঙ্কর ষণ্ডেরও সম্মুখীন হন। (সর্বজ্ঞ হয়েও) স্ত্রী-পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করেন, গ্রাম নগরের ঠিকানা ও পথের হদিস জানতে চান। (আপনারা তো সর্বজ্ঞ) তবে কেন প্রশ্ন করেন- জিজ্ঞাসা করলে বলেন- ‘শূন্য ঘরে যাওয়া …ভিক্ষা না পাওয়া …কুকুরের তাড়া খাওয়া …হস্তী …অশ্ব …ষাঁড়ের সামনে পড়া অদৃষ্টাধীন।’…”
‘সুখ হতে সুখ প্রাপ্য নয়, দুঃখ থেকেই সুখ প্রাপ্য’- এ ভিত্তিতে বর্ধমান মহাবীরের বিশ্বাস ছিলো যে, দৈনিক দুঃখভোগই পাপক্ষালন এবং কৈবল্যসুখ প্রাপ্তির সাধন। কায়িক তপস্যা যথা আমরণ অনশন, শীত-গ্রীষ্মে নগ্ন হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন জৈন-আগমে বহুল প্রচলিত ছিলো। তাই বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মজ্ঝিমনিকায় (১/২/৪) জৈন সাধুদের তপস্যা এবং তার ঔচিত্যের বর্ণনায় দেখা যায় বুদ্ধ মহানাম শাক্যকে বলছেন- “মহানাম ! একদা আমি রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলাম। তখন বহুসংখ্যক নিগণ্ঠ সাধু গিরির কালোশিলার ওপর দণ্ডায়মান হয়ে তপস্যার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট-বেদনার তীব্রতাকে উপলব্ধি করছিলেন। …(কারণ জিজ্ঞাসা করলে) তাঁরা বললেন- ‘নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, …। তিনি বলেছেন …নিগণ্ঠগণ! তোমাদের পূর্বকৃত পাপকে এই দুষ্কর তপস্যার দ্বারা নাশ করো। যারা কায়মনোবাক্যে সংযমী তারা ভবিষ্যতে কোনো পাপ করবে না এই প্রকার তপস্যা দ্বারা পুরানো কর্মের সমাপ্তি ঘটিয়ে এবং নতুন কোনো ধর্ম গ্রহণ না করলে, ভবিষ্যতে চিত্ত নির্মল হয়ে যাবে। অনাসক্তি থেকেই ভবিষ্যতে কর্মক্ষয় হবে, তা থেকে দুঃখক্ষয়, তা থেকে বেদনাক্ষয়, এবং শেষে সকল দুঃখ নাশ হয়ে যাবে।’…”বুদ্ধ তাদের প্রশ্ন করেন- “তোমরা কি প্রথমে আত্মোপলব্ধি করেছো? সে সময় কি কোনো পাপ কর্ম করেছো? জানতে পেরেছো কি, কতোটা পাপক্ষয় হয়েছে কতোটা বাকি আছে? ইহজন্মেই পাপ নাশ হয়ে পুণ্যলাভ হবে কিনা তা কি তোমরা নিশ্চিত জানো?” নিগণ্ঠগণ এই প্রশ্ন সমুদয়ের প্রত্যেকটিরই উত্তর দেন ‘না’। অতঃপর বুদ্ধ বলেন- “এইভাবেই পৃথিবীতে যাদের ভয়ঙ্কর স্বভাব, রক্তরঞ্জিত যাদের হাত, ক্রূরকর্মা, তারাই নিগণ্ঠ সাধু সাজে।” (দর্শন-দিগদর্শন/ রাহুল সাংকৃত্যায়ন)।
সমকালীন প্রচলিত ধর্ম ও দর্শন হিসেবে জৈনমতকে উদ্দেশ্য করে বৌদ্ধ ত্রিপিটকে তীব্র কটাপূর্ণ উদ্ধৃতির এসব বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, সে সময়ে জৈনধর্ম ও দর্শন ভারতীয় সামাজিক জীবনে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিলো। প্রাচীন জৈনদর্শন মতে, জল মাটি প্রভৃতি সকল জড়-অজড় উপাদানই আত্মায় পূর্ণ; সকল প্রকার হিংসা থেকে মানুষকে রক্ষা করা দরকার। তাই মহাবীর জলের ব্যবহার, অর্থাৎ চলাফেরা করা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই কঠিন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছিলেন বলে এরই পরিণাম হিসেবে শস্য কাটা, নিড়ানি দেওয়া ইত্যাদি কাজে অসংখ্য জীবকে মরতে দেখে জৈনগণ কৃষিকার্য ছেড়ে দেয়। ফলে বণিক সম্প্রদায়ে ধীরে ধীরে জৈন মতাবলম্বী বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মন্তব্য করেন- ‘ইউরোপে ইহুদীগণ রাজশক্তি কর্তৃক কৃষিকার্যে বঞ্চিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রহণ করে, কিন্তু ভারতীয় জৈনগণ তা করে স্বধর্ম প্রেরিত হয়ে স্বেচ্ছাপূর্বক। মানুষের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে কিভাবে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে শ্রম ও উৎপাদন থেকে সরিয়ে এনে শ্রম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করা যায় এ তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ।’ পরবর্তীকালে প্রতিভাবান জৈন দার্শনিকদের কল্যাণে বিকশিত জৈনদর্শন তার সমৃদ্ধ তর্ক ও প্রমাণশাস্ত্রের মাধ্যমে ভারতীয় দার্শনিক সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেও জৈনদের বিরাট অংশ একে একে শেষপর্যন্ত নবদীক্ষিত বৌদ্ধধর্মে মিশে যায়।
বুদ্ধের সঙ্গে মহাবীরের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল বুদ্ধ নতুন একটি ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু মহাবীর তা করেন নি। তিনি পার্শ্ব প্রবতিত ধর্মের সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাই তার ভূমিকা যতটা ধর্ম প্রবর্তকের, তার চেয়ে বেশি ধর্ম সংস্কারকের। তিনি পার্শ্বের চারটি বিধান (সত্যবাদিতা, কাউকে আঘাত না করা, সম্পত্তির মালিক না হওয়া এবং দান ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ না করা) মেনে নিয়ে এদের সঙ্গে আরও দুটি বিধান (ব্রহ্মচর্য এবং বস্ত্রসমেত সবস্ব ত্যাগ) যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু একথা আক্ষরিক অর্থে সত্য হলেও প্রকৃত অর্থে সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে জৈনধর্ম বলতে মূলত মহাবীরের ধর্মমতকেই বোঝায়।
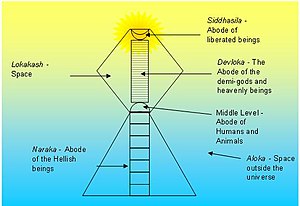
জৈনধর্ম একান্তভাবে নিরীশ্বরবাদী। এই ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়নি, কিন্তু এতে ঈশ্বরের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। এই মত অনুসারে বিশ্বসৃষ্টি এবং রক্ষার পেছনে কোন দৈব অনুগ্রহ নেই। ব্যতিক্রমহীন সর্বজনীন বিধান এই বিশ্বকে নিয়ত্রিত করে। এই বিশ্ব অনন্ত। এখানে পর্যায়ক্রমে উত্থানের পরে পতন, উন্নতির পরে অবনতি আসে। প্রতিটি পর্বে ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১২ জন রাজচক্রবর্তী এবং ৬৩ জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। একটি পর্বে উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌঁছলে মানুষের আকৃতি এবং আয়ু প্রচণ্ড রকম বেড়ে যায়। তখন মানুষের আইন বা সম্পত্তি, কোন কিছুর প্রয়ােজন হয় না। কল্পবৃক্ষের কাছ থেকে সে তখন যা চায় তাই পায়। জৈনধর্মমত অনুসারে এই বিশ্বে এখন অবনতির পর্ব চলছে। শেষ তীর্থঙ্করের নির্বাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে প্রকৃত ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে। এই অবনতি ৪০,০০০ বছর ধরে চলবে। এর মধ্যে মানুষ ক্রমশ বামনাকার লাভ করবে। তার আয়ু ২০ বছরে এসে ঠেকবে। এক সময় মানুষ গুহায় ফিরে যাবে। তার সভ্যতা, সংস্কৃতি এমনকি আগুনের ব্যবহার পর্যন্ত সে ভুলে যাবে। তারপরে আবার উন্নতির পালা শুরু হবে। অনন্তকাল ধরে এই ভাবে উন্নতি-অবনতি চক্রবৎ পরিবর্তিত হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম যে মহাপ্রলয়ে বিশ্বাস করে, জৈনধম তা করে না।
জীব (soul) এবং অজীব (matter) এই দুইটি শব্দকে জৈন ধর্মবিশ্বাসের দুটি স্তম্ভ বলা যায়। জৈনদের কাছে জীব শব্দটির দ্যোতনা আধ্যাত্মিক এবং অজীব শব্দটির দ্যোতনা বাস্তব। কিন্তু তারা উভয়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কঠিন সীমারেখা টানেনি। তারা অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন জীবকে বাস্তবায়িত করেছে, আবার বাস্তবচেতনাসম্পন্ন অজীবকে আধ্যাত্মিকতা দান করেছে। তাদের মতে জীব এবং অজীবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এই বিশ্ব কাজ করে।
জৈনরা জীবের ব্যাপক অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের মতে জীব শুধু প্রাণীজগতেই নেই, তথাকথিত অ-প্রাণীজগতে (লতা, গম, পাহাড়, পর্বত, নদী, স্রোত ইত্যাদি) একই ভাবে আছে। এই জীব উজ্জ্বল, সবজ্ঞ এবং পরম সুখের আকর। তাদের সংখ্যা অনন্ত। তারা সকলেই সমান এবং একমাত্র বস্তুর অনুষঙ্গেই তারা ভিন্ন হয়ে যায়। এই বস্তু হল কর্ম। মানুষের জীবনে কর্মের শেষ নেই। একটি কর্মের পর আর একটি কর্ম আসে। তাই তার সংসারেরও শেষ নেই। একটি জন্মের পর সে অন্য জন্ম লাভ করে। এই কর্মবন্ধন ছিন্ন করতে পারলে সংসারবন্ধন থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। এই কাজ খুব কঠিন ও অনেকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।
জৈনদের কাছে জীব অতি পবিত্র। কর্মের বন্ধনই একে অপবিত্র করে। তাদের মতে এই অপবিত্রতা দূর করে জীবের পবিত্রতা সাধন করাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। উপনিষদে বর্ণিত জ্ঞানের দ্বারা এই পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। কেননা, অন্ধের হস্তীদর্শনের মত এই জ্ঞান সর্বদা আংশিক এবং আপেক্ষিক। এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং সংযত জীবনযাপন প্রয়োজন। এই জীবনযাপন গৃহীর পক্ষে দুঃসাধ্য। জৈনধর্মে তাই মঠ-জীবনের ওপর বিশেষ গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রায়শ্চিত্ত ও সংযমের সাহায্যে দুঃসাধ্য ব্রত উদযাপনের পর জীব যখন কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে, তখন সে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। তখন তার স্থান দেবতারও ঊর্ধ্বে। কেননা দেবতা কর্মের অধীন, কিন্তু সে নয়।
জৈনদের সাধনা একান্তভাবে ত্যাগ ও পবিত্রতার সাধনা। মহাবীর তার অন্যতম শিষ্য গৌতমকে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে এই সত্য অতি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন সব আসক্তি ত্যাগ কর, পদ্মের মত, শরৎকালের জলের মত পবিত্র হও। জীব এবং বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি জৈনধর্মের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ শতাব্দীর জৈন সন্ন্যাসী পুজ্যপাদের ছন্দোবদ্ধ উক্তির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, জীব এক, বস্তু আর এক, সত্যের সারমর্ম এই। আর যা কিছু বলা হয়, সব এই মর্মবাণীর ব্যাখ্যা মাত্র। পুজ্যপাদ সেই ব্যাখ্যাও শুনিয়েছেন। তার মতে দেহ, গৃহ, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র এবং শত্রু, সবই জীব থেকে আলাদা। একমাত্র নির্বোধ মানুষই এদের নিজের বলে ভাবে। তার মতে এরা নানা দিক থেকে উড়ে আসা পাখির মত, যারা সন্ধ্যায় একই বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেয় এবং ভাের হলে আপন খেয়ালে ভিন্ন ভিন্ন দিকে উড়ে যায়। এই কবিতাটিতে তিনি জরা, মত্যু সব কিছুকে প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, মত্যু আমার জন্য নয়, তাহলে আমি ভয় পাব কেন? রােগও আমার জন্য নয়, তাহলে আমি কেন নিরাশ হব? আমি শিশু নই, যুবক নই, বৃদ্ধ নই। এসবই আমার শরীরের বিভিন্ন অবস্থা। অহিংসা জৈন ধর্মের আর একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। এর উপর জৈনরা মাত্রাতিরিক্ত গরুত্ব আরােপ করেছিল। তাই তাদের কাছে অজ্ঞানে সামান্যতম কীট হত্যাও পাপ। এদিক থেকে জৈনধর্ম অন্য সব ধর্মকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।
মহাবীর পরবর্তী গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈনধর্ম
গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈন ধর্মের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতে এই যুগকেই জৈনধর্মের সব চেয়ে গৌরবের যুগ বলা যায়। গুপ্ত যুগে এই ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু স্থানান্তরিত করা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। উভয় যুগেই এই ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপােষকতা লাভ করেছিল। তবে এই পৃষ্ঠপােষকতা বরাবর অক্ষুন্ন থাকেনি। অবশ্য বরাবরই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, বিশেষত ব্যবসায়ীদের সক্রিয় সমর্থন এই ধর্মের পুষ্টি সাধন করেছিল। গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈন ধর্মসাহিত্যের বাহন ছিল প্রধানত প্রাকৃত ভাষা। গুপ্ত যুগে ধীরে ধীরে সংস্কৃত প্রাকৃতের স্থান গ্রহণ করেছিল। গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈনধর্মের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগে এই ধর্মের অবনতি সূচিত হয়েছিল। গুপ্ত যুগে জৈনধর্মের অবনতি ঘটলেও, এখনও এই ধর্ম ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম বলতে যা বােঝায়, জৈনধর্ম বােধহয় সেই অর্থে ধর্ম ছিল না। এটি ছিল একটি নৈতিক বিধান। কিন্তু মূলত নৈতিক বিধান হলেও, এই ধর্ম নীতি সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে যতটা আপস করেছিল, ভারতে অন্য কোন প্রতিবাদী ধর্ম তা করেনি। এই ধর্ম হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরােধিতা করেনি। হিন্দু দেব-দেবীকে গ্রহণ করেছিল। ন্যায়ের দিক থেকে এই ধর্মে চূড়ান্ত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি, কোনটাই ছিল না, তাই এই ধর্ম স্থায়ী হয়েছিল।
গুপ্ত-পূর্ব যুগের জৈনধর্মের ইতিহাসের প্রধানত দুইটি দিক। একটি অন্তরঙ্গ, অন্যটি বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ দিকের ইতিহাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিরােধের কাহিনী। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, বৌদ্ধধর্মে এই বিরােধ যতটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল, জৈনধর্মে তা করেনি। বিরােধের ফলে বৌদ্ধধর্মের সারবস্তু আক্রান্ত হয়েছিল। জৈনধর্মে তা হয়নি। জৈনধর্মে ধর্মের সারবস্তুকে নিয়ে নয়, কয়েকটি অনুষঙ্গকে নিয়ে এই বিরােধের সৃষ্টি হয়েছিল। জৈনধর্মের ইতিহাসের বহিরঙ্গ দিক বলতে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণে এই ধর্মের সম্প্রসারণ কাহিনী বােঝায়। গুপ্ত-পূর্ব যুগের জৈনধর্মের ইতিহাসের এই দুইটি প্রধান দিক ছাড়া আরও দুইটি দিক আছে। একটি হল সাহিত্যের দিক এবং অন্যটি গুহা স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের দিক। এই যুগের জৈনধর্মের ইতিবৃত্তের জন্য কালাকাচার্য কথানকম গ্রন্থ এবং শ্রাবণবেলগােলা, হাথিগুম্ফা এবং মথুরায় প্রাপ্ত কয়েকটি লেখের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া কলিঙ্গ এবং মথুরায় প্রাপ্ত গুহা স্থাপত্য এবং জৈন ভাস্কর্য নিদর্শনও আমাদের সাহায্য করে। জৈনগণ মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রখ্যাত ধর্মগুরু, কল্পসূত্র গ্রন্থের রচয়িতা ভদ্রবাহু তার সমসাময়িক ছিলেন। জৈনধর্মের দিক কিন্তু তাদের সময় থেকে শুরু হয়নি। এই বিবর্তনের একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। মহাবীর পর্যন্ত সেই ইতিহাস আলােচনা করা হয়েছে, এখন মহাবীর পরবর্তী জৈনধর্মের বিবর্তনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস এখন আলােচনা করা যাক।
মহাবীর সমগ্র জৈন সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তার পরে, অনেকের মতে গৌতম ইন্দ্রভূতি বারাে বৎসর জৈন ধর্মগুরু রূপে কাজ করেন। তার পরে পুনরায় বারাে বছরের জন্য এই পদ অলঙ্কৃত করেন সুধর্মণ। তার পরে তার শিষ্য জম্বুস্বামী এই পদ লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ চব্বিশ বছর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শেষ কেবলিন। তারপরে মানুষের পক্ষে মােক্ষ এবং কেবলজ্ঞান লাভ করা আর সম্ভব নয় বলে মনে করা হত। তার পরে যে ছয়জন ধর্মগুরুর আসন অধিকার করেছিলেন, জৈন ইতিহাসে তারা শ্রুতকেবলিন বলে পরিচিত। পূর্ব ধর্মগুরুদের কেবলজ্ঞান তাদের ছিল না, তবে জৈনধর্মশাস্ত্র তাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। তাদের পরে যারা এসেছিলেন, তারা দশপূর্বী বলে পরিচিত। অর্থাৎ তাদের শুধু দ্বাদশ ‘অঙ্গের’ দশটি পূর্বের জ্ঞান ছিল। এভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জৈন ধর্মগুরুদের আধ্যাত্মিক অধিকার এবং গৌরব হ্রাস পেয়েছিল।
জম্বুস্বামীর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন প্রভাব। তিনি পূর্বে একজন যুবরাজ এবং দস্যু ছিলেন। তিনি সয়ম্ভব নামক একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণকে জৈনধর্মে দীক্ষা দেন। এই সয়ম্ভব প্রভাবের পরে ধর্মগুরুর পদ লাভ করেন। তার পরে এই পদ লাভ করেন যশােভদ্র। পরবর্তী ধর্মগুরু সভৃতিবিজয়ের কার্যকাল ছিল মাত্র দুই বছর। তার পরে আসেন প্রখ্যাত ধর্মগুরু ভদ্রবাহু। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি ছিলেন শেষ শ্রুতকেবলিন। তার নেতৃত্বকালে জৈনধর্মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর গ্রন্থ, ভদ্রবাহুচরিত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে মগধে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভদ্রবাহু তার সঙ্গীদের নিয়ে দক্ষিণ ভারতে মহীশূর অঞ্চলে আসেন। এইভাবে তারা উত্তর ভারতের জৈনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আগেই বলা হয়েছে যে, এই বিচ্ছেদের ক্রম পরিণতি হিসাবে জৈনগণ শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর, এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান। জৈনদের এই পারস্পরিক বিচ্ছেদ সম্পর্কে দুইটি বিষয় মনে রাখা প্রয়ােজন। প্রথমত, জৈনধর্মের মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়নি। বৌদ্ধধর্মে, ধর্মের সারবস্তুকে কেন্দ্র করে হীনযান এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। জৈনধর্মের ইতিহাসে তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। শ্বেতাম্বর-দিগম্বর বিভাগ ঘটেছিল একান্তভাবে আনুষঙ্গিক গৌণ বিষয়কে কেন্দ্র করে। বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্ম ছিল অনেক বেশি রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতা তাকে বাঁচিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই বিচ্ছেদ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এজন্য মগধের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষকে দায়ী করা চলে না। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি এবং প্রথম দিকের ভাস্কর্য নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, এই বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছিল। পাটলিপুত্রে স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে বয়স্ক জৈনদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতেও এই বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। এই সম্মেলনে ১১টি অঙ্গ এবং ১৪টি পূর্ব জৈনধর্ম শাস্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল, কিন্ত ভদ্রবাহু এবং তার অনুচরবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত অনুমােদন করেননি

সে যাই হােক, ভদ্রবাহু যখন মহীশূরে যান, তখন মগধের জৈনদের ধর্মগুরু হিসাবে স্থূলভদ্র সেখানে থাকেন। স্থূলভদ্র ছিলেন নন্দবংশের শেষ রাজার প্রধানমন্ত্রী শকতালের মান। তিনি তার দুই ভাগিনেয় মহাগিরি এবং সুহস্তিনকে জৈনধর্মে দীক্ষা দেন। অল্পকাল সরে এই দুই ভাইয়ের মধ্যেও বিরােধের সূত্রপাত হয় এবং তারা ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। স্থূলভদ্রের মৃত্যুর পর মহাগিরি মগধের জৈনদের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন। প্রকৃত সংস্কারকের উৎসাহ মহাগিরির ছিল। তিনি পুনরায় মগধের জৈনদের মধ্যে নগ্নতার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ফলবতী হয়নি। সুহস্তিন কর্তৃক মগধের রাজা সম্প্রতিকে জৈনধর্মে দীক্ষা দান এই ধর্মের প্রকৃত উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্বণে সম্প্রতিকর্তৃক জৈনধর্মের পৃষ্ঠপােষকতার বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে সম্প্রতি জৈনদের জন্য সমগ্র জম্বুদ্বীপে মন্দির নির্মাণ করেন। সুহস্তিন যখন উজ্জয়িনীতে ছিলেন, তখন তিনি তার পরিচালনায় জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার এবং অনুষ্ঠানের আয়ােজন করেন। প্রকৃতপক্ষে অশােক বৌদ্ধধর্মের জন্য যা করেছিলেন, সম্প্রতি জৈনধর্মের জন্য তাই করেন। তিনি সুদূর আফগানিস্তান, অন্ধ্র ও তামিল অঞ্চলে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এভাবে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে শ্বেতাম্বরদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তিনি জৈন সঙ্ঘের সদস্যদের উত্তম আহার্য এবং অন্যান্য দ্রব্য দিতেন। এর ফলে আপাত দৃষ্টিতে জৈনধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে এই ধর্ম ক্রমশ দুর্বল হয়েছিল। পাছে রাজা অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে সুহস্তিনকে এই সবই মেনে নিতে হয়েছিল। মহাগিরি সুহস্তিনকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সুহস্তিন এতদিন জৈনদের কার্যত নেতা ছিলেন। এবার তিনি আইনসিদ্ধভাবে নেতৃপদ লাভ করেন। মহাগিরির সংস্কার প্রয়াস এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে মত বিরােধের ফলে জৈন সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হয়েছিল, তিনি তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। তিনি নতুন শিষ্য গ্রহণ এবং নূতন শাখা স্থাপন করেন। এই কাজও অতিরিক্ত এবং অনুচিত দ্রুততার সঙ্গে করা হয়েছিল। অবন্তিকুমারের জীবনের করুণ পরিণাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধনীর দুলাল এবং বিলাস ব্যসনে লালিত অবন্তিকুমার জৈন সঙ্ঘে যােগদান করেছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরে সন্ন্যাস জীবন তার মােহভঙ্গ ঘটিয়েছিল এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
সুহস্তিনের পর তার অন্যতম শিষ্য সুস্থিত জৈন সম্প্রদায়ের নেতা হন। তার এবং তার পরবর্তী নেতা ইন্দ্রদিন্নের নেতৃত্বকালের সঙ্গে জৈন ধর্মগুরু কালিকার নাম বিশেষভাবে সাড়ত। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে উজ্জয়িনীর রাজা গর্দভিল্ল কালিকাকে অপমান করেন। এই অপমানের প্রতিশােধ গ্রহণের জন্য তিনি শকস্থানের শকরাজার শরণাপন্ন হন এবং শেষ পর্যন্ত তার সাহায্যে গর্দভিল্লকে পরাজিত করেন। কয়েক বছর পরে গর্দভিল্লের পুত্র প্রতিষ্ঠান থেকে সৈন্যসহ অগ্রসর হন, উজ্জয়িনী থেকে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করেন এবং নিজে সাড়ম্বরে সেখানে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫৮-৫৭ অব্দের বিক্রমাব্দের প্রবর্তক। গর্দভিল্লের পুত্র এই বিক্রমাদিত্যও জৈনধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপােষক ছিলেন। অনেকে এই বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেছেন। আবার অনেকে মনে করেন যে, এই ঐতিহ্যের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সে যাই হােক, মােটামুটিভাবে বলা যায় যে, কালিকা কাহিনী খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই শতাব্দীতে ভারতে শক আক্রমণ ঘটেছিল এবং সাতবাহনগণ সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং পুরাণে গর্দভিল্লদের অন্ধ্রভৃত্য বলা হয়েছে। ইন্দ্রদিন্নের পর নেতৃপদ লাভ করেন যথাক্রমে দিশূরি, সিংহগিরি এবং বজ্রস্বামী। এই বজ্রস্বামী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রধানত পাটলিপুত্র এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রচার করেন। তারপরে নেতা হন বজ্রসেন। তার পরবর্তী নেতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু সেই সব কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য খুবই সামান্য। সুতরাং গুপ্তপূর্ব যুগের জৈনধর্মের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস এখানেই শেষ করা যায়।
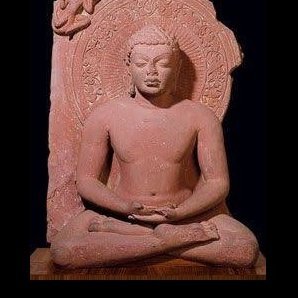
এখন আমরা জৈনধর্মের বহিরঙ্গ দিক, অর্থাৎ তার সম্প্রসারণের দিক আলােচনা করতে পারি। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়ােজন যে, এই সম্প্রসারণ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে ঘটেনি, সাময়িক অভিপ্রয়াণের ফলে ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও তার সূচনাকাল থেকে রাজানুগ্রহ লাভ করেছিল। বিম্বিসার মহাবীরের অনুরক্ত ছিলেন। অন্য ধর্মের তুলনায় জৈনধর্ম সম্পর্কে অজাতশত্রুর আগ্রহ বেশি ছিল। জৈনগণ অজাতশত্রুকে তার পিতৃহত্যার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এ থেকে তার পরােক্ষ আভাস পাওয়া যায়। জৈনধর্মের আদি কেন্দ্র ছিল মগধ। মহাবীরের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে তার সময় কোসল, বিদেহ এবং অঙ্গ রাজ্যে এই ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভারতে শ্রাবণবেলগােলাকে কেন্দ্র করে মহীশূর অঞ্চলে জৈনধর্মের সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রচলিত জৈন ঐতিহ্য অভিন্ন নয়। দিগম্বর ঐতিহ্য অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায়, ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে, মগধ থেকে এই অভিপ্রয়াণ ঘটেছিল। শেতাম্বর ঐতিহ্য অনুসারে এই অভিপ্রয়াণ ঘটেছিল মালবের উজ্জয়িনী থেকে। তাছাড়া এই অভিপ্রয়াণের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং ভদ্রবাহুর প্রকৃত কোন যােগ ছিল কিনা, প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করে অনেকে সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনুরূপ আর একটি অভিপ্রয়াণের ফলে জৈনধর্ম, মগধের দক্ষিণ-পূর্বে, কলিঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে মহাবীর স্বয়ং কলিঙ্গে এসেছিলেন। খারবেলের লেখ থেকে মনে হয় যে, তিনি কুমারী পাহাড়ে, অর্থাৎ উদয়গিরিতে, তার ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে খারবেল শাসিত কলিঙ্গ রাজ্য জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে মনে হয়। খারবেলের লেখ এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই লেখের সূচনায় তিনি জৈনদের প্রতি তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি নিজে একজন জৈনগৃহী ছিলেন। এই লেখতে তিনি বলেছেন যে, জৈন সন্ন্যাসীদের তিনি রাজকীয় বৃত্তি, শ্বেতবস্ত্র ইত্যাদি দান করেছিলেন। তিনি জৈন সন্ন্যাসীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলনে সাতটি অঙ্গ সঙ্কলিত হয়েছিল। এর আগে তিনি কলিঙ্গের যে জিন মূর্তি নন্দরাজা অপসারণ করেছিলেন, সেটি পুনরুদ্ধার করেন। তার অগ্রমহিষী জৈন সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের জন্য গুহা দান করেছিলেন। উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরির বহুসংখ্যক গুহায় জৈনধর্মের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং মনে হয় যে, খারবেলের সময় কলিঙ্গে জৈনধর্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এখানে উল্লেখযােগ্য যে, জৈন ইতিবৃত্তসমূহে খারবেলের জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপােষকতার কোন উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে খারবেলের লেখই একমাত্র প্রমাণ। এবং এযাবৎকাল বহু আলােচিত এই লেখটির বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতৈক্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
জৈন সম্প্রদায়ের অপর একটি অভিপ্রয়াণের ফলে জৈনধর্ম মথুরায় এসেছিল। এখানে বহু সংখ্যক জৈন লেখ পাওয়া গেছে। এই লেখগুলি সর্বদা তারিখযুক্ত না হলেও অনেকগুলিতে কনিষ্কের সিংহাসন আরােহণ সূচক শকাব্দ পাওয়া গেছে। এই লেখগুলি খৃষ্টীয় ১ম এবং ২য় শতাব্দীতে জিন মূর্তি, ফলক এবং খিলানের উপর উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া মথুরায় খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে নির্মিত একটি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। এই লেখগুলিতে জৈনধর্মের জন্য ব্যক্তিগত দানের উল্লেখ আছে। এগুলি থেকে মথুরা এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠার পেছনে সমাজের সর্বস্তরের ধর্মভাবাপন্ন মানুষের সক্রিয় সমর্থন ছিল। জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য বাসস্থান এবং বস্ত্র তারা দান করেছিলেন। তাদের আনুকূল্যে আয়গপট, স্থূপ এবং মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল। এই লেখগুলিতে জৈন ধর্ম সঙঘ সংগঠনের বিভিন্ন দিকের, যেমন গণ, কুল, শাখা ইত্যাদি ভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক থেকে এই লেখগুলি জৈন ধর্ম সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়ের পরিপূরক। এই লেখ এবং ভাস্কর্য নিদর্শন থেকে জৈন সন্ন্যাসিনীদের অস্তিত্ব এবং জৈনধর্ম সংগঠনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা যায়। এই লেখগুলিতে উল্লিখিত দাতাদের মধ্যে ব্যবসায়ী, মণিহার, লৌহবণিক, গামিক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। কঙ্কালী টীলায় একটি বৃহৎ জৈন স্থূপ এবং অন্তত দুইটি জৈন মন্দির পাওয়া গেছে। এই লেখগুলির বেশির ভাগও সেখানেই পাওয়া গেছে।
আরও দক্ষিণে, উজ্জয়িনী অঞ্চল, জৈনধর্মের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মালবে জৈনধর্মের এই সম্প্রসারণের সঙ্গে হয়ত খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে সম্প্রতি কর্তৃক জৈনধর্ম গ্রহণের যােগ ছিল। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীর শকক্ষত্রপ জয়দামনের পৌত্রের (দাময়সদ অথবা প্রথম রুদ্ৰসিংহ) জুনাগড় লেখে কেবলিজ্ঞানলব্ধ এবং জরামরণমুক্ত মানুষের উল্লেখ আছে। এই নির্বাচিত শব্দসমূহ নিশ্চিতভাবে জৈনধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই লেখটি যে গুহায় পাওয়া গেছে তাতে স্বস্তিকা, ভদ্রাসন প্রভৃতি জৈন প্রতীকের ব্যবহার দেখে মনে হয় যে, এই গুহাটি জৈনদের বাসস্থান ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এই জুনাগড় লেখেই জৈন সন্ন্যাসীদের কেবলিজ্ঞান লাভের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। টঙ্কের গুহাগুলিও প্রায় একই সময়ের। এগুলোতে পার্শ্ব, মহাবীর প্রভৃতি জৈন ধর্মগুরুদের মূর্তি পাওয়া গেছে।
জৈনধর্মে মূর্তি পূজার প্রচলন মৌর্য-পূর্ব যুগেও ছিল। নন্দরাজা কর্তৃক জিন মূর্তি অপসারণের কাহিনীতে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জৈনধর্মের উৎপত্তির সময় থেকে তারা তীর্থঙ্করদের মূর্তি পূজা করতেন। তাদের এই দাবি সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও মৌর্য-শুঙ্গ যুগে যে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম একটি প্রস্তরমূর্তি জৈনধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। মস্তকবিহীন এই নগ্ন মূর্তিটি পাটনায়, লােহিয়ানপুরে পাওয়া গেছে। এর উত্তম পালিশ দেখে এটিকে মৌর্য-শুঙ্গ যুগের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। এর নগ্নতা এবং দোদুল্যমান দৃঢ় বাহুদ্বয়, জৈন তীর্থঙ্করদের কায়ােৎসর্গ মুদ্রার স্মৃতি স্মরণে আনে। মথুরায় অনেকগুলি জৈন মূর্তি এবং আয়গপট পাওয়া গেছে। এই আয়গপটগুলির কেন্দ্রস্থলে এবং প্রান্তদেশে অষ্টমঙ্গল, অর্থাৎ জৈনদের পবিত্র চিহ্নসমূহ পাওয়া গেছে। এগুলি নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীর শেষদিকে এবং খৃষ্টীয় শতাব্দীর শুরুতেই ভারতের কোন কোন অঞ্চলে জৈনদের মধ্যে মূর্তি পূজার বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। জৈনগণ শুধু যে তীর্থঙ্করদের মূর্তি পূজা করতেন, এমন নয়। আচার দিন অভিধান-চিন্তামণি প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তারা হিন্দুধর্মের দেবদেবী যেমন লক্ষ্মী, গণেশ, কুবের প্রভৃতি দেব-দেবীকেও তাদের ধর্মে গৌণ স্থান দিয়েছিলেন। তবে তাদের মূর্তিপূজার প্রধান উপজীব্য ছিলেন, আদিনাথ থেকে আরম্ভ করে মহাবীর পর্যন্ত ২৪ জন তীর্থঙ্কর। প্রতি তীর্থঙ্করের একটি লাঞ্ছন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে আদিনাথের লাঞ্ছন ছিল ষাঁড় এবং মহাবীরের সিংহ। তাছাড়া তাদের প্রত্যেকের উপাসক এবং শাসনদেবতা থাকত। জৈন গ্রন্থাদিতে এদের অনেক সময় যক্ষ এবং যক্ষিণী বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, মহাযান বৌদ্ধধর্মের ধ্যানী বুদ্ধ এবং ধ্যানী বােধিসত্ত্বদের মত, জৈন ভাস্কর্যের এই বিকাশও ধীরে ধীরে হয়েছিল।
জিন মূর্তিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। দণ্ডায়মান জিন মূর্তিগুলি দীর্ঘবাহু। দণ্ডায়মান মূর্তিগুলির এই ভঙ্গিকে কায়ােৎসর্গ মুদ্রা বলা হয়। তাছাড়া মূর্তিগুলি নরম প্রকৃতির, যৌবনের এবং নগ্ন। শ্বেতাম্বর ধর্মশাস্ত্র অনুসারে এগুলি আংশিক আবৃত। পরিপূর্ণ যক্ষ ও যক্ষিণীমূর্তিগুলি তীর্থঙ্করদের বামে ও দক্ষিণে স্থাপিত। জিন মূর্তিগুলি সর্বদাই যে দণ্ডায়মান, এমন নয়। মথুরার জাদুঘরে রক্ষিত, কুষাণ যুগে নির্মিত, অনেকগুলি মূর্তি উপবিষ্ট। তাদের আসনের নিচে স্থাপিত ধর্মচক্র, সারনাথে প্রাপ্ত বুদ্ধের ধর্মচক্রবর্তন মূর্তি মনে আনে। কুষাণ যুগের আদি তীর্থঙ্করের যে মূর্তি পাওয়া গেছে, তাতেও স্তম্ভের উপর নির্মিত অনুরূপ একটি চক্র দেখা যায়। এই যুগে নির্মিত শেষ চারজন তীর্থঙ্করের সমাধি মুদ্রায় সমাসীন মূর্তিও পাওয়া গেছে।
জৈনগণ বিদ্যাচর্চাকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন। বিদ্যাদেবীদের উপর তারা যে গুরুত্ব আরােপ করতেন, তা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে এই বিদ্যাদেবীদের সংখ্যা ছিল ষোল এবং তাদের শীর্ষে ছিলেন সরস্বতী। জৈনদের কাছে তিনি ছিলেন শ্রুতদেবতা। তিনি তীর্থঙ্করদের শ্রুত, অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের কাজ পরিচালনা করতেন। লখনৌতে একটি মস্তকবিহীন সরস্বতী মূর্তি জাদুঘরে রক্ষিত আছে। কুষাণ যুগে নির্মিত এই মূর্তির বা হাতে আছে একটি পুথি। ভারতের বিভিন্ন জৈন মন্দিরে নানাভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে নির্মিত সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিগুলির কখনও দুইটি, কখনও বা চার, ছয়, আট, এমনকি ষোলটি হাত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার হাতের সংখ্যা চার। সরস্বতীর সম্মানে জৈনগণ এখনও জ্ঞানপঞ্চমী অথবা শ্রুতপঞ্চমী অনুষ্ঠান পালন করেন।
এভাবে গুপ্ত-পূর্ব যুগ পর্যন্ত জৈনধর্মের ইতিহাস পর্যালােচনা করে সে সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য অনায়াসে করা যায় –
- প্রথমত বলা যায় যে, এই যুগে জৈন সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং সংহতি চিরকালের মত বিনষ্ট হয়েছিল।
- দ্বিতীয়ত, তখন জৈন ধর্মশাস্ত্র তার নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল, যদিও তখনও তা লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়নি।
- তৃতীয়ত, এই যুগে জৈনধর্ম বিহারের বাইরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি দক্ষিণ ভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল।
- চতুর্থত, কোন কোন দিক থেকে এই যুগই ছিল জৈনধর্মের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। তবে তার প্রভাব বৌদ্ধধর্মের মত অত ব্যাপক ছিল না।
গুপ্ত যুগে জৈন ধর্মের ইতিহাস
খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শেষাশেষি জৈনধর্ম ভারতের সর্বত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈনধর্মের আদি বাসস্থান মগধ থেকে যাত্রা শুরু করে এই ধর্ম ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্বস্থ কলিঙ্গ, পশ্চিমের মথুরা ও মালবে এবং দক্ষিণের তামিল অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম মগধের উপর তার পূর্ব অধিকারটি হারিয়েছিল। প্রথম দিকে উত্তর ভারতে, এই ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপােষকতা লাভ করেছিল। জৈনধর্মের সম্প্রসারণের পিছনে অন্যতম উপাদান হিসাবে এই পৃষ্ঠপােষকতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার অবসান ঘটেছিল। তবে সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন এই ধর্ম দীর্ঘকাল লাভ করেছিল। এভাবে উত্তর ভারতে জৈনধর্ম যা হারিয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে সে তাই ফিরে পেয়েছিল। গুপ্তযুগে সেখানকার বিভিন্ন রাজবংশ এই ধর্মের পৃষ্ঠপােষকতা করেছিলেন। বলা যায়, এ যুগে জৈনধর্মের কেন্দ্রবিন্দু উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
সাংগঠনিক দিক থেকেও এই যুগে জৈনধর্মে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বর-দিগম্বর বিভেদ তখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। এর ফলে কেবল জৈন সন্ন্যাসীগণ নন, গৃহীরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। যাপনীয়গণের মত একটি আপসমনােভাবাপন্ন গােষ্ঠী তখনও ছিল, কিন্তু তাদের গুরুত্ব খুব বেশি ছিল না। এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতে সঙ্ঘ এবং গণের মত এবং উত্তর ভারতে কূল, শাখা এবং পরবর্তীকালে গচ্ছের মত ক্ষুদ্র গােষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল। বিস্তৃত অঞ্চলে এই ধর্মের প্রসার এবং সন্ন্যাসীদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের ফলে এটাই ছিল স্বাভাবিক।
গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদের যুগে একদিকে হিন্দুধর্মের এবং অন্যদিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে, বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মেরও অবনতি ঘটেছিল। গুপ্ত যুগে জৈনধর্ম সম্পর্কিত লেখের সংখ্যা খুবই কম। ফা-হিয়েনের রচনায় এই ধর্মের কোন উল্লেখ নেই। প্রধানত রাজকীয় পৃষ্ঠপােষকতার অভাবে এই অবনতি ঘটেছিল। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই ধর্মের জনপ্রিয়তা তখনও অক্ষুন্ন ছিল। এই যুগের কয়েকটি লেখে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মথুরায় প্রাপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের একটি লেখ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযােগ্য। এতে জনৈকা মহিলা কর্তৃক একটি জৈন মৃর্তি উৎসর্গের কথা আছে। প্রথম কুমারগুপ্তর রাজত্বকালে অপর একটি লেখ মালবে, উদয়গিরিতে পাওয়া গেছে। এতে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক পার্শ্বের মূর্তি স্থাপনের কথা আছে। স্কন্দগুপ্তের সময়ের কাহায়ুম লেখে সেই গ্রামে জৈন ধর্মগুরুদের পাচটি মূর্তি স্থাপনের কথা আছে। এ এথেকে বােঝা যায় যে, সাধারণ মানুষ তখনও এই ধর্ম অনুসরণ করত এবং পূর্বের তুলনায় পশ্চিমে এই ধর্ম অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। বিহারে এবং বঙ্গদেশে এই ধর্মের তখন অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছিল। খৃষ্টীয় ৪৭৮ অব্দের পাহাড়পুর তাম্রপটে জনৈক ব্যক্তি এবং তার পত্নী কর্তৃক একটি জৈন বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূজার্চনার জন্য ভূমিয়াদানের উল্লেখ আছে। তবে এটা লক্ষণীয় যে, এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী, স্থানীয় ছিলেন না। তিনি বারাণসী থেকে সেখানে এসেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের পর হিউয়েন সাঙের রচনায় এ বিষয়ে ঈষৎ ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে বহুসংখ্যক দিগম্বর নিগ্রন্থ ছিলেন। তবে সাধারণভাবে তদকালীন ব্রাহ্মণ লেখকগণ জৈন সন্ন্যাসীদের খুব হীন চোখে দেখতেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে এবং দণ্ডিণের দশকুমারচরিতে তার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট।
পূর্বে বলা হয়েছে যে, গুপ্ত যুগে জৈনধর্ম, দক্ষিণে ভারতে রাজকীয় আনুকূল্য বিশেষভাবে পেয়েছিল। এর ফলে কন্নড় ভাষাভাষী অঞ্চলে এই ধর্ম খুবই প্রসার লাভ করেছিল। বহুসংখ্যক রাজপরিবার, মন্ত্রিবর্গ এবং ক্ষুদ্র নৃপতিদের মধ্যে এই ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজারা জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিনা, বলা যায় না, তবে তারা যে এই ধর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহীশূরের গঙ্গা রাজবংশ এই ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জৈন ধর্মগুরু সিংহনন্দিনের শিষ্য এবং তার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই জৈন ছিলেন। এই ঐতিহ্য হয়ত সর্বাংশে ইতিহাসসম্মত নয়। তবে গঙ্গাবংশের রাজাদের লেখে তাদের এই ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক পৃষ্ঠপােষকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের অবিনীত, শিবমার, শ্রীপুরুষের লেখ থেকে জানা যায় যে, তারা জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য প্রভূত দান এবং বহুসংখ্যক জৈন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাদের ব্যক্তিগত ধর্ম যাই হােক না কেন, জৈনধর্মের প্রতি তাদের উদারতা প্রদর্শনে তা কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। প্রখ্যাত জৈন লেখক পূজ্যপাদ এই বংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
বৈজয়ন্তী অথবা বনবাসীর কদম্ববংশীয় নৃপতিগণকে অনেক সময় জৈন মনে করা হয়। কিন্তু তাদের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য তথ্য থেকে এই ধারণা সত্য মনে হয় না। তবে তারা গোড়া হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও জৈনধর্মের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তারা জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য দান এবং জৈন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাদের রাজ্যের বহুসংখ্যক প্রজা জৈন মতাবলম্বী হওয়ায় হয়ত তাদের এই কাজ করতে হয়েছিল।

বাদামির চালুক্যবংশীয় নৃপতিদের জৈনধর্মের প্রতি আগ্রহের কথা জানা যায় না। দুটি লেখে প্রথম পুলকেশি এবং কীর্তিবর্মণ কর্তৃক জৈনদের জন্য দানের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই লেখ দুইটি কতটা প্রামাণ্য, তা বলা কঠিন। দ্বিতীয় পুলকেশির আইহােল লেখ থেকে জানা যায় যে, তার আশ্রিত ব্যক্তি রবিকীর্তি সেই গ্রামে জিনেন্দ্রের এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এটি মেগুটি মন্দির নামে পরিচিত। বাদামির একটি গুহায় এবং আইহােলের আর একটি গুহায় জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি পাওয়া গেছে। এই গুহা দুটি চালুক্য শাসনের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল, মনে করা হয়।
দূর দক্ষিণে, তামিল অঞ্চলে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর গােড়ার দিকে জৈনধর্মের প্রকৃত অবস্থা কি ছিল তা বলা কঠিন। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে এই অঞ্চলে জৈনধর্মের শ্রীবৃদ্ধির আভাস চাওয়া যায়। এই সাহিত্যের রচনাকাল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে। তবে এই সাহিত্য যে অনেকাংশে জৈন লেখকদের সৃষ্টি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ থেকে মনে হয় যে, এই সাহিত্য যাদের জন্য রচিত হয়েছিল, তারা অনেকেই জৈন ছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মণিমেখলাই-এ জৈন সন্ন্যাসীদের (বেশিরভাগ দিগম্বর) উল্লেখ আছে। অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ, জীবকচিন্তামণি, নীলকেশি, যশােধারাকাব্য ইত্যাদির বিষয়বস্তুও জৈনধর্ম। তবে তাদের প্রকৃত তারিখ অনিশ্চিত। বলা যায় যে, এই অঞ্চলে জৈনধর্মের বহুল প্রসারের সময় এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। সেদিক থেকে এগুলিকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্বে স্থান দিতে হয়। কেননা এই শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের বিপর্যয় শুরু হয়েছিল।
জৈন ঐতিহ্যও দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। বিখ্যাত জৈন লেখক সামন্তভদ্রের সঙ্গে কাঞ্চীর নাম যুক্ত করা হয়। দক্ষিণ ভারতের প্রথম প্রাকৃত ভাষার লেখক, দিগম্বর সাহিত্যে অতি পরিচিত কুণ্ডকুণ্ডকেও অনুরূপভাবে পল্লব রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালের সংস্কৃত অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, জৈন পণ্ডিত সর্বনন্দিন কাঞ্চীর রাজা সিংহবর্মণের রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় ৪৫৮ অব্দে তার প্রাকৃত গ্রন্থ, ‘লােকবিভাগ’ রচনা করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, কর্ণাটক থেকে আগত যে বিদেশীরা দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করেছিল তারাও জৈন ছিল।
জৈনধর্ম সম্পর্কিত ইতিহাস থেকে দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের আরও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণের জৈন সম্প্রদায় ‘মূল সঙ্ঘ’ গঠন করেছিল। পূজ্যপাদের অন্যতম শিষ্য বজ্ৰনন্দি, খৃষ্টীয় ৪৭০ অব্দে, মাদুরায় দ্রাবিড় সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন। এই সঙ্ঘ অহিংসা সম্পর্কে উদার মনােভাব গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী ঐতিহ্য অনুসারে দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর চারজন প্রশিষ্য, মাঘনন্দিন, জিনসেন, সিংহ এবং দেব মূলসঙ্ঘের মধ্যে চারটি গণের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই গণগুলির নাম ছিল যথাক্রমে, নন্দিগণ, সেনগণ, সিংহগণ এবং দেবগণ। লেখগুলির সঙ্গে এই ঐতিহ্যের বিশেষ সঙ্গতি না থাকলেও সাধারণভাবে বলা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে সুসংগঠিত জৈন সম্প্রদায় বিশেষ বিস্তার লাভ করেছিল। হিউয়েন সাঙের রচনায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, পাণ্ড্য রাজ্যে অনেক নির্গ্রন্থ ছিলেন।
খৃষ্টীয় ৭মম শতাব্দীতে শৈব এবং বৈষ্ণব সন্তগণের জোর প্রচার কার্যের ফলে জৈনধর্ম রাজানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়। দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি তখন থেকে ক্রমশ কমে আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ঐতিহ্য অনুসারে প্রখ্যাত পল্লব রাজা মহেন্দ্রবর্মণ পূর্বে জৈন ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সন্ত অপ্পরের প্রচারের ফলে শৈব ধর্মে দীক্ষিত হন।
গুপ্ত যুগে জৈনধর্মের এই বহিরঙ্গ ইতিহাসের তুলনায় তার অভ্যন্তরীণ ইতিহাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মহাবীরের মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে পাটলিপুত্রে বয়স্ক জৈনদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই সম্মেলনে ধর্মীয় অনুশাসনগুলিকে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা ফলবতী হয়নি। জৈনধর্মের অনুশাসনের বিকাশ এবং অগ্রগতি কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি। জৈন ধর্মগুরুদের রচনার ফলে একদিকে যেমন নূতন অনুশাসনের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি তার সময়ের ব্যবধানে পুরাতন অনুশাসনসমূহের স্মৃতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এই স্মৃতিকে বিপন্ন করেছে। প্রাচীন ধর্মগুরুগণ, অনুশাসনগুলিকে কণ্ঠস্থ করেছিলেন, ধীরে ধীরে তারা অবলুপ্ত হয়েছেন। এইভাবে ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে জৈনধর্মের অনুশাসনের ক্ষেত্রে ঘােরতর অনিশ্চয়তার হয়েছিল। অনুশাসনগুলি পুনরুদ্ধার করে এই সঙ্কটের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর গােড়ার দিকে দুই বার হয়েছিল। প্রথমবার মথুরায় চেষ্টা করেছিলেন স্থাণ্ডিল। দ্বিতীয়বার অনুরূপ চেষ্টা করেছিলেন নাগার্জুন, বলভীতে। কিন্তু কোন প্রয়াসই সার্থক হয়নি।
খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে বলভীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলন অনেক বেশি সফল হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, বলভীর মৈত্রক বংশের রাজা প্রথম ধ্রুবসেনের রাজত্বকালে এবং তার পৃষ্ঠপােষকতায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই অনুমান হয়ত সত্য নয়। কেননা মৈত্রক বংশের লেখ ইত্যাদিতে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। এই বংশের রাজাদের জৈনধর্ম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল, তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সম্মেলনকে একান্তভাবে জৈনধর্ম সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত মনে হয়। এই সম্মেলনে জৈনধর্মের অনুশাসন তার বর্তমান আকার লাভ করেছিল। এই সম্মেলনের গুরুত্ব এইখানে। এই অনুশাসনগুলি প্রায় সবই প্রাচীন, তবে এই সম্মেলনে সেগুলির নতুন শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছিল। এই বিন্যাস অনুসারে জৈনধর্মগ্রন্থগুলি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীগুলি হল, অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্ৰাকীর্ণক, ছেদসূত্র এবং মূলসূত্র। ষষ্ঠ শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট নামকরণ এই সম্মেলনে করা হয়নি।
গুপ্ত যুগে জৈন সন্ন্যাসীদের কৃতিত্ব শুধু এক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধর্মীয় সাহিত্যের সহায়ক গ্রন্থাদি রচনায়ও তারা যথেষ্ট উৎসাহ ও যােগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পূর্বতন ছন্দোবদ্ধ টীকা, যাকে নিযুক্তি বলা হত, এ যুগে তাদের নতুন রূপ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া ভাষ্যাকারে তারা পরিবর্ধিত হয়েছিল। সঙ্ঘদাস, জিনদাস এবং সিদ্ধসেন নামক পণ্ডিতগণ এই কাজ করেছিলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন বিষয়ক গ্রন্থের প্রাকৃত ভাষায় টীকা অর্থাৎ চুর্ণী, এই যুগে রচিত হয়েছিল। এ যুগের জৈন পণ্ডিতদের মধ্যে। প্রাকৃতের পরিবর্তে, সংস্কৃত সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। কেননা সংস্কৃতের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মীয় গােষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলােচনা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাছাড়া তখন প্রাকৃতের তুলনায় সংস্কৃতের মর্যাদাও বেশি ছিল। তাই প্রাচীন প্রাকৃত টীকার পরিবর্তে এখন সংস্কৃত টীকা রচিত হয়েছিল। প্রখ্যাত জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র তার গ্রন্থাদি এবং টীকা সংস্কৃতে লিখেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে দিগম্বর জৈনগণ প্রাকৃত এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেছিল। দিগম্বর লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কুণ্ডকুণ্ড খৃষ্টীয় শতাব্দীর গােড়ার দিকের মানুষ ছিলেন। তিনি প্রাকৃত ভাষায় তার গ্রন্থাদি লিখেছিলেন। গুপ্ত যুগের পালি ভাষায় লেখকদের মধ্যে বট্টকের, স্বামী কার্তিকেয়, যতিবৃষভ প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযােগ্য। এ যুগে সংস্কৃত ভাষায় যারা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে পূজ্যপাদ, অকলঙ্ক, মহাতুঙ্গ প্রভৃতি প্রধান। এ যুগের জৈন দর্শন বিশেষভাবে ন্যায়শাস্ত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুপ্ত যুগে জৈনদের মধ্যে পূর্বের মত মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরি গুহায় উৎকীর্ণ তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়
পূর্বে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, এখানে এই দুই ধারার পার্থক্য একটি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। জৈনরা বেদ ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা। প্রত্যেক জীবই জিনদের পন্থা অনুসরণ করে বন্ধনমুক্ত হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। দার্শনিক দৃষ্টিতে জৈনদের নিজেদের মধ্যে কোন ভেদ না থাকলেও পরবর্তীকালে আচারগত দৃষ্টিতে কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ায় জৈনধর্ম দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। জৈনমতের এই দু’টি অবান্তর ভেদ হচ্ছে- শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বর সম্প্রদায়ের যতি বা সন্ন্যাসীরা নিজ শরীরের আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রের উপযোগ গ্রহণ করেন না, তারা সর্বদা নগ্ন থাকেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের যতিরা সাদা বস্ত্র পরিধান করেন। আচারগত ধর্মানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি ভিন্নতা ছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মূল ধর্মসূত্র একই।
নিজ নিজ প্রাচীনত্ব নিয়েও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে প্রাচীন বলে প্রচার করেন। দিগম্বররা বলেন, ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্বেতাম্বরের উৎপত্তি। কিন্তু শ্বেতাম্বররা মনে করেন, ৮২ খ্রীষ্টাব্দে দিগম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অনুশ্রুতি অনুসারে বর্ধমান মহাবীরের পরিনির্বাণের (৫২৭ খ্রীষ্টপূর্ব) ৬০৯ বছর পর ৮২ খ্রীষ্টাব্দে শিবভূতি নামে এক আচার্য ছিলেন যাকে আর্যরক্ষিত জৈনধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। একদা শিবভূতির নিবাসস্থান রথবীরপুরের রাজা শিবভূতিকে একটি মহামূল্য পোশাক উপহার দেন। মুনি আর্যরক্ষিত তার শিষ্যকে সেই পোশাক পরিহিত দেখে তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন। গুরুর অভিপ্রায় বুঝে শিবভূতি নির্বসন হয়েই অবস্থান করেন। এথেকেই দিগম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।
তবে এটাও জানা যায় যে, পার্শ্বনাথ বস্ত্র পরিধানের বিরোধী ছিলেন না। তিনি শ্বেত বস্ত্র পরিধান অনুমোদন করতেন। কিন্তু মহাবীর বর্ধমান অত্যন্ত বৈরাগ্যবান হওয়ায় বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন এবং তার মতে নগ্ন থাকাই যতির আদর্শ। এসব ঘটনা থেকে অনুমান হয়, পরবর্তীকালের বিভক্ত শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক জৈন সম্প্রদায়ের ভেদবীজ বহুপূর্ব থেকেই সুপ্তভাবে বর্তমান ছিলো। পার্শ্বনাথ অহিংসা (non-violence), সত্য (truthfulness), অস্তেয় (non-stealing) ও অপরিগ্রহ (non-attachment) এই চারটি মহাব্রত স্বীকার করতেন। মহাবীর এর সাথে ব্রহ্মচর্য (celibacy)-কে অন্তর্ভুক্ত করে পাঁচটি মহাব্রত (five great vows) স্বীকার করেছেন, যা সম্যক চরিত্রের জন্য পালন করতে হয়।

মহাবীরের পরিনির্বাণের পরে দুশো বছর পর্যন্ত ভিক্ষুগণ ক্ষুদ্র একটি গণ বা সঙ্ঘে থাকতেন। মৌর্যযুগে জৈনধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিলো। জৈনমত অনুসারে, ক্রমাগত অনাবৃষ্টির দরুন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হলে রাজত্ব ত্যাগ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪-৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই সময় এক নাগাড়ে ১২ বছর দুর্ভিক্ষ হলে জৈন ভিক্ষুদের এক অংশ আচার্য ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে নিষ্ক্রমণ করেন। অন্যেরা স্থূলভদ্রের পরিচালনায় মগধে থেকে যান।
সেই নিষ্ক্রমণ থেকে ভিক্ষুদের নিয়মাবলী নিয়ে জৈনমতে বিভাগ দেখা দিয়েছিলো। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জৈনসঙ্ঘের নেতা সঙ্ঘভদ্রের পরিশোধিত আচার গ্রহণ করেই শ্বেতাম্বরগণ দিগম্বর হতে পৃথক হন। মানুষের দুর্বলতার ধরন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিরীক্ষণ করে এবং উগ্র তপস্যা ও কঠোর আচার পালনাদি সম্ভব নয় ভেবে সঙ্ঘভদ্র সর্বজনের পালনীয়রূপে আচারের কিছু সংশোধন করেন। সেই সময় থেকেই মূলত দু’টি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে। তখন মগধে অবস্থিত জৈনসঙ্ঘের নেতা স্থূলভদ্র দুর্ভিক্ষের কারণে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ ভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পড়তে অনুমতি দেন। দুর্ভিক্ষের পর ভদ্রবাহু মগধে ফিরে এলে যারা পূর্বের মতো শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন তারা শ্বেতাম্বর নামে অভিহিত হন। আর যারা নগ্ন থাকতেন তারা দিগম্বর সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হন। তখন থেকেই প্রাকৃতিক কারণে দিগম্বর সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতে এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় উত্তর ভারতে প্রাধান্য পায়।
জৈনদের মৌলিক বিষয়ে কোন ভেদ না থাকলেও কিছু অদ্ভুত গৌন আচার বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্নতা ছিলো। এই দুই সম্প্রদায়ের ভেদ উল্লেখ করে মাধবাচার্য্য ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে বলেন- ‘ধূলি পরিষ্কারক সম্মার্জনী ধারণকারী যিনি ভিক্ষান্ন ভোজন ও কেশমুণ্ডন করেন, সেই ক্ষমাশীল আসক্তিশূন্য জৈনমুনি শ্বেতাম্বর। অন্যদিকে মুণ্ডিতমস্তক, সম্মার্জনী ধারণকারী যিনি নিজের হাতকেই পাত্ররূপে ব্যবহার করে দাতৃগৃহে উর্ধ্বমুখে আহার করেন তিনি হচ্ছেন দিগম্বর জৈনঋষি।’
দিগম্বরমতে তীর্থঙ্করগণ কোন বস্তু সংগ্রহ করেন না এবং কেবল-জ্ঞানী বলে ভোজন না করেই বাস করেন। তাদের মতে বস্ত্রধারী সম্পত্তিযুক্ত সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু মোক্ষলাভে অধিকারী নয় এবং স্ত্রীর মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্যতার জন্য পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক। বিপরীতে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এতোটা কঠোর নয়। তারা শ্বেতবস্ত্র ধারণকে অনিবার্য মনে করেন। তাদের মতে মহাবীরের শিষ্যদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ, গৃহী, ভিক্ষু সকলেই ছিলো। শিষ্যরা সঙ্ঘ গঠন করে একাদশ গণে বিভক্ত হয়ে অপসর নামক আশ্রমে বসবাস করতো। প্রত্যেক গণে একজন গণধর নামে নেতা থাকতো।
মহাবীরের পরিনির্বাণের পর তার প্রধান অনুগামীরা দীর্ঘকাল যাবৎ সঙ্ঘকে রক্ষা করেছিলেন। ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভদ্রবাহু এবং ৩১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্থূলভদ্র সঙ্ঘপ্রধান হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সময়কাল নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা যায়। কেননা জৈনদের ‘পট্টাবলি’ অনুসারে স্থূলভদ্রের পরলোক গমন নন্দ বংশের নবম নন্দের মৃত্যুকালে (৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব) হয়েছে বলে বলা হয়। এছাড়া ভদ্রবাহুর সময়কালও ৪৩৩-৩৫৭ খ্রীষ্টপূর্বে। আচার্য স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে জৈনশাস্ত্র সংগ্রহ হয়েছিলো। এই সময়েই জৈনরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। সেই থেকে এরপর সতেরোশো খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রখ্যাত জৈনপণ্ডিত দার্শনিকগণ কর্তৃক বিভিন্ন জৈনগ্রন্থ রচিত হয়।
জৈন সাহিত্য
জৈনাচার্যদের মতে জৈনধর্ম চিরন্তন। প্রবহমান কালস্রোতে বহু তীর্থঙ্কর এসেছেন এবং জৈনমত উজ্জীবিত করেছেন। এ পরম্পরায় উল্লেখকৃত চব্বিশজন তীর্থঙ্করের চব্বিশতম ও অন্তিম তীর্থঙ্কর হচ্ছেন মহাবীর বর্ধমান। জৈন ঐতিহ্য থেকে জানা যায়, মহাবীরের সময়কাল থেকে জৈনাচার্য ভদ্রবাহুর (৪৩৩-৩৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব) সময় পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর জৈনসাহিত্য জৈনভিক্ষুদের শ্রুতিপরম্পরায় প্রচলিত ছিলো। আবার জৈন অনুশ্রুতি অনুসারে ইন্দ্রভূতি গৌতম (৬০৭-৫১৫ খ্রীষ্টপূর্ব) নামে মহাবীরের শিষ্য ‘চতুর্দশপূর্ব’ নামে পরিচিত জৈনধর্মের মূল বিষয়গুলোকে ‘দৃষ্টিবাদ’ নামক আগম বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থে সঙ্কলন করেছিলেন। জৈনদের ‘পট্টাবলি’ অনুসারে আচার্য স্থূলভদ্রের (মৃত্যু ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব) কাল পর্যন্ত গ্রন্থটি বিদ্যমান ছিলো, তারপর তা বিলুপ্ত হয়। অনুশ্রুতি অনুযায়ী উল্লিখিত জৈনাচার্যদের সময়কাল ও অনুমিত সালগননায় পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি, গরমিল ও বিতর্ক থাকলেও প্রাচীনত্ব অনুমানে সন্দেহ নেই।
‘সিদ্ধান্ত’— বা ‘আগম’ জৈনদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। প্রথমতম লেখক হচ্ছেন আচার্য ভদ্রবাহু। তিনি দশাবয়ব ন্যায়ের প্রবর্তক। তিনি জৈন তর্কশাস্ত্রের বিধি নিয়ে রচিত ‘দশবৈকালিকসূত্রে’র ওপর প্রাকৃত ভাষায় ‘দশবৈকালিকনির্যুক্তি’ নামক ব্যাখ্যা বা ভাষ্য রচনা করেন। তিনি ‘জৈনশ্রুতকেবলী’ অর্থাৎ দৃষ্টিবাদের ‘চতুর্দশপূর্বে’র তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি আবশ্যকসূত্র, উত্তরধ্যানসূত্র, আচারসুত্র ও কল্পসূত্রের ব্যাখ্যা লেখেন এবং সূত্রকৃতাঙ্গনির্যুক্তিতে স্যাদ্বাদের বিশদ ব্যাখ্যা করেন।
৩৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আচার্য ভদ্রবাহুর পরলোক গমনের পর আচার্য স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে একটি সভা আহ্বান করেন। তাতে ১১টি অঙ্গ পুনরায় স্থিরীকৃত হয় এবং দ্বাদশতম অঙ্গ ‘চতুর্দশপূর্ব’ দ্বারা গঠিত হয়। এ সময়েই জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এ সভায় পুনঃসংগঠিত জৈন শাস্ত্রগুলি শ্বেতাম্বরগণ গ্রহণ করেন। কিন্তু দিগম্বরগণ বলেন যে, প্রাচীন শাস্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে, তার পুনর্রচনায় যত্নশীল হতে হবে।
দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর সময়কাল প্রথম খ্রিস্টাব্দ। দিগম্বর সম্প্রদায় মতে দ্বিতীয় ভদ্রবাহু ৭৯ খ্রিস্টাব্দে দৃঢ়ভাবে দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। যদিও তার পূর্বেই এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিলো।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য দূর করার জন্য পঞ্চম শতাব্দীতে (৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) দেবর্দ্ধিগণির সভাপতিত্বে গুজরাটের বল্লভীরূপে একটি সভা ডাকা হয়। তিনি প্রথম জৈন সম্প্রদায়ের মূলসূত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পূর্বে সংগৃহীত দ্বাদশ অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হওয়ায় তার লিপিবদ্ধ এগারোটি অঙ্গ এই সভায় গৃহীত হয়, যা এখনো প্রচলিত আছে। সভায় চুরাশিটি (৮৪) সাহিত্য অনুমোদিত হয়েছিলো। এর মধ্যে ৪১ টি সূত্রগ্রন্থ, ১২ টি নির্যুক্তি, ১টি মহাভাষ্য, ১০ টি প্রকীর্ণ, ৬ টি ছেদসূত্র, ৪ টি মূলসূত্র, ১ টি অন্তযোগদ্বারসূত্র এবং ১ টি নন্দীসূত্র।
৪১ টি সূত্রকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন ১১ টি অঙ্গ, ১২ টি উপাঙ্গ, ৬টি ছেদ, ৪টি মূল এবং ৮টি বিবিধ। এগারোটি অঙ্গসূত্র হচ্ছে- (১) আচারাঙ্গসূত্র, (২) সূত্র (সৌত্র্য) কৃতাঙ্গ, (৩) স্থানাঙ্গ, (৪) সমবায়াঙ্গ, (৫) ভগবতী, (৬) জ্ঞাতৃধর্ম কথা, (৭) উপাসকদশা, (৮) অন্তকৃদ্দশা, (৯) অনুত্তরৌপপাতিকদশা, (১০) প্রশ্নব্যাকরণ, (১১) বিপাকশ্রুত। বারোটি উপাঙ্গ হচ্ছে- (১) ঔপপাতিক, (২) রাজপ্রশ্নীয়, (৩) জীবাভিগম, (৪) প্রজ্ঞাপনা, (৫) জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, (৭) সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, (৮) নিরয়াবলি, (৯) কল্পাবতংসিকা, (১০) পুষ্পিকা, (১১) পুষ্পচুলিকা, (১২) বন্দিদশা। দশটি প্রকীর্ণ হচ্ছে- (১) চতুঃশরণ, (২) সংস্তরক, (৩) আতুরপ্রত্যাখ্যান, (৪) ভক্তাপরিজ্ঞা, (৫) তণ্ডুলবৈয়াসীয়, (৬) চন্দ্রবেধ্যক, (৭) দেবেন্দ্রস্তব, (৮) পণিবীজ্জা, (৯) মহাপ্রত্যাখ্যান, (১০) বীরস্তব। ছয়টি ছেদসূত্র হচ্ছে- (১) নিশীথ, (২) মহানিশীথ, (৩) ব্যবহার, (৪) দশাশ্রুতস্কন্ধ, (৫) বৃহৎকল্প, (৬) পঞ্চকল্প। চারটি মূলসূত্র হচ্ছে- (১) উত্তরাধ্যয়ন, (২) দশবৈকালিক, (৩) আবশ্যক, (৪) পিণ্ডনির্যুক্তি।
প্রাচীন এই জৈনগ্রন্থগুলির ভাষা অর্ধমাগধী প্রাকৃত। মহাবীর এ ভাষাতেই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে জৈনদার্শনিকরা দার্শনিক তত্ত্বালোচনার লক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষাকে প্রাধান্য দেন। প্রথম খ্রীষ্টাব্দ থেকে জৈনগণ গ্রন্থ রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। এই দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজনেই অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনাও লেখা হতে থাকে। তাই জৈনদের বারোটি উপাঙ্গের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম উপাঙ্গে গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা রয়েছে। দিগম্বরমতে ৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জৈনশাস্ত্র লিখিত হয়েছে। এরপর থেকে জৈনশাস্ত্রে সাতটি তত্ত্ব, নয়টি পদার্থ, ছয়টি দ্রব্য, পঞ্চ অস্তিকায় প্রভৃতি আলোচনা শুরু হয়।
দর্শনের প্রমাণশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রে জৈনদর্শনের অবদান অপরিসীম। জৈনদার্শনিকরা ধর্ম দর্শন নীতি এবং এই প্রমাণ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রখ্যাত সেসব জৈনদার্শনিকদের মধ্যে কুন্দকুন্দাচার্য (৫০ খ্রিস্টপূর্ব), ‘বাচক শ্রবণ’ নামে খ্যাত উমাস্বাতি বা উমাপতি (০১-৮৫ খ্রি.), সমন্তভদ্র (ষষ্ঠ শতক) – এই তিনজন জৈনাচার্য জৈনদর্শনকে সুব্যবস্থিত করেছেন। কুন্দকুন্দাচার্য ‘নিয়মসার’, ‘পঞ্চাস্তিকায়সার’, ‘সময়সার’ ও ‘প্রবচন’ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এরমধ্যে শেষ তিনটির মহত্ত্ব হচ্ছে ‘প্রস্থানত্রয়ী’র মতো।
উমাস্বাতি ন্যগ্রোধিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম স্বাতি এবং মাতার নাম উমা। তিনি কৌভিষণি গোত্রীয় ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধবাচার্যে ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে তাকে ‘উমাস্বাতি বাচকাচার্য’ বলা হয়েছে। তার বাসস্থান ছিলো মগধ। তিনি পাটলিপুত্রে তার রচিত ‘তত্ত্বার্থসূত্র’ বা ‘তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে’র ব্যাখ্যা রচনা করেন। তিনি জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ নামে সাতটি তত্ত্ব স্বীকার করেন। সমন্তভদ্র ‘তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে’র উপর ‘গন্ধহস্তিমহাভাষ্য’ নামক টীকাভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই ভাষ্যের সূচনাংশ ১৪টি কারিকায় ‘আপ্তমীমাংসা’ নামে পরিচিত। বাচস্পতি মিশ্র (৮৪১ খ্রি.) তা থেকে স্যাদ্বাদের আলোচনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সমন্তভদ্রের অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে ‘যুক্ত্যনুসন্ধান’ ১৪৩ পদ্যে তীর্থঙ্করদের স্তুতিমূলক ‘স্বম্ভূস্তোত্র’, ‘জিনস্তুতিশতক’, ‘রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার’ ইত্যাদি। সমন্তভদ্র ছিলেন দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। সিদ্ধসেন দিবাকর ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি (৪৮০-৫০০ খ্রি.) ‘তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে’র ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ন্যায়াবতার’ এবং জৈনদর্শনের উপর প্রাকৃত ভাষায় ‘সম্মতিতর্কসূত্র’ রচনা করেন। তারমধ্যে প্রথমটি ৩৬ সংখ্যক কারিকায় ন্যায়গ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টি (তর্ক) ন্যায়শাস্ত্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থ। তিনি জীবকে জ্ঞাতা ও (আত্মা ও অনাত্মার) প্রকাশক বলে প্রতিপাদন করেছেন। তিনি জৈনন্যায়ের অবতারণা করেন, যার গ্রন্থান্তর হচ্ছে ‘কল্যাণমন্দিরস্তোত্র’।
পূজ্যপাদ দেবনন্দী (৫০০ খ্রি.) যাকে বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধির সাথে অভিন্ন মনে করা হয়, ‘তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে’র ‘সর্বার্থসিদ্ধি’ নামক টীকা লেখেন।
অকলঙ্কদেব (ষষ্ঠ শতক) ‘আপ্তমীমাংসা’র টীকা ‘অষ্টাশতী’, ‘ন্যায়বিনিশ্চয়’, ‘তত্ত্বার্থবার্ত্তিকব্যাখ্যানালঙ্কার’, ‘লঘীয়স্ত্রয়’, ‘স্বরূপসম্বোধন’ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। মীমাংসক কুমারিল ভট্ট (৬৪০-৭০০ খ্রি.) সমন্তভদ্র ও অকলঙ্কদেবের জৈনমতকে উদ্ধৃত করে খণ্ডন করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে কুমারিলের খণ্ডনকে বিদ্যানন্দ (অষ্টম শতক) ও প্রভাচন্দ্র (৮২৫ খ্রি.) প্রতিরোধ করে জৈনমত মন্ডিত করেন।
বিদ্যানন্দ (অষ্টম শতক) পাটলিপুত্রের দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি ‘পাত্রকেশরী স্বামী’ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনমতের প্রধান প্রধান গ্রন্থের ও মতের আলোচনা করেন। তিনি ‘আপ্তমীমাংসা’র ব্যাখ্যা ‘আপ্তমীমাংসালঙ্কৃতি’ বা ‘অষ্টসাহস্রী’, ‘প্রমাণপরীক্ষা’ রচনা করেন।
আর প্রভাচন্দ্র (৮২৫ খ্রি.) মাণিক্যনন্দীর ‘পরীক্ষামুখসূত্র’র উপর সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড’ এবং অকলঙ্কদেবের ‘লঘীয়স্ত্রয়ে’র উপর টীকা ‘ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়’ রচনা করেন।
মানিক্যনন্দী (৭৫০-৮০০ খ্রি.) দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রমাণ নিয়ে ‘পরীক্ষামুখসূত্র’ প্রণয়ন করেন। আর বাদিরাজ সূরি (নবম শতক) কর্তৃক রচিত ‘ন্যায়বিনিশ্চয়নির্ণয়’ হচ্ছে জৈন ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অভয়দেব সূরি (নবম-দশক শতক) ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন। তার রচিত জৈন ন্যায় নিয়ে গ্রন্থ ‘বিবাদমহার্ণব’ এবং সিদ্ধসেন দিবাকরের ‘সম্মতিতর্কসূত্রে’র উপর ব্যাখ্যা ‘তত্ত্বার্থবোধবিধায়িনী’ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

অনন্তবীর্য (একাদশ শতক) ছিলেন দিগম্বর জৈন। তিনি মাণিক্যনন্দীর ‘পরীক্ষামুখসূত্রে’র ওপর ‘পরীক্ষামুখপঞ্জিকা’ বা ‘প্রমেয়রত্নমালা’ রচনা করেন। মাধবাচার্য্যরে (চতুর্দশ শতক) সর্বদর্শনসংগ্রহে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হেমচন্দ্র সূরি (১০৮৮-১১৭২ খ্রি.) টীকাসহ ‘প্রমাণমীমাংসা’ ‘বীতরাগস্তুতি’ ও ‘আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার’ গ্রন্থ রচনা করেন। হেমচন্দ্রের সমসাময়িক দেবসূরি (একাদশ শতক) ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন। তার উপাধি ছিলো ‘বাদিপ্রবর’। তিনি জৈন ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে ‘প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার’ ও টীকা ‘স্যাদ্বাদরত্নাকর’ রচনা করেন। এছাড়া চন্দ্রপ্রভ (১১০০ খ্রি.) রচিত দুটি জৈনগ্রন্থ হলো ‘দর্শনশুদ্ধি’ ও ‘প্রমেয়রত্নকোশ’।
‘কলিকাল গৌতম’ নামে খ্যাত হরিভদ্র সূরি (দ্বাদশ শতক) ছিলেন আনন্দ সূরির শিষ্য। তিনি চিত্রকূটে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে জৈনধর্ম গ্রহণ করে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ‘ষড়্দর্শনসমুচ্চয়’, ‘ন্যায়াবতারবিবৃতি’, ‘যোগবিন্দু’, ‘ধর্মবিন্দু’ প্রভৃতি। তার যোগবিন্দু ও ধর্মবিন্দু এবং সকলকীর্ত্তির (১৪৬৪ খ্রি.) রচিত ‘প্রশ্নোত্তরোপাসকাচার’-এ জৈন ও সাধারণ লোকের কর্তব্য বলা হয়েছে।
হেমচন্দ্র সূরির ‘বীতরাগস্তুতি’র টীকা ‘স্যাদ্বাদমঞ্জরী’ রচনা করেন মল্লিসেন (১২৯২ খ্রি.)। নেমিচন্দ্রের দার্শনিক গ্রন্থ হলো ‘দ্রব্যসংগ্রহ’। রাজশেখর সূরি (১৩৮৪ খ্রি.) রচিত নানান গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ‘স্যাদ্বাদকলিকা’ ও শ্রীধরের ‘ন্যায়কন্দলী’র উপর টীকা ‘পঞ্জিকা’। আর যশোবিজয়গণি (১৬০৮-১৬৮৮ খ্রি.) কর্তৃক রচিত শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ‘ন্যায়প্রদীপ’, ‘জৈনতর্কভাষা’, ‘ন্যায়রহস্য’, ‘ন্যায়ামৃততরঙ্গিনী’ ও ‘ন্যায়খন্ডখাদ্য’। দর্শনশাস্ত্র এসব দার্শনিকদের মহত্তপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ।
বৌদ্ধ ধর্ম
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান হয়েছিল।
- বৈদিক ব্রাহ্মণ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান ঘটেছিল।
- 663 খ্রিস্টপূর্বাব্দে কপিলাবস্তুর লুম্বিনী গ্রামে (সিংহলী মতে 566 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন।
- গৌতম বুদ্ধ প্রথম ঋষিপত্তনে যার বর্তমান নাম সারনাথ ধর্ম প্রচার করেছিলেন।
- গৌতম বুদ্ধ 483 খ্রিস্টপূর্বাব্দে 80 বছর বয়সে কুশিনগর(মল্ল)এ দেহত্যাগ করেন।
- গৌতম বুদ্ধের দেহত্যাগ এর মহাপরিনির্বাণ নামে পরিচিত।
- আসক্তি বিনাশের জন্য বুদ্ধ আটটি যা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত পথের কথা বলেছেন ।
- ত্রিপিটক হল – বিনয় পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধর্ম পিটক।
- ত্রিপিটক পালি ভাষায় লেখা।
- বুদ্ধদেবের উপদেশ গুলি প্রাকৃত বা অর্ধমাঘধি ভাষায় রচিত।
-
প্রথম রাজগৃহ অজাত শস্ত্রু মতান্ত্ররে মহাকাশ্যপ 483 খীষ্ট-পূর্বাব্দে হর্যঙ্ক বংশের সময় দ্বিতীয় বৈশালী কালাশোক 83 খীষ্ট–পূর্বাব্দে শিশুনাগ বংশের সময় তৃতীয় পাটলিপুত্র অশোক(জলন্ধর কুন্দলবন বিহার 251 খীষ্ট-পূর্বাব্দে মৌর্য বংশের সময় চতুর্থ কাশ্মির কনিষ্ক 98 খীষ্টাব্দে কুষান বংশের সময় মানব সভ্যতা বিকাশের ধারায় প্রতিটা আবিষ্কারই ছিল যুগান্তকারী; আর এর অভিঘাতে সমাজও হয়েছে বহুবিবর্তিত। এক সময়ে আগুনের ব্যবহার ও আবিষ্কার যেমন নবদিগন্তের সূচনা করে, তেমন ভাবেই লােহার আবিষ্কার ও ব্যবহার (দশম-নবম খ্রি. পূ.) আনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফলে সনাতনী সমাজ ব্যবস্থা নতুনভাবে বিন্যস্ত হতে থাকে। চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থায়। অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বৃত্তি-বিভাজনও পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকে। শুক্ল যজুর্বেদের কালে সমাজে আটান্ন (৫৮) প্রকারের বৃত্তির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, এর মধ্যে সাতটা বৃত্তি কেবল মাত্র নারীজাতির জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। সেই যুগে এইরকম উন্নত সমাজ, জীবনযাত্রা ব্যবস্থা ও এতগুলাে বৃত্তি ও কুটীর শিল্পের কথা ভাবলেও বিস্ময়ে স্তব্ধ হতে হয়।
সমাজে অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরকালই ছিল; এতদিন তা ছিল মূলত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এখন বৈশ্য শ্রেণির উদ্ভব হয়। ক্রমে এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বলে বলীয়ান হয়ে তৃতীয় শক্তিরূপে হাত বাড়ায় রাজশক্তির দিকে। এতদিনে বণিকের মানদণ্ড হল—রাজদণ্ডের অভিলাষী। এরা নিজেদের সংগঠিত করে জৈন ধর্মে, যার প্রথম তীর্থঙ্কর—ঋষভদেব। এরা সেই সেদিন থেকে আজও কঠোরভাবে নিরামিষাশী।
এই সময়ে ভারতবর্ষে কোনও রকম রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। এক অখণ্ড রাষ্ট্রের পরিবর্তে বহু ছােট ছােট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, ক্রমে যা পরবর্তীকালে ষােড়শ মহাজনপদের রূপ নেয়। আবার এরাও প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। ক্রমে ষােড়শ মহাজনপদ ভাঙতে ভাঙতে মগধ, কোশল, বৎস ও অবন্তী – এই চারে এসে দাড়ায়, ও শেষে মগধের ছত্রছায়ায় স্থান পায়। এর পেছনে অনেক কারণের মধ্যে লােহার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতে লােহার খনিগুলাে প্রধানত বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পূর্ব অংশেই বিখ্যাত।
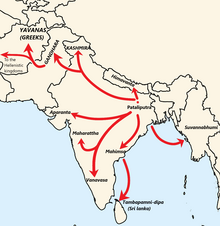
-
আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সমাজের এই বহু বিবর্তনের ধাক্কাকে সামাল দিতে বিবর্তিত ও বিবর্ধিত হতে থাকে সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক ও উপনিষদে। কিন্তু আর্য সংস্কৃতির মূল যে যাগ-যজ্ঞ তাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হয় বিপুল থেকে বিপুলতর ভাবে। ফলে ধর্ম-কর্ম (যাগ-যজ্ঞ ও বলিদান) সর্বসাধারণের সাধ্যের অতীত হয়ে যায়। রাজা-রাজড়া ও ধনাঢ্য লােকেরাই একমাত্র এই বিপুল আয়ােজনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম ছিল। নিরুপায় সাধারণ মানুষ তখন ধর্মকর্মের প্রয়ােজনে ও আকাঙ্ক্ষায় অনার্য জাতির মধ্যে প্রচলিত সরল অনাড়ম্বর ও ব্যয়বাহুল্যতাহীন পূজা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে থাকে। এই সময়কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে ষাটটা প্রতিবাদী ধর্ম মাথা তুলে দাঁড়ায়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম হল জৈন ধর্ম, এ ছাড়াও চার্বাক, জাবালি, কপিল, আজীবক ইত্যাদিরাও ছিলেন। এদের বক্তব্যের চমৎকারিত্বে বহু মানুষ আকৃষ্ট হয়ে বিপথগামী হতে থাকে ও দলে দলে লােক সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে। এর পরে সর্বশেষ আঘাতটা হানেন—স্বয়ং বুদ্ধদেব। ফলে সমাজ চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।
আগেও আলােচনা করা হয়েছে যে– লােহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে উদ্বৃত্ত পণ্যের বিপণনের প্রয়ােজনীয়তায় বৈশ্যশ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ, আর্থিক বলে বলীয়ান হওয়া ও সবশেষে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তৃতীয় শক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়। জৈন ধর্মের সংগঠিত এই শক্তির হুমকিতে সনাতনী সমাজ ব্যবস্থা থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এই সময় থেকে যাগ-যজ্ঞে গবাদি পশুর বলি রূপে ব্যবহার ক্রমশ কমতে থাকে; আর আজ তা প্রতীকে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় সেদিনের সেই সমগ্র আর্যাবর্ত (সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারত) আজ নিরামিষাশী। এরও বহু বহু পরবর্তীকালে সম্রাট অশােক, তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি কালে ঘােষণা করেন যে, তার সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে যাগ-যজ্ঞের নামে গবাদি পশু বধ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে ধীরে ধীরে কমতে কমতে আসা যাগ-যজ্ঞে বলি প্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল; তার পরিবর্তে শুরু হল (বলিতে) প্রতীকের ব্যবহার (আখ বলি, চাল কুমড়া বলি, শসা বলি, নারিকেল বলি ইত্যাদি)।
এই ধর্ম, অর্থ ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে বুদ্ধদেব (সম্ভবত ৫৬৩ খ্রি. পূ.) উপলব্ধ, সত্য-জ্ঞান প্রচার করেন। তিনি নিজে তার প্রচারিত উপলব্ধিকে ‘সদ্ধর্ম’ বলতেন। পরবর্তীকালে যা বৌদ্ধ ধর্মদর্শন নামে তার শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা দেশে দেশে প্রচারিত হয়।
বুদ্ধের উপদেশাবলির মূল চার সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনটে হল অস্বীকারাত্মক আর মাত্র একটা হল স্বীকারাত্মক –
১. ঈশ্বরকে অস্বীকার করা, অন্যথায় ‘মানুষ স্বয়ং নিজের প্রভু’—এই সিদ্ধান্তের বিরােধিতা করা হয়।
২. আত্মাকে নিত্য স্বীকার না করা; তা না হলে নিত্য একরস মানলে তার পরিশুদ্ধি ও মুক্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না।
৩. কোনও গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করা, তা না হলে বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।
৪. জীবনপ্রবাহকে এই শরীরের মধ্যেই সীমিত মনে করা, নতুবা জীবন ও তার নানা বৈচিত্র্য কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন না হয়ে, স্রেফ এক আকস্মিক ঘটনা বলে প্রতিভাত হবে। (বৌদ্ধ দর্শন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন।)বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও দর্শন এই চার সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যার প্রথম তিনটে সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা করে। তবে এই তিন সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্ম ও বস্তুবাদে সমান ভাবে বর্তমান। তবে চতুর্থ সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্মকে বস্তুবাদ থেকে আলাদা করে; আর সেই সঙ্গে ব্যক্তির ভবিষ্যৎকে আশাপ্রদভাবে দেখাবার এক সুন্দর প্রচেষ্টা; যা না থাকলে কোনও আদর্শবাদই কার্যকরী রূপ পেতে পারে না। তা হলে বৌদ্ধ ধর্মের মূল চারটে সিদ্ধান্তের সারাৎসার হল—মানুষকে (প্রথম তিন সিদ্ধান্তে) তিনটে বড় পরতন্ত্রতা থেকে মুক্তি দেওয়া ও পরিশেষে (চতুর্থ সিদ্ধান্তে) মানুষের মনে আশাপ্রদ ভবিষ্যতের চিত্র আঁকা, যা মানবমনে শীল ও সদাচারের ভিত প্রতিষ্ঠা করে।
বৌদ্ধ ধর্ম শিশুনাগযুগ, মৌর্যযুগ ও শুঙ্গযুগ, ইন্দো-গ্রিকযুগ, কুষাণ, গুপ্ত, বর্ধন ও পালযুগ-এর পৃষ্ঠপােষণায় প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে, সারা পৃথিবীর এক সুবিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে খুব সম্ভবত পৃথিবীর যত লােক বৌদ্ধ ধর্ম মানে, এত লােকে আর কোনও ধর্ম। মানে না। তাই দেশ-কাল-প্রকৃতি-জলবায়ু-জাতিগত বৈশিষ্ট্য খাদ্যাখাদ্যের অভ্যাস ইত্যাদির প্রভাবে এই ধর্মদর্শন অনিবার্যভাবে বহু বিবর্তিত বহু বিচিত্র ও বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তাই বৌদ্ধ ধর্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা প্রায় অন্ধের হস্তী দর্শনের মতাে। এ ছাড়া গােদের উপরে বিষফোড়ার মতাে আছে আদি ভাষা ও বর্তমান কালের বহু দেশের বহু ভাষার ভার।
এইভাবে বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বৌদ্ধেরা নিজেদের ইতিহাস বড় একটা লেখেননি। মুসলমানেরা ভারতে সাতশাে বছর রাজত্ব করেও বৌদ্ধ ধর্মের কথা বড় একটা জানেন না। সম্ভবত সেই কারণে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি মহম্মদ বিন্ ইক্তিয়ার ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংস করার পরে বলেছিলেন যে, তিনি ওই বিহারটাকে কেল্লা বলে ভুল করেছিলেন, তাই সমস্ত ‘দুর্গরক্ষী’ সৈন্যকে হত্যা করার পরে দেখলেন, সকলে নিরস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক ও গেরুয়া কাপড়ধারী। তখন তিনি তাদের ‘মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ’ বলে মনে করেছিলেন। এ ছাড়াও আবুল ফজলের অত বড় বই ‘আইন-ই আকবরি’-তে বৌদ্ধ ধর্মের কোনও রকম নামগন্ধও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস লেখার চেষ্টা হিন্দুরাও বড় একটা করেননি। শেষে এই প্রচেষ্টা করলেন ইউরােপীয় পণ্ডিতরা ও তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারত সন্তানেরা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে চিনদেশ থেকে আসা বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের (ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খ্রি.), সাংয়ূম (৫১৮ খ্রি.), হিউ-এন সাং (৬২৯-৬৪৫ খ্রি.), ইৎসিং (৬৭১-৬৯৫ খ্রি.), হুইচাও (৭২৬-৭২৯ খ্রি.), ঔ কোং (৭৫১-৭৯০ খ্রি.), কি-য়ে (৯৭৬ খ্রি) ও চাউ-জুকুয়া (১২২৫ খ্রি.)) ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে প্রাচীন ভারত ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ইউরােপীয়রা সিংহলে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। তাই পালি শিখে, বই পড়া শুরু করে বুঝলেন, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল কতগুলাে ধর্মনীতির সমষ্টিমাত্র (হিংসা করিয়াে না, মিথ্যা কথা কহিয়াে না, চুরি করিয়াে না, পরস্ত্রীগমন করিয়াে না, ও মদ খাইও না—একেই পঞ্চশীল বলে)। হজসন সাহেব নেপালে দেখলেন বৌদ্ধ ধর্ম অনেক দর্শন গ্রন্থের সমষ্টি মাত্র; আর এই সব দর্শন অতি সুগভীর। যা ইউরােপে ১৮-১৯ শতকে প্রথম প্রকাশ পায়, সেই সব তত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্মে ২-৩ শতকেই চৰ্চিত হয়েছিল।
ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্ম আবার অন্য রকম, সেখানে বৌদ্ধ মঠ মাত্রই এক-একটা পাঠশালা; আবার সেখানে পূজাপাঠেরও বেশ ভাল রকমই ব্যবস্থা আছে। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মে মহাসমারােহে কালীপূজা, মন্ত্রতন্ত্র, হােম জপ ও মানুষ পূজা হয়। আবার চিন দেশের বৌদ্ধ ধর্মে মদ-মাংস খায়, প্রাণী হত্যা করে, অথচ বৌদ্ধ। জাপানিরা নানা ধরনের দেবদেবীর উপাসনা করে। এ ছাড়াও কোথাও পূর্বপুরুষের উপাসনা, কোথাও ভূত প্রেত পূজা আবার কোথাও বা চরমভাবে দেহতত্ত্বের উপাসনা চলছে। এই রকম বহু বৈচিত্র্যময়তার সামগ্রিকতা নিয়েই—বৌদ্ধ ধর্ম।
বুদ্ধদেবের উপদেশাবলি তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। কারণ বুদ্ধদেব তাঁর জীবদ্দশায় কোনও উপদেশাবলিই লিখিত আকারে রেখে যাননি। এই সময়ে বৈদিক গ্রন্থগুলােও মুখপরম্পরায় চলে আসছিল; কিন্তু তাদের শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, এক্ষেত্রে যার একান্তই অভাব দেখা যায়। বুদ্ধদেব নিজেও এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন বলেই তার ‘দেশনা’র যথেচ্ছ ব্যাখ্যা যাতে না হয়, তাই শিষ্যদের তিনি চারভাবে বাণীর সত্যতা যাচাই করে নেবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তার আশঙ্কাই সত্য হল। ফলে তার মহাপরিনির্বাণের মাত্র একশাে বছরের মধ্যেই বৌদ্ধ সংঘে বিভেদের সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। অবশ্য এর ফলে দেশে দেশে বৌদ্ধ সংঘের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়।
বৌদ্ধ সংঘে অনৈক্য
বহু মানুষ একসঙ্গে এক জায়গায় ওঠা-বসা করলে অতি তুচ্ছ কারণেও মনান্তর বা মতান্তর হওয়াটাই স্বাভাবিক। বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও একেবারে গােড়ার দিকে এই রকমই কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল। তবে বুদ্ধদেবের জীবিতকালে, যেহেতু তিনিই ছিলেন সংঘের শেষকথা, তাই তার হস্তক্ষেপের ফলে এগুলাে বেশি গড়াতে পারেনি।
একসময়ে কোনও শিক্ষানবিশ কোনও ভিক্ষুকে মুরুব্বি করে সংঘে উপস্থিত হলে সেখানকার সবচেয়ে বয়স্ক ভিক্ষু (স্থবির বা থের) অন্য আরও পাঁচজন ভিক্ষুর সামনে নবিশকে কতগুলাে প্রশ্ন করতেন। নাম-ধাম ইত্যাদির পরে জিজ্ঞাসা করা হত, তার কোনও উৎকট রােগ (কুষ্ঠ, শ্বেতী, যক্ষ্মা বা মৃগী) আছে কি না, সে ক্রীতদাস, রাজকর্মচারী বা রাজদণ্ডে দণ্ডিত কি না; এ ছাড়াও তার ভিক্ষাপাত্র, চীবর ইত্যাদি (ভিক্ষু হতে গেলে যে সব জিনিসের প্রয়ােজন) আছে কি না এবং সবশেষে তাকে জিজ্ঞাসা করা হত তার উপাধ্যায় গুরু কে? অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই শিক্ষানবিশকে তার আগ্রহ, মেধা ও অনুসন্ধিৎসা অনুসারে তালিমের ব্যবস্থা করা হত (Specialisation) যাতে সে ধর্মের বিশেষ এক দিকে পারঙ্গম হয়ে উঠতে পারে। ফলে একই সংঘের মধ্যে বিভিন্ন উপাধ্যায়, তার ছাত্রদের ধর্মের বিভিন্ন দিকে পারঙ্গম করে তুলছেন। অর্থাৎ প্রতিটা বিহার-ই যেন এক-একটা মহাবিদ্যালয়। এখানে ধর্মের কিছু সাধারণ বিষয় সকলকে শিখতে হলেও অনুসন্ধিৎসা, মেধা ও ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী প্রত্যেককে ধর্মের বিভিন্ন দিকে specialise করে গড়ে তােলা হত; তাই সকলেই বৌদ্ধ হলেও তাদের ঘরানা ছিল আলাদা। যেমন সারিপুত্ত হলেন উচ্চজ্ঞানের অধিকারীদের মধ্যে প্রধান। মহামােগ্গলান—অলৌকিক ক্ষমতাশালীদের মধ্যে প্রধান।
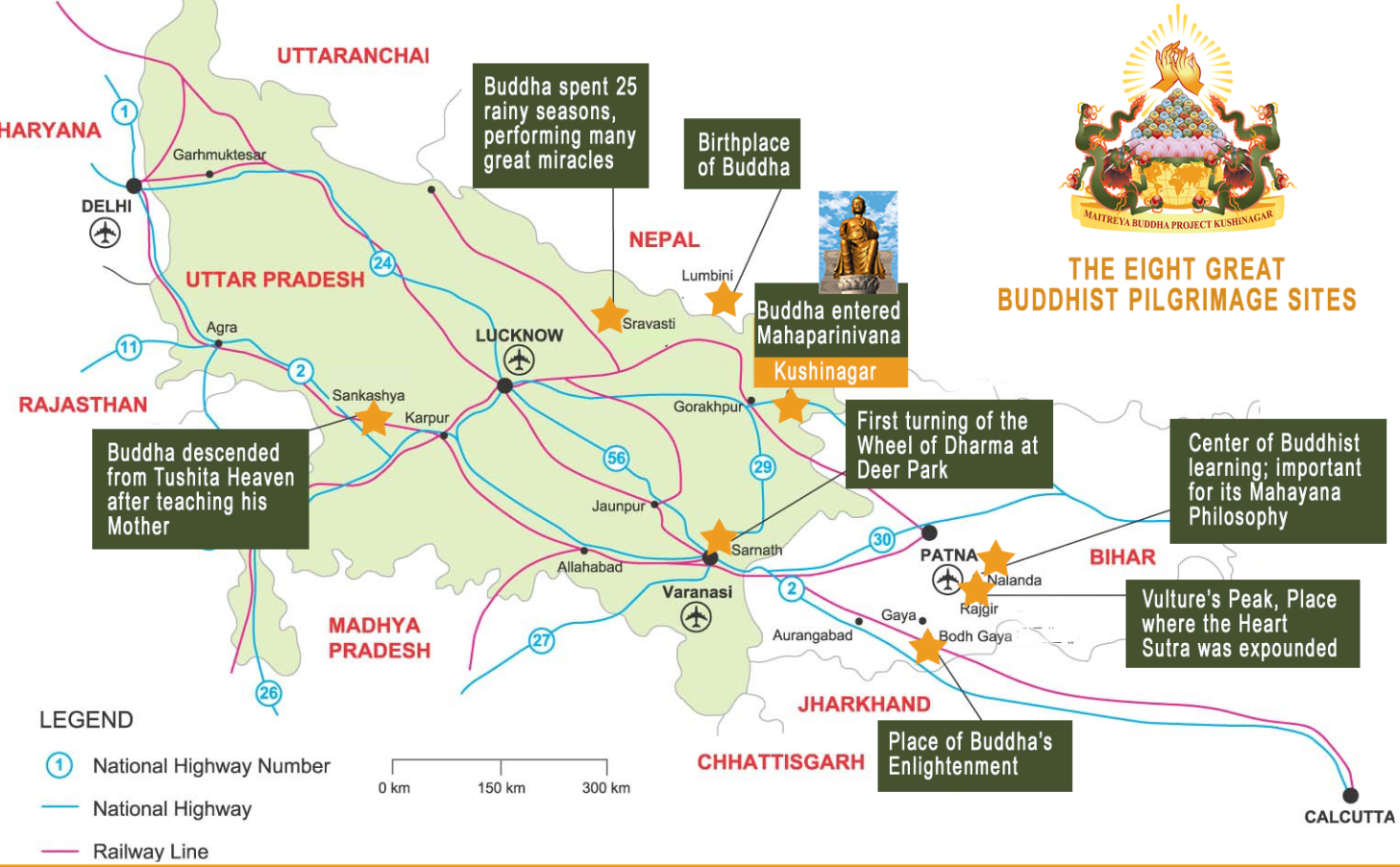
- মহাকস্সপ—ধূত অনুশাসন গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধান। পুণ্ণ মন্তানিপুত্ত—বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকদের মধ্যে (সেই যুগে) প্রধান। মহাকচ্চায়ন—বুদ্ধ বচনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান। রাহুল—শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধান। রেবত খাদিরবনিয়— আরণ্যক ভিক্ষুর মধ্যে প্রধান। আনন্দ—বহুশাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে প্রধান। উপালি— ‘বিনয়’ বিশারদ। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের শাখার ভিক্ষুদের কাছে পূজিত হতেন। ফলে শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ প্রকট না হলেও আচার্যদের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রাধান্যের দ্বন্দ্বে সংঘে বিভাজনের সৃষ্টি হয়। ফলে সেখানে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরকালই ছিল। সম্ভবত এই রকমই কোনও এক মতভেদ হয়েছিল কোসাম্বিতে ‘ধমধর’ ও ‘বিনয়ধর’ ভিক্ষুদের মধ্যে। এরপর উল্লেখযােগ্য সংঘভেদের ঘটনা হল বুদ্ধদেবের শ্যালক দেবদত্তকে নিয়ে। তিনি সংঘে ভিক্ষুদের জীবনযাত্রায় বহুল পরিমাণে কঠোরতা (ধূতাঙ্গ) আনতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব সকলের জন্যে কঠোরতা প্রচলনের অনুমতি না দেওয়ায় দেবদত্ত তার বহু অনুচরদের নিয়ে সংঘ ত্যাগ করেন। এ ছাড়াও কতগুলাে ছােট ছােট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মতবিরােধ সংঘভেদের পর্যায়ে চলে যায়। বুদ্ধ স্বয়ং তা কঠোর হস্তে দমন করেন; আর সংঘভেদসৃষ্টিকারীদের মাতা-পিতা হত্যার সমান অপরাধী বলে আদেশ জারি করে তখনকার মতাে পরিস্থিতি সামাল দেন। কিন্তু এর পরেও তার মহাপরিনির্বাণের অল্পদিন পরেই তার বচনগুলাের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা সংঘভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও বুদ্ধদেব নিজে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মৌন থাকতেন অথবা প্রশ্নকারীকে ‘তােমার এ সব কথায় কাজ কী হে,’ বলে থামিয়ে দিতেন। যেমন সৃষ্টিতত্ত্বের প্রশ্নে, জীবাত্মা, পরমাত্মা, আত্মার অবিনশ্বরতা ও নবকলেবর ধারণ, পাপ-পুণ্যের ভার জন্ম-জন্মান্তরে বয়ে বেড়াতে হয় কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব প্রশ্নে মৌন থাকায় পরবর্তীকালে নানা বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যার অর্গল খুলে দেয়। বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধদেবই শেষ কথা। তার ব্যক্তিত্বের সামনে অনেক মনান্তর ও মতান্তর নিশ্চুপ থাকলেও ভেতরে ভেতরে বহু অসন্তোষ তুষের আগুনের মতাে চাপা দেওয়া ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।
শাক্যসিংহের মহাপরিনির্বাণের খবর পেয়ে তার শিষ্যরা যখন হাহাকার করছিলেন, তখন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সুভদ্দ স্বগতােক্তি করে বলেছিলেন, যাক বাবা বাঁচা গেল, এখন থেকে বিনয় নিয়ম পালনের কঠোরতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আমরা আমাদের ইচ্ছামতাে কাজ করতে পারব। সুভদ্দের উক্তিতে শঙ্কিত অন্যতম প্রধান শিষ্য মহাকসপ স্থবির বুদ্ধদেবের প্রবচিত ধর্ম ও বিনয় অর্থাৎ, বুদ্ধবচন যাতে যথাযথভাবে রক্ষা করা যায়, তার জন্যে মহাপরিনির্বাণের তিনমাসের মাথায় মগধের রাজধানী রাজগৃহে, অজাতশত্রুর রাজত্বকালে, বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও তার একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুচরদের নিয়ে, প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত করেন। প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির পৃষ্ঠপােষক ছিলেন বলে (রাজা অজাতশত্রু) বৌদ্ধ ধর্মে আজও অমর হয়ে আছেন। বুদ্ধদেব তার পরবর্তী কোনও উত্তরাধিকারীর কথা উল্লেখ করে যাননি; তাই বৌদ্ধ ধর্মের স্থায়িত্বকল্পে অনুশাসনগুলাের মূল্য ছিল অপরিসীম। তাই সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মগুলাে সংগ্রহ ও সংকলন করাই ছিল তখন এক স্বাভাবিক চাহিদা।
প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি
এই সংগীতিতে মােট পাঁচশােজন অৰ্হত্বপ্রাপ্ত স্থবির যােগ দেন; আর সংঘনায়ক রূপে মহাকস্সপ স্থবির। তিনি ভিক্ষুসংঘের অনুমতি নিয়ে, ‘ধর্ম ও বিনয়ের’ মধ্যে বিনয় নিয়মগুলাে সর্বপ্রাচীন, তাই বুদ্ধদেবের শিক্ষাবলি সংরক্ষণের প্রয়ােজনে প্রথমেই ভিক্ষু উপালীকে আহ্বান করেন। কারণ তিনিই বুদ্ধদেবের কাছ থেকে সর্বান্তঃকরণে প্রতিটা বিনয় নিয়ম শিক্ষা করেছিলেন। এইভাবে সর্বপ্রথম বিনয় সংগায়ন (বিনয় পিটক) সংস্থাপন করার পরে আনন্দ থেরকে- (বুদ্ধদেবের সর্বক্ষণের একান্ত সচিব ও আমৃত্যু পার্শ্বচর) সর্বসম্মতিক্রমে বুদ্ধদেবের ধর্ম সম্পর্কে মুখনিঃসৃত বাণী পঞ্চনিকায় (দীঘ, মজ্জিম, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক) সংগায়ন (ধর্ম বা সংস্থাপন পিটক) করতে বলা হয়। সবশেষে সূত্ত অনুরুদ্ধ মহাথের কস্সপের নির্দেশে অভিধর্ম আবৃত্তি করেন (অভিধর্ম পিটক)। এইভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে বুদ্ধদেবের অমূল্য বাণীর সংকলন বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটক (ধর্মপিটক বা সূত্ত পিটক ও বিনয়পিটক, অভিধর্ম পিটক) সংকলিত হয়; যার ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম।
যখন রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপােষণায় ও মহাকস্সপের নেতৃত্বে মগধের রাজধানী রাজগৃহে বুদ্ধদেবের বাণী সংরক্ষণের জন্যে তার শিষ্যমণ্ডলী প্রথম সংগীতির আয়ােজন করেন, তখন রাজগৃহের কাছেই পুরাণ নামে এক স্থবির পাঁচশাে ভিক্ষুসংঘ নিয়ে অবস্থান করতেন। তাকে প্রথম সংগীতিতে যােগ দেওয়ার জন্যে অনুরােধ করা হলেও তিনি তা উপেক্ষা করেন; কারণ তিনি বিনয় নিয়মের কিছু রদ-বদল করতে চান। এ ছাড়াও বুদ্ধদেব তার মহাপরিনির্বাণের আগে শিষ্য আনন্দকে আদেশ করেছিলেন যে, উদ্ধত ও উগ্রস্বভাবের জন্যে ভিক্ষুসংঘ যেন ভিক্ষু ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড (সবরকম সামাজিক যােগাযােগ বিচ্ছিন্ন) দেয়।
এই সব উদাহরণগুলাে থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বুদ্ধদেবের জীবিত অবস্থা থেকেই সংঘের মধ্যে মতভেদের বীজের অঙ্কুরােদগম হয়েছিল।
এ ছাড়া আরও একটা ঘটনা বৌদ্ধ ধর্মের উপরে বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তা হল, বুদ্ধদেব যখন তার ধর্ম দিকে দিকে প্রচার করছেন, দলে-দলে লােক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে, তখন সিদ্ধার্থ গৌতমের পালিতা মাতা গৌতমী (বুদ্ধদেবের মা, মায়াদেবী তার জন্মের পরে পরেই মারা যান। তখন শুদ্ধোদন তার শ্যালিকা গৌতমীকে বিবাহ করেন। তিনিই সিদ্ধার্থকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করেন। তারই নামানুসারে (গৌতমী) সিদ্ধার্থের আর এক নাম হয় গৌতম) বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা নিতে চান ও দীক্ষান্তে ভিক্ষুণী হওয়ার বাসনা জানান। প্রসঙ্গত বলা যায় তখনও অবধি বৌদ্ধ সংঘে নারীর কোনও স্থান ছিল না। মায়ের এই প্রস্তাব বুদ্ধদেব শােনামাত্রই প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুদিন বাদে মাতা গৌতমী তার বাসনা আনন্দকে বলেন। এবারেও বুদ্ধদেব তাকে ফিরিয়ে দেন। এরপর তৃতীয় বার আনন্দের একান্ত অনুরােধে তিনি নিমরাজি হন। গৌতমীকে দীক্ষা দানের পরে বুদ্ধদেব আনন্দকে বলেছিলেন—সংঘে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সদ্ধর্মের (বৌদ্ধ ধর্ম) আয়ু হাজার বছর থেকে কমে মাত্র কয়েকশাে বছরে এসে দাঁড়াল। আদর্শরমণী রূপে মাতা গৌতমী বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘে প্রথম ভিক্ষুণী হলেন। এরপরে বুদ্ধদেব একে একে বহু নারীকেই দীক্ষা দান করেন। অম্বপালী গণিকা, বিশাখা, সুজাতা, ক্ষেমা, উৎপবর্ণা, পূর্ণা, ভিয্যা, ধীরা, মিত্রা, ভদ্রা, উপক্ষমা, মুক্তা ও স্ত্রী যশােধরা ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশ জন নারীকে দীক্ষা ও প্রবজ্যা দেন। কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই নারীকে ভিক্ষু সংঘে একবার প্রবেশাধিকার দিলে তার বিপদ ও পরিণাম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই ভাবী অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা মাথায় রেখে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায় ও সংঘের জন্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাবলি ও দণ্ড তৈরি করেছিলেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর জীবন দর্শন ধর্মজগতের আদর্শ। কিন্তু নরনারীর সংমিশ্রণের বিপদ কালের প্রবাহে বহু বিচিত্র রূপ ধারণ করতে থাকে। ধর্মজগতের উচ্চনীতির অভ্যাস করলেও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও রিপুতাড়নকে অগ্রাহ্য করতে পারল না।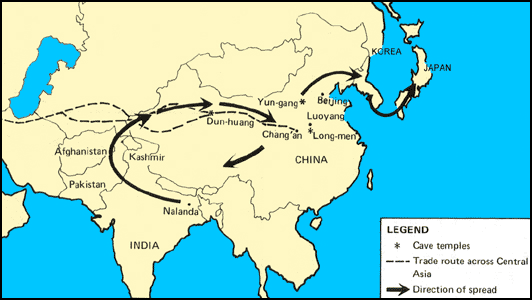
- কালক্রমে ব্যভিচারের মাত্রা পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হতে থাকে। সংঘের নিয়মানুসারে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে বিবাহ দেওয়ার প্রচলন ছিল না। ফলে এরা সমাজে পতিত হিসাবেই ঘৃণিত হত। এইভাবে বাংলা, ওড়িশায় ও অসমে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তাচলের কালে নেড়ানেড়ি, সহজিয়া, কিশােরী ভজক, কর্তাভজা, বাউল, মহিমাধর্মী ইত্যাদি ইত্যাদি অতিবিচিত্র নামে বজতন্ত্র (যান) বৌদ্ধ উপাসকেরা সমাজের চোখে অতি হীন হয়ে পড়লেন। তখন বৈষ্ণবাচার্যেরা এদের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু করে সমাজে আশ্রয় দিতে থাকেন। তাই সমাজে পাঁচসিকা পয়সা গােস্বামীকে দিয়ে বৈষ্ণবী গ্রহণের প্রথা চালু হয়। বৈষ্ণব ধর্মের এই প্রথা মােটেই হাস্যকর বা নিন্দনীয় নয়; তা একান্তই সমাজ রক্ষা ও অনুশাসনের তাগিদেই সৃষ্ট হয়েছিল। ১৬শ শতাব্দীর শেষেও এই রকম অবাধ মিলনজনিত পতিত হতভাগ্য, সমাজতাড়িত, নিরাশ্রয় শত শত নেড়ানেড়িকে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, তার ছেলে খড়দহে শ্যামসুন্দরের পায়ে ঠাঁই দিয়ে ও মুর্শিদাবাদের রূপ গােস্বামী এই একই কাজ করে পতিতপাবন নাম অর্জন করেন। আর আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ‘জয় নিতাই’, ‘জয় নিতাই’ ধ্বনি দিয়ে সম্ভাষণ খুবই প্রচলিত।
বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের আগে তার একান্ত সচিব আনন্দ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তার অবর্তমানে সংঘে সর্বোচ্চ পদাধিকারী (শাস্তা) কে হতে পারেন? উত্তরে বুদ্ধদেব বলেন, ধম্ম ও বিনয়ের দেশনাই সংঘের আগামী দিনের শাস্তা। এই কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, গূঢ় অর্থবহুল তার দেশনার উপর তিনি অবিচলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। আর ধর্মের মূল তত্ত্বগুলাের পর্যালােচনা করে মতভেদের কারণগুলাের নিরসন করা। এই দুইই হবে আগামীদিনের বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় স্বরূপ। এ ছাড়াও তিনি বুদ্ধদেশিত দণ্ডবিধি ও তার বিধিনিষেধগুলােকেও সংঘের সর্বোত্তম সংঘনায়ক রক্ষক বলেছিলেন। এ ছাড়াও প্রতিটা বিহারেই একজন করে সর্বজনশ্রদ্ধেয় সংঘনায়ক রয়েছেন তারাই ধর্মকে রক্ষা করবেন।
কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সংঘ-নায়কদের নিজ নিজ তত্ত্বাবধানেই বিভিন্ন সংঘ পরিচালিত হতে থাকে। ‘উপােসথ দিবসে’ বুদ্ধবচনের সংক্ষিপ্ত বা অতি সংক্ষিপ্ত উক্তিগুলাের অর্থ স্পষ্ট বা বিশদভাবে অর্থ বােধগম্য করার জন্যে যে বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলাে করা হয়েছে, উত্তর ভারতের সংঘগুলাের মধ্যে, ওই ব্যাখ্যাগুলাের মধ্যে কোনটা সঠিক তা নির্ধারণ করার মতাে উপযুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির অভাবেই সমস্ত বৌদ্ধসংঘে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ওই (বুদ্ধ পরবর্তী) সময়কালে সংঘের সর্বাধিনায়ক হতে পারে এমন কাউকে তিনি খুঁজে পাননি। তাই চোখ বুজে সংঘের ভবিষ্যৎ মহাকালের চরণে সমর্পণ না করে কতগুলাে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন –
ক) নিষ্ফল কথাবার্তা না বলা।
খ) কিছুদিন অন্তর অন্তর সভায় মিলিত হওয়া।
গ) একত্রিতভাবে (সমগ্র) ধর্মীয় কাজকর্ম করা।
ঘ) বয়ােজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সম্মান দেখানাে ও সংঘপ্রধানকে মান্য করে চলা।এ ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মে সম্প্রদায় সৃষ্টির বীজ মূলত ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। হিন্দুদর্শনে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে উপনিষদ থেকে ছয় ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়। হিন্দু ধর্মে সাধারণভাবে আত্মাকে শরীরের মধ্যে অবস্থানকারী এক আলাদা শক্তি, যা নিত্য চেতন, কূটস্থ, অবিনাশী বলে মানা হয়। অর্থাৎ যার প্রেরণায় ও দৌলতে শরীর নামক যন্ত্রটা চলছে ও যে আমার মনের মনন, কানের শ্রবণ, চোখের দর্শন, জিহ্বার আস্বাদন, নাসিকার আঘ্রাণ—তিনিই সেই। জীবের মৃত্যুর পরে আত্মার দেহান্তর গমন ঘটে। এই মতই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব বলতেন—আত্মা কোনও নিত্য কূটস্থ বস্তু নয়, বরং বিশেষ কারণে বস্তু ও মন সহযােগে উৎপন্ন এক শক্তি, যা অন্য বাহ্য পদার্থের মতাে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন ও বিনাশ হচ্ছে। চিত্তের এই ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া ও বিলীন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই চিত্ত প্রবাহ শরীরে বর্তমান থাকে। সে যুগে তার এই সরল মতবাদ সমগ্র মানব সমাজকে নাড়া দেয়। শিক্ষিতরাও তার এই মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ (তার এই মতবাদ) এ এক সম্পূর্ণ নতুন সহজ-সরল মতবাদের ধারা। তাই এর বিশদ ব্যাখ্যা বা মর্মার্থ জানার জন্যে লােকে ভীষণ ভাবে আগ্রহী হয়ে পড়ে। কিন্তু (বুদ্ধের) আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষের আগ্রহকে তৃপ্ত করার মতাে কোনও ধর্মীয় উপদেষ্টা বা শাস্তা ছিলেন না। তাই বুদ্ধবচনের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে ব্যর্থ সংঘ-নায়ক বা শাস্তারা নিজেদের বােধ-বুদ্ধি মতাে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করতে থাকেন যা পরবর্তীকালে (বৌদ্ধ ধর্মে) বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
বুদ্ধদেবের আত্মা (সৎকায়) তত্ত্ব (রাহুল সাংকৃত্যায়ন)
আত্মা = (সৎকায়) – রূপী ও অরূপী
রূপী – সান্ত ও অনন্ত
অরূপী – সান্ত ও অনন্ত
সব মিলে নিত্য বা অনিত্যপরিশেষে বলা যায় সংঘে অসন্তোষের বীজ যে বুদ্ধদেবের জীবিত অবস্থাতে ছাইচাপা ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে পরেই তার পবিত্র চিতাভস্মের অংশ বিভাজনের দাবিদারদের মধ্যেও প্রবল দলাদলি ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল।
দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি
এরপরে বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার ঠিক একশাে বছর বাদে (বৈশালী) বেসালিতে শিশুনাগপুত্র কালাসােকের রাজত্বকালে তারই পৃষ্ঠপােষণায় দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করা হয়। এই সংগীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধদেবের শিক্ষাপদগুলাের ব্যতিক্রমের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করে যথার্থ বুদ্ধবচন রক্ষা করা। এই অধিবেশনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা বয়সে নবীন, সেই বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুকেরা বুদ্ধদেবের বিনয় নিয়ম ব্যবহারে দশটা শিথিলতা ও ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সংঘে অনাচারের সৃষ্টি করেন। এই বিনয় বিরুদ্ধ দশবিধ (দশবথুনি) আচরণ বিধিসম্মত বলে পালন করা মূলত ছিল, নতুন অধিকার পাওয়ার আন্দোলন। ফলে (দশবস্তু) বিনয় নিয়মের দশটা শিথিলতা অর্জন ও রক্ষা করার অধিকার নিয়ে সংঘে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে আলােড়ন প্রবল থেকে প্রবলতর রূপ নিল।
এই দশবিধি আচরণ হল –
১। কপ্পতি সিঙ্গিলােণকপ্পো – দরকার অনুসারে ব্যবহারের জন্যে ভিক্ষুগণ শৃঙ্গাধারে লবণ রাখতে পারেন।
২। কপ্পতি দ্বংগুলকগপ্পো – মধ্যাহ্নের পরে, ছায়া দুই আঙুল অতিক্রম না করা পর্যন্ত ভিক্ষুগণ ভােজন করতে পারেন।
৩। কপ্পতি গামন্তরকপ্পো – ভিক্ষুগণ একবার ভােজন করে আবার অন্য গ্রামে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা বা ভিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন।
৪। কপ্পতি আবাসকপ্পো – একই সীমানায় ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুরা আলাদা আলাদা ভাবে উপােসথ পালন করতে পারেন।
৫। কপ্পতি অনুমতিকপ্পো – সংঘের উপস্থিত ভিক্ষুরা অপর ভিক্ষুদের অনুমতি পরে গ্রহণ করবেন। এই মনে করে বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে পারেন।
৬। কপ্পতি আচিন্নকপ্পো – পরম্পরাগত বা পূর্বাপর আচার্য কিংবা উপাধ্যায় স্থানীয় স্থবিরদের আচরিত প্রথামতে ভিক্ষুক আচরণ করতে পারেন।
৭। কপ্পতি অমথিতকপ্পো – ভিক্ষুগণ দুধ ও দইয়ের মাঝামাঝি অবস্থার পানীয় পান করতে পারেন।
৮। কপ্পতি জলেগিকপ্পো – ভিক্ষুগণ ঝাঝালাে তালরস পানীয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন।
৯। কপ্পতি অদকং নিসীদনং – দশা বা ঝালরহীন আসন প্রমাণাতিরিক্ত হলেও ভিক্ষুগণ তাতে উপবেশন করতে পারেন।
১০। কপ্পতি জাতরূপরজতং – ভিক্ষুগণ স্বর্ণরৌপ্য বা মুদ্রাদি দান গ্রহণ করতে পারেন।বুদ্ধ দেশিত মূল বিনয় নিয়ম অনুসারে দশবিধ আচরণে ওই সবক’টা কথাই নিষেধ করা ছিল। নবীনেরা তা উল্লঙ্ঘন করে সব ক’টা কথাকে ‘হাঁ করে নেন।
বিনয় নিয়মের এই দশটা শিথিলতাকে প্রবীণেরা কোনও ভাবেই মেনে নিলেন না। এদের মধ্যে কিছু কিছু স্থবিরের বয়স ১৪০, ১৫০ এমনকী ১৬৫ বছরও ছিল। এদের কয়েকজন স্থবির আনন্দের সমসাময়িক ছিলেন। এরা সব দিক বিচার বিবেচনা করে ‘সব্বকামী ও বিনয়ানুসারে’ একমত হন যে, বজ্জিদেশীয় ভিক্ষুকদের মতবাদগুলাে মূল বৌদ্ধ ধর্মের পরিপন্থী। ফলে রক্ষণশীল স্থবিরেরা দশহাজার নবীন বজ্জি ভিক্ষুককে বিতাড়িত করেন। তখন তারা বৈশালীর উপকণ্ঠে মহাবনের কূটাগারশালায় পালটা মহাসভার আয়ােজন করেন। পরবর্তীকালে ওই মহাসভা মহাসংগীতি নামে খ্যাত হয়, আর যারা ওই মহাসংগীতিতে যােগ দিয়েছিলেন তাদের মহাসাংঘিক বলা হয়। এ ছাড়া এই নবীনেরা ত্রিপিটকেও কিছু রদবদল করেন; আর ‘অভিধম্মপিটক’কে বুদ্ধ বচন থেকে বাদ দিয়ে দেন। আজও উত্তর ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বহুল ভাবে প্রচলিত তার মূলে এই দ্বিতীয় মহাসংগীতির ‘দশবস্তু’ নিয়ে বিরােধ, আর এরই পাশাপাশি এশিয়ার দক্ষিণে স্থবিরবাদ বা থেরবাদ বা মূল রক্ষণশীল বৌদ্ধ ধর্ম এখনও সমান ভাবে প্রচলিত।
এ ছাড়াও মথুরার এক বিদ্বান ও প্রজ্ঞাবান ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্রের কুক্কুটরাম সংঘে প্রবজ্যা নেন। পরবর্তীকালে ইনি সংঘরাজ হন। এই দার্শনিকের পাঁচ মতবাদও দ্বিতীয় সংগীতিতে প্রবল মতানৈক্যের সৃষ্টি করে। এই পঞ্চ মতবাদ হল –
ক) অহৎ অজ্ঞাতসারে পাপ করতে পারেন।
খ) তিনি নিজে যে একজন অর্হৎ, সে কথা তাঁর নাও জানা থাকতে পারে।
গ) কোনও মতবাদ সম্পর্কে অর্হৎ-এর সন্দেহ থাকতেই পারে।
ঘ) গুরু ছাড়া কেউ অর্হৎ হতে পারবে না।
ঙ) ধ্যানস্থ অবস্থায় হঠাৎ ‘হা কষ্ট!’ ‘হা কষ্ট!’ এইরকম বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ করে সত্য উপলব্ধি করা যায়।তা হলে এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে হীনযানেরা হীন কীসে? মহাযানেরাই বা মহান কীসে? আর যান কথাটারই বা অর্থ কী? ‘যান’ কথাটার প্রকৃত অর্থ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ আছে। সাহেবরা মনে করতেন। যান শব্দের অর্থ vehicle অর্থাৎ গাড়ি-ঘােড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক বৌদ্ধদের মধ্যে যান শব্দের অর্থ পন্থ বা মত। যেমন আমরা বলি নানকপন্থী, কবীরপন্থী ইত্যাদি। সেই রকমই হীনযান, মহাযান, মন্ত্রযান, শ্রাবকযান ইত্যাদি।
মহাসাংঘিকদের মাত্র একখানা বই আজ অবধি পাওয়া গিয়েছে ও প্রকাশিত হয়েছে, তা হল ‘মহাবস্তু অবদান’। মহাসাংঘিকরাই পরবর্তীকালে মহাযান নামে প্রসিদ্ধ হন। মহাসাংঘিক থেকে মহাযানে সংগঠিত হতে তিনশাে বছর লেগে যায়। এই নবীন মহাসাংঘিক বা মহাযানীরা নিজেদের বড় দেখাবার জন্যে, আর একই সঙ্গে অন্যদের ছােট বা হেয় করার জন্যে হীনযান বা হীনযানী বলে অভিহিত করেন। এর আগেও কিন্তু যান ছিল, প্রত্যেক বুদ্ধ যান বা প্রত্যেক যান ও শ্রাবক যান। যখন পৃথিবীতে কোনও বুদ্ধ উপস্থিত নেই, তার মুখ থেকে ধর্মকথা শােনার কোনও সুযােগ নেই, তখন লােকে নিজের চেষ্টায়, যত্নে ও উদ্যমে জন্ম-জরা-মরণাদির হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে (হিন্দু ঋষিরা এইভাবে মুক্তিলাভ করতেন)। এইভাবে স্বপ্রচেষ্টায় ও যত্নে যারা উদ্ধার পান তাদের প্রত্যেক বুদ্ধ যান বলে। এরা নিজেরা নিজেদের উদ্ধার করতে পারলেও অন্যকে উদ্ধার করার শক্তি নেই। স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ থেকে যারা ধর্মজ্ঞান লাভ করেন তারাই-শ্রাবক। এরা অনেকেই বুদ্ধদেবের পরামর্শে উদ্ধার পান। এরা প্রথমে শ্রাবক, তারপর ভিক্ষু হয়ে বিহারে বসবাস করেন, তারপর স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও সবশেষে অর্হৎ হয়ে জন্ম-জরা-মরণাদির হাত থেকে উদ্ধার পান। কিন্তু এরাও অন্যকে উদ্ধার করতে পারেন না।
মহাযানীরা প্রত্যেক বুদ্ধ ও শ্রাবক এই দুই যানকেই হীন মনে করতেন। কারণ এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর, নিজের উদ্ধার হওয়া ছাড়া এরা জগতের কথা ভাবেন না, তাই জগৎ সমাজ বা মানব বলে এদের কাছে কিছুরই অস্তিত্ব নেই, কেবলই আত্ম উদ্ধার চিন্তা। তাই এরা হীন। অপর পক্ষে মহাযানীরা নিজেদের মহান বলে ভাবতেন কারণ, এরা নিজের উদ্ধারের থেকে জগৎ উদ্ধারের কথাই বেশি করে ভাবেন; অর্থাৎ জগৎ উদ্ধারই মহাযানীদের চরম ও পরম মহাব্রত। যখন ‘অবলােকিতেশ্বর’ উদ্ধার হবেন-হবেন, মহাশূন্যে নিলীন হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জগতের সমস্ত প্রাণী তাকে কাতরভাবে বলে উঠল—আপনি নির্বাণ লাভ করলে, কে আমাদের উদ্ধার করবে? এই কথা শুনে বােধিসত্ত্ব অবলােকিতেশ্বর তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলেন পৃথিবীতে যতদিন অবধি একটা প্রাণীও বদ্ধ থাকবে, ততদিন অবধি তিনি নিজে নির্বাণে প্রবেশ করবেন না। এই যে দয়া, সর্বভূতে করুণা, এর জন্যে মহাযান ‘মহা’। তাই মহাযান ধর্মের সারাৎসার কথা করুণা হল— ‘সমস্ত জীবে করুণা কর।” আর এই ধর্মের প্রধান গ্রন্থ হল ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’।
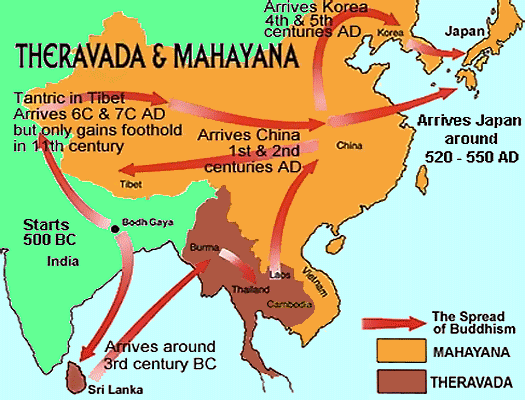
-
একথা থেকে মনে হয় যেন সে যুগে জীবমাত্রই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু তা তাে সত্যি নয়। তখন ভারতবর্ষে নানা রকমের ধর্ম বর্তমান ছিল, তারা একথা মানতে যাবে কেন? এদিকে অবলােকিতেশ্বরও যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! তখন তিনি বুদ্ধদেবকে যে যে কথা বলেছিলেন, তা যদি গীতার ভাষায় প্রকাশ করা যায়— “যাে যাে যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধায়াচিতুমিচ্ছতি। তথ্য স্যাম্যাচলাং শ্রদ্ধাং তমেব বিদধাম্যহং (৭/২৯)।” অর্থাৎ, “যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে যে দেবমূর্তি অর্চনা করতে চায়, আমি (অন্তর্যামীরূপে) সেই সব ভক্তের সেই সেই দেবমূর্তিতে ভক্তি অচলা করে দিই।” অবলােকিতেশ্বর সেই সেই (দেবমূর্তিরূপে) রূপ পরিগ্রহ করে সকলকে উদ্ধার করবেন।
বােধিসত্বেরা নির্বাণের অভিলাষী, তারা মানুষ। তাই ভগবানের মুখে যে কথা শােভা পায়, মানুষের মুখে তা আরও বেশি করে শােভা পায়। এ থেকেই বােঝা যায়, তাদের করুণা কত গভীর।
মহাসাংঘিকেরা দশবস্তু নিয়ে যে মতভেদের সৃষ্টি করেন তা থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রধান দুই ভাগে হীনযান (স্থবিরবাদী বা থেরবাদী) ও মহাসাংঘিক (পরবর্তীকালে মহাযান) বিভক্ত হয়ে যায়। কালক্রমে মহাসাংঘিকরা সাতটা শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়-
- ক) একব্যবহারিক
- খ) চৈতিক বা চৈত্যক (লােকোত্তর বা চৈত্যবাদ)
- গ) কৌকুট্টিক বা গােকুলিক
- ঘ) বহুশ্রুতীয়,
- ঙ) প্রজ্ঞপ্তিবাদ
- চ) পূর্বশৈল,
- ছ) অপরশৈল।
এর মধ্যে চৈত্যবাদ (লােকোত্তর) ও শৈল সম্প্রদায়ই ছিল সবথেকে জনপ্রিয়। এদের প্রভাব দক্ষিণ ভারতেই বেশি। অপরদিকে হীনযানীরাও এগারােটা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে –
- ১) মহীশাসক
- ২) বাৎসীপুত্রীয়
- ৩) সম্মিতীয়
- ৪) ছন্নগারিক
- ৫) ভদ্রযানীয়
- ৬) ধর্মোত্তরীয়
- ৭) সর্বাস্তিবাদ
- ৮) ধর্মগুপ্তিক
- ৯) কাশ্যপীয়
- ১০) হৈমবত
- ১১) সংক্রান্তিক
এদের মধ্যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জনপ্রিয়তা সর্বাস্তিবাদীদেরই সবচেয়ে বেশি ছিল। এ ছাড়াও আরও কতগুলাে উপশাখা বা উপদলের কথাও বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে সময়ের সঙ্গে এরা নিজেদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হারিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। বিভজ্যবাদ (বা বিভজ্জবাদ) নামে আরও একটা শাখার উল্লেখ তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতির ইতিহাসে পাওয়া যায়। কথিত আছে এরাই তৃতীয় সংগীতির মূল আহ্বায়ক ছিলেন। আর এরাই মহাবিহারে একমাত্র প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল থেরবাদী ছিলেন।
তবে এরও কিছু কাল পরে হীনযান ও মহাসাংঘিক বিভিন্ন শাখা, উপশাখাগুলাে নিজেদের দার্শনিকতা, বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে না। ফলে ক্রমশ তারা হীনবল হতে হতে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে থাকে। তা হলে দেখা গেল বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের মাত্র একশাে বছরের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম ১৮টা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে তাতেও শেষরক্ষা হয় না।
তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি
এর পরে বৌদ্ধ ধর্মের তৃতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় সম্রাট অশােকের রাজত্বকালে। সম্ভবত অশােকের রাজত্বের ১৭ বছরের মাথায়, ২৪৭ খ্রি. পূ.। এই অধিবেশনের মূল পৃষ্ঠপােষক ছিলেন সম্রাট অশােক, আর তা চলেছিল প্রায় নয় মাস কাল ধরে (জানুয়ারির মাঝামাঝি শুরু হয়ে শেষ হয় অগস্টের মধ্যে)। কথিত আছে সম্রাট অশােক এক সময়ে সমসাময়িক যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের ভালমন্দ বিচারে সময় কাটাতেন। ‘সারাসারং গবেসন্তো’ বিচার করার জন্যে তিনি বিভিন্ন ধর্মের তীর্থিকদের নিমন্ত্রণ করে, বিভিন্ন প্রসঙ্গের উত্থাপন করে, নানা প্রশ্ন করতেন। এই সময়ে নিগ্রোধ নামে এক অল্পবয়স্ক শ্রমণ তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করেন। তাই রাজা অশােক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ ছাড়াও জানা যায় যে, তার পিতা বিন্দুসার ৬০,০০০ জন জৈন, আজীবক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজককে পালন-পােষণ করতেন। অশােক তাদের তাড়িয়ে দিয়ে ৬০,০০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অসােকারাম নামে বিহারে স্থান দেন। একদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও তীর্থিকদের এত দিনের রাজ-পৃষ্ঠপােষণা থেকে বঞ্চিত হওয়া, আর অপর দিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সে রাজ-অনুগ্রহ লাভ। এর ফলে মূলত লােভনীয় সুযােগ-সুবিধা ভােগ করার জন্যই, বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীরা বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে, বৌদ্ধ বিহারগুলােতে অনুপ্রবেশ করে, নিজেদের ধর্মের আচার-ব্যবহার ও মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের ঘাের দুর্দিন শুরু হয় তার (বুদ্ধদেবের) মৃত্যুর মাত্র দু’শাে বছরের মধ্যে। প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ই নিজেদের শাখা-শাস্ত্রকে বুদ্ধদেবের মুখের বাণী বলে প্রচার করতে থাকে। যেহেতু বৌদ্ধসংঘে কোনও মুখ্য উপদেষ্টা ছিল না, তাই সঠিক বুদ্ধবচন স্থির করাও সম্ভব ছিল না। ফলে সংঘে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আর তা আরও বেশি হওয়ার কারণও ওই সব অন্য সম্প্রদায়ের তীর্থিকরা (ছদ্ম বৌদ্ধভিক্ষুরা)। এরা ঘােলা জলে মাছ ধরাটাই বেশি পছন্দ করতেন। বৌদ্ধভিক্ষুরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই বিশৃঙ্খলাকে থামাতে পারছিলেন না। এক সময়ে ভিক্ষুরা তীর্থিকদের সঙ্গে সংঘকর্ম করবেন বলে বৌদ্ধবিহারগুলােতে সংঘর্মক ‘উপােসথ’ বা ‘পবারণাকস্ম’ বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মের এই অবস্থা দেখে তখনকার (অসােকারামের) সংঘনায়ক মােগ্ললিপুত্ত তিস্স বিহার ছেড়ে উপরিগঙ্গার অহােগঙ্গোপর্বতে চলে যান। একথা যখন সম্রাট অশােকের কানে গেল, তখন তিনি তার এক অমাত্যকে (অসােকারাম) বৌদ্ধ সংঘে পাঠান, যাতে ভিক্ষুদের বিনয়বিহিত ধর্মকর্মগুলাে ঠিকঠাক চলে তার অনুরােধ জানাতে। কিন্তু ভিক্ষুরা রাজাদেশ পালনে অক্ষম বলায়, সেই অমাত্য তরােয়াল নিয়ে বহু ভিক্ষুর মুণ্ডচ্ছেদ করেন। এই সংবাদে সম্রাট ভীষণ দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজের ভুলের গ্লানিতে, অহােগঙ্গোপর্বতবাসী তিসসকে, সসম্মানে পাটলিপুত্রে এনে, নিজের ভুলের পরিণাম জানতে চান। তিস্স রাজাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, অজান্তে কৃত পাপ তার উপর বর্তাবে ন।
কথিত আছে এরপরে রাজাকে তিস্স সাতদিন ধরে বুদ্ধদেবের ধর্মদেশনা করলেন। সপ্তম দিনে বিচার সভা বসল। অশােক নিজে উপস্থিত থেকে, তিস্সর নেতৃত্বে ভিক্ষুদের বুদ্ধদেশিত ধর্মের ব্যাখ্যা করতে বলেন। আর অতি সহজে তাতে জল-দুধ আলাদা করা গেল। তখন বৌদ্ধভিক্ষুর ছদ্মবেশধারী ৬০,০০০ তীর্থিককে শ্বেতবস্ত্র হাতে ধরিয়ে বৌদ্ধ সংঘ থেকে বিতাড়িত করা হল।

-
এরপরে রাজার নির্দেশে ‘উপােসথসভা’ আবার চালু হল। বিশাল বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে থেকে মহাস্থবির মােগ্ললিপুত্ত তিস্স এক হাজার জন অর্হৎ ভিক্ষুকে নির্বাচন করলেন, আর তাদের নিয়েই তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হল। শােনা যায় ওই সব ভিক্ষুদের মধ্যে ছয়টা বিশেষ ক্ষমতা ছিল। আর তারা ত্রিপিটক সম্পর্কে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।
এই সময়ে সংঘ-ভেদজনিত বিশৃঙ্খলা সম্ভবত সম্রাট অশােকের সুবিশাল রাজত্বের সর্বত্রই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, আর তা থামাবার জন্যে রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ আদেশ প্রচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ ছাড়াও লক্ষ করার বিষয় হল, চিনা বা তিব্বতি গ্রন্থে তৃতীয় সংগীতির কোনও উল্লেখই নেই। অথচ পালি উপাদানে সংগীতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, তৃতীয় সংগীতিতে স্থবিরবাদ বা থেরবাদীদের (হীনযান) প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাস্থবির তিস্স সমগ্র বৌদ্ধসংঘের প্রধান বলে বিবেচনা করা কখনওই ঠিক হবে না। সম্ভবত তিনি যে সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন, তারা অন্য সব সম্প্রদায়ের মতবাদগুলােকে সাময়িকভাবে পরাস্ত করে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ থেকে পরােক্ষ প্রমাণ মেলে যে, সম্রাট অশােক বৌদ্ধ ধর্মের থেরবাদী, স্থবিরবাদীদের বা বিভাজ্জবাদীদের পৃষ্ঠপােষণা করেছিলেন। অথবা তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে স্বীকার না করে সমস্ত সম্প্রদায়কে পুনরায় এক করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় সংঘে তীর্থিক (Heretics) বলতে কেবলমাত্র অবৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরই বলা হত তা নয়। বৌদ্ধদের মধ্যে কেবলমাত্র থেরবাদী ও তার বিভিন্ন শাখা-উপশাখা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে বােঝানাে হত, যেমন আচরীয়বাদ বা মহাসাংঘিক ও তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাদেরও বােঝানাে হত। কারণ আচরীয়বাদ (মহাসাংঘিক) ও থেরবাদীদের মধ্যে বিনয় নিয়মগুলাে ছিল একেবারেই আলাদা। তাই একই ছাদের তলায় থেকে দুই সম্প্রদায়ের (হীনযান ও মহাসাংঘিক) আলাদা আলাদা প্রতিমােক্ষের অনুষ্ঠান বা উপােসথ পালন করা সম্ভব ছিল না। এটাই ছিল দু’দলের মধ্যে মতবিরােধের প্রধান কারণ।
যাই হােক, তৃতীয় সংগীতির সারাৎসার আলােচনা করলে যে কয়েকটা সত্য বেরিয়ে আসে তা হল –
- ১। বিভজ্জবাদী বা থেরবাদীরাই বৌদ্ধ ধর্মের এক ও একমাত্র মূল সম্প্রদায় বলে স্বীকৃত হয়েছিল। আর তাদেরই পুরাে প্রাধান্যে তৃতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- ২। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে তীর্থিকেরা সাময়িকভাবে ধর্মকে ম্লান করে রেখেছিল, কারণ সমস্ত সমকালীন প্রামাণিক গ্রন্থেই স্বীকার করা হয়েছে যে, পাটলিপুত্রে সাত বছর ধরে তীর্থিকদের প্রাধান্য বজায় ছিল বলে থেরবাদীরা সংঘে উপােসথ পালন সাত বছর বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।
- ৩। অবশেষে তীর্থিকদের পরাজয় ও থেরবাদীদের জয় হয় মােগ্ললিপুত্র তিস্সের নেতৃত্বে। দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে থেরবাদীরা যে সবশেষে জয়ী হয়েছিলেন—তৃতীয় সংগীতি সেই বার্তাই বহন করে।
- ৪| এই সংগীতিতে সম্রাট অশােকের ভূমিকা, অবদান ও তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোন দিকে ছিল তা খুব সঠিকভাবে বুঝে ওঠা দুষ্কর। সম্ভবত তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে বৌদ্ধ ধর্মের সংহতি ও একাত্মতা আনতে চেষ্টা করেছিলেন।
এরপর তৃতীয় সংগীতির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পরে মহাস্থবির মােগ্ললিপুত্র তিস্স সুদূর ভবিষ্যতেও সদ্ধম্ম যাতে স্থিতিশীল থাকে সেই কথা চিন্তা করে এক মহান কাজ করে বসেন, যা বৌদ্ধ ধর্মকে দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে দেয়। কথিত আছে, নয়টা দূর-সূদূর রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়জন ধর্মদূতকে পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবত এই মহান কাজে তিনি সক্রিয় রাজঅনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপােষকতা পেয়েছিলেন, যা একই সঙ্গে সম্রাট অশােককেও বহিঃবিশ্বে মহান ও অমর করে।
এরা হলেন। মজ্ঝন্তিক (মধ্যন্তিক) থেরকে কাশ্মীর-গান্ধার রাজ্যে। মহাদেবকে – মহিষমণ্ডল বা মাহিষ্মতীতে। রক্খিত (রক্ষিত) থেরকে – বনবাসীতে। যবন ও যােনক ধম্মরক্খিতকে – অপরান্তরাজ্যে। মহাধম্মরক্খত থেরকে – মহাবট্ঠ বা মহারাষ্ট্রে। মহারক্ষিত থেরকে— যবনলােকে বা যবনবিষয়ে। মজ্ঝিম থেরকে – হিমবন্ত প্রদেশে। সােন ও উত্তর থেরদেরকে – সুবন্নভূমি (সুবর্ণভূমিতে)। মহিন্দ থেরকে— তম্বপন্নি (তাম্রপর্ণীতে)।
সবশেষে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, সম্রাট অশােকের পৃষ্ঠপােষণায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল, তার তুলনা পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাসে একান্তই বিরল। ওই সময়কালের লেখ থেকে জানা যায় খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম পূর্বে ও দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরে কানাড়া ও মাহিষ্মতী পর্যন্ত, পশ্চিমে ব্রোচ ও সােপার, উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরে বিপুলভাবে বিস্তার ঘটেছিল।
প্রসঙ্গত বলা যায়, সম্রাট অশােকের ধর্মবিজয় সম্ভবত এখান থেকেই শুরু হয়। এই উপলক্ষে তিনি তার ছেলে মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু রূপে সিংহলে পাঠান। তারাই বৌদ্ধ ধর্মকে পৃথিবীর পূর্বদেশগুলােতে লাওস, কাম্বােডিয়া, ইন্দোচিন, চিন, জাপান ইত্যাদি ইত্যাদি দেশে প্রচার-প্রসার ঘটান। এ ছাড়াও পশ্চিম দেশগুলােতেও [গ্রিক শাসিত অঞ্চলগুলােতে যেমন সিরিয়া, ইজিপ্ট, সাইরিন (আফ্রিকায়) ও এপিরাস বা করিন্থে (গ্রিসে) অর্থাৎ সুদূর এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরােপে।] এই সময়েই বৌদ্ধ ধর্মের মহাবিপুল প্রচার-প্রসার ঘটে। এই কারণেই সম্রাট অশােকের নাম শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসেই নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আর সবশেষে যে কথা উল্লেখ না করলে অপূর্ণ থেকে যায় তা হল, এই মােগ্ললিপুত্ত তিস্য ছিলেন সম্রাট অশােকের সম্ভবত একমাত্র জীবিত সহােদর ভাই। বাকিদের (সহােদর ও বৈমাত্রেয় ) তিনি সিংহাসন দখলের লড়াইতে হত্যা করে ‘চণ্ডাশােক’ নামে পরিচিত হন। কলিঙ্গ যুদ্ধ ও সেখানে তার পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস ও বীভৎস হত্যালীলা এর পরের ঘটনা।
চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি
খ্রি. পূ. প্রথম শতাব্দীর কিছু আগে পরে, সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে, স্থবির বসুমিত্রের সভাপতিত্বে ও পণ্ডিত অশ্বঘােষের সহ-সভাপতিত্বে, জলন্ধরে নিমন্ত্রিত হয়ে, বহু শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুদের মধ্যে থেকে মাত্র পাঁচশাে জনকে নির্বাচন করে, এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
কথিত আছে যে সম্রাট কণিষ্ক বহু দেশ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পরে রাজকার্যের অবসরে, পার্শ্ব নামে এক স্থবিরের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। জানা যায়, এই সময়ে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতেন। ফলে তিনি ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তখন পার্শ্ব তাকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যদের নিজস্ব অভিমতের ফলে সমগ্র মূল বৌদ্ধ শাসনের এই দুরবস্থার কথা জানান। তখন সম্রাট সমস্ত সম্প্রদায়ের মতামত পর্যালােচনা করে ত্রিপিটকের নব-সংকলন ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বৌদ্ধ ধর্মকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে এক শাশ্বত সত্যধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠার জন্যেই এই মহাসভার আয়ােজন করেন।
উদ্দেশ্য যতই মহৎ হােক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এই সংগীতির মূল প্রেরণা ছিল সর্বাস্তিবাদী (মহাযান) সম্প্রদায়ের আয়ােজনে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মহা আয়ােজন। ঠিক এই একই ঘটনার উলটোটা ঘটেছিল তৃতীয় সংগীতিতে থেরবাদী বা স্থবিরবাদীদের হীনযান দ্বারা, সম্রাট অশােকের পৌরােহিত্যে ও পৃষ্ঠপােষণায়। তাই দেখা যায় এই চতুর্থ সংগীতির কোনও উল্লেখই পালি সাহিত্যে (বিশেষত সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে) পাওয়া যায় না। আবার তৃতীয় সংগীতির কোনও উল্লেখই সর্বাস্তিবাদী বা মহাসাংঘিকরা স্বীকার করেন। প্রথম থেকেই এই সংগীতির প্রস্তুতি পর্বে যে বিপুল সংখ্যক শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু সমাগম হয়েছিল তার মধ্যে থেকে মাত্র পাঁচশাে জনকে নির্বাচন করা হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক পাল্লা ভারীর কথা মাথায় রেখেই। এ ছাড়াও উত্তর ভারতের কাশ্মীর প্রদেশ ও সবশেষে জলন্ধরে সংগীতির স্থান নির্বাচনও করা হয়েছিল ওই একই উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে। আসলে সম্রাট অশােকের উপর যেমন থেরবাদী বা স্থবিরবাদীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, সেই রকমই সম্রাট কণিষ্কের উপরেও সর্বাস্তিবাদীদের (পরবর্তীকালের মহাযান সম্প্রদায়ের) যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাই এই দুই মহৎ (তৃতীয় ও চতুর্থ সংগীতি) প্রচেষ্টাতে খুব সূক্ষ্ম সম্প্রদায়গত স্বার্থবুদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। তবে এসব সত্ত্বেও প্রত্যেকটা সংগীতিরই ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

Growth of Buddhism 08 -
এই সংগীতিতে শীলবান, প্রজ্ঞাবান, পাঞ্চবিদ্যা ও ত্রিপিটক বিশারদ ভিক্ষুরা ত্রিপিটকের (সুত্র, বিনয় ও অভিধর্ম সর্বসম্মত) যথার্থ ব্যাখ্যা নিরূপণের জন্যে, বহু প্রাচীন নিদর্শন বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করে, প্রাচীন, অতি-প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের দুরূহ ভাষাগুলােকে বার বার পর্যালােচনা করে, সেগুলাের প্রকৃত অর্থ ও সম্পূর্ণ অর্থ নির্ধারণ করেন। এ ছাড়াও সমস্ত কঠিন প্রশ্নের পুত্থানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে নিঃশেষে সমস্ত বিশিষ্ট পদ ব্যঞ্জনের অর্থ ব্যাখ্যা ও টীকা নির্ধারণ করেন। ফলে এই সময়কাল থেকেই পিটক যুগের অবসান ঘটে ও তার পরিবর্তে পিটক গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থ বা বিভাষাগ্রন্থ বা বিভাষাশাস্ত্রের সূচনা হয়। এই বিভাষাগ্রন্থগুলােই পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মের সঠিক আকরগ্রন্থ বলে আদৃত হয়। সংগীতির সদস্যরা প্রথমে এক লক্ষ শ্লোকের ‘উপদেশশাস্ত্র’ নামে সূত্রপিটকের টীকা গ্রন্থ, এক লক্ষ শ্লোকের ‘বিনয়বিভাষাশাস্ত্র’ নামে বিনয়পিটকের টীকা গ্রন্থ, এক লক্ষ শ্লোকের ‘অভিধর্ম বিভাষাশাস্ত্র’ নামে অভিধর্মপিটকের টীকা গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে, সবসমেত মােট তিন লক্ষ শ্লোকের মূল ত্রিপিটকের টীকা গ্রন্থ বা বিভাষাশাস্ত্রগুলাে এই চতুর্থ সংগীতিতেই সংকলিত হয়, যার শব্দসমষ্টি সংখ্যা ছেষট্টি লক্ষ। এসব কথাই সংকলিত হয় সংস্কৃত ভাষায় (বুদ্ধদেব তার ধর্মপ্রচার কালে সংস্কৃত বা ছান্দস ভাষার ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। হয়তাে সর্বাস্তিবাদী মতে তার সময়কালের সত্য কালের প্রবাহে পরিবর্তনের প্রয়ােজনীয়তা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু থেরবাদী বিভাজ্যবাদী বা স্থবিরবাদীরা আজও পালি ভাষাকেই ধর্মের এক ও একমাত্র বাহক বলে মনে করেন। যদিও মূল ত্রিপিটক গ্রন্থের ভাষা ঠিক কী ছিল তা স্পষ্টভাবে আজও জানা যায়নি।) এই গ্রন্থগুলােই সর্বাস্তিবাদী বা পরবর্তীকালের মহাযান সম্প্রদায়ের সর্বপ্রাচীন আকরগ্রন্থ। এর পরবর্তীকালে মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের ধারক ও বাহক রূপে সংস্কৃত ভাষাকেই ব্যবহার করা হয়।
এ থেকে বলা যায়—
- ১। চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতে কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এখানে দক্ষিণাঞ্চলের ও সিংহল, ব্রহ্মদেশ বা শ্যামদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত। তাই বােধহয় একমাত্র কাশ্মীর প্রদেশকেই সদ্ধর্ম চর্চার পবিত্রভূমি বলে গণ্য করা হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য জায়গাগুলােকে সদ্ধর্ম চর্চা ও প্রচারের জন্যে প্রতিকূল মনে করা হয়েছিল।
- ২। এই সংগীতির সমগ্র উপাদানগুলাে পর্যালােচনা করলে বােঝা যায় যে, এই অধিবেশন বিশেষত মহাযান সম্প্রদায়েরই প্রভাবান্বিত অধিবেশন।
- ৩। ত্রিপিটকের পুনরালােচনা, পর্যালােচনা, বিভাষা বা টীকা গ্রন্থের উদ্ভাবন ও সর্বাস্তিবাদী সম্মত অভিধর্মপিটকের সংকলন। (প্রায় তিনশাে বছর) দীর্ঘদিনের মনান্তর, মতান্তর ও দলাদলির অবসান ঘটিয়ে মহাসাংঘিক বা সর্বাস্তিবাদী বা মহাযান সম্প্রদায় এই সংগীতি থেকেই প্রাচীনপন্থী থেরবাদী বা স্থবিরবাদী বা হীনযান সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা হয়ে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আত্মপ্রকাশ করে ও দেশে দেশে বিপুল ভাবে বিস্তার লাভ করে।
এই মূল চারটি প্রধান বৌদ্ধ সংগীতি ছাড়াও সিংহল বা শ্রীলঙ্কায় তিনটি, শ্যামদেশে বা থাইল্যান্ডে নয়টি ও ব্রহ্মদেশে বা মায়ানমারে দুইটি সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য এগুলাে সবই খােলাখুলি ভাবে সম্প্রদায়গত সংগীতি।
হীনযান ও মহাযান
তা হলে এখন মুল যে প্রশ্নটা এসে দাঁড়াচ্ছে তা হল, হীনযান ও মহাযান কাকে বলে? এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? আর হীনযানীরা কেন ‘হীন’ বা মহাযানীরাই বা কেন ‘মহান?
হীনযানের লক্ষ্য ছিল ব্যষ্টির মুক্তি আর মহাযানের লক্ষ্য হল সমষ্টির মুক্তি। তাই হীনযানীরা অৰ্হত্ব পেলেই খুশি, কিন্তু মহাযানীরা চায় বুদ্ধত্ব। অর্হৎও নির্বাণ লাভ করবেন, বুদ্ধও নির্বাণ পাবেন। তা হলে এ দুইয়ের মধ্যে তফাত কী? দু’দলই তাে জন্ম-জরা-মরণ-এর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে— বােধিজ্ঞান লাভ করবেন। তা হলে পার্থক্য কোথায়? মহাযানীরা বলেন— বুদ্ধদেব যখন বােধগয়ায় অশ্বত্থ গাছের তলায় সম্যক সম্বােধি লাভ করলেন, তখনই তিনি নির্বাণের জন্যে ব্যাকুল হলেন, শুনতে পেলেন—মগধ যে অধর্মের ভারে ডুবতে বসেছে, তার কী হবে? তখন তিনি মগধ উদ্ধারের জন্য বহুকাল বেঁচে থেকে ধর্ম প্রচার করলেন বলেই—তিনি বুদ্ধ। আর তার শিষ্যেরা আত্মােদ্ধারের চিন্তাতেই বিভাের তাই তারা—অর্হৎ।
থেরবাদীরা (হীনযানীরা) বা স্থবিরবাদীরা বুদ্ধদেবকে আর পাঁচজন মানুষের মতােই মানুষ বলে ভাবতেন, তাই তাদের কাছে বুদ্ধদেব ছিলেন লৌকিক। মহাসাংঘিক (মহাযান) মতে তিনি ছিলেন অলৌকিক নয়— লােকোত্তর। তাই মহাসাংঘিকদের লােকোত্তরবাদীও বলা হয়। তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েও জীবজগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। কারণ যখন তার মতাদর্শনকে লক্ষ লক্ষ লােক নিজেদের জীবনযাত্রার দিশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, আচার ব্যবহার স্থির করেছেন, তখন তার নশ্বর দেহ না থাকলেও, তার অনির্বচনীয় পরােক্ষ অস্তিত্বকে তাে কখনওই অস্বীকার করা যায় না। ফলে লােকোত্তরবাদীরা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দার্শনিকতার পথে পা বাড়াল। আর তখন স্থবিরবাদীরা বিনয় নিয়ম সম্বন্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকল, তাই হীনযানের শিক্ষা নিষেধমুখে আর মহাযানের শিক্ষা উপদেশ বিধিমুখে।
শ্রাবকানে সর্বপ্রথম ‘ত্রিশরণ’ গমন তারপরে ‘পঞ্চশীল’ গ্রহণ। গৃহস্থ ও ভিক্ষুরা এই দুই-ই করত। এরপরে ‘অষ্টশীল’ গ্রহণ অর্থাৎ পাঁচের উপর আরও তিন সুচন্দনাদি ত্যাগ (ফুলের মালা, চন্দন ও বিলাসদ্রব্য ত্যাগ), রূঢ়বাক্যপ্রয়ােগ ত্যাগ (জিহ্বসংযম) ও গীতবাদিত্রাদি ত্যাগ (গান-বাজনা ইত্যাদি করে কালক্ষেপ করবে না)। এই তিন শীল, খুব উচ্চ গৃহস্থ বা ভক্তের জন্যে, গৃহস্থ এর পরে আর যেতে পারবে না। তার উপরে আরও দুই শীল। অর্থাৎ দশশীল। এই দুই শীল হল —উচ্চাসন-মহাসন ত্যাগ ও কাঞ্চন ত্যাগ। এই দুই শুধুমাত্র ভিক্ষুদের জন্যে, এতে গৃহস্থের অধিকার নেই। এ ছাড়াও ছিল ‘পােষধ ব্রত’ অর্থাৎ উপােস করা— দুই অষ্টমীতে (শুক্ল ও কৃষ্ণ ), দুই চতুর্দশীতে (শুক্ল ও কৃষ্ণ), পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়। সেইদিনগুলােতে গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে ধর্মচর্চা করবে।
মহাযানীরাও ত্রিশরণ গমন ও শীল রক্ষা করেন। কিন্তু পােষধ ব্রতের কথা বড় একটা পাওয়া যায় না। দুই যানেই ত্রিশরণ গমনের মন্ত্র এক, তবে তাদের ক্রম আলাদা আলাদা। যেমন হীনযানে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ, কিন্তু মহাযানে ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ, বুদ্ধ এখানে দ্বিতীয় স্থানে। এখানে তিনি মানুষী বুদ্ধ, তাও আবার মানুষী বুদ্ধদের মধ্যে সপ্তম স্থানে। কারণ তারা বলেন, হিন্দুদের ব্যাসদেব যেমন সমস্ত কিছুকে কলমবন্দি করে গিয়েছেন, তেমনই তাদের ধর্মও অনাদি অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের (বৈরােচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমােঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য) মাধ্যমে। আবার এই দেবমণ্ডলের আদি দেবতা আদিবুদ্ধ। ইনিই সৃষ্টির আদি কারণ— শূন্য বা বজ্ৰ৷ ইনি সর্বব্যাপী-সর্বকারণ-সর্বশক্তির আধার ও সর্বজ্ঞ। সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে ইনি বিদ্যমান। তাই সবকিছুই স্বভাবশুদ্ধ, শূন্যরূপ নিঃস্বভাব ও বুদ্বুদ স্বরূপ। কেবল শূন্যতাই নিত্য। আদিবুদ্ধ সেই শূন্যের রূপকল্পনা। এই আদিবুদ্ধ থেকেই পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উদ্ভব। শাক্যসিংহও তেমনইভাবে সবকিছুকেই কলমবন্দি করেছেন। (প্রসঙ্গত বলা যায়, বুদ্ধদেব তার কোনও কথাই লিখিত আকারে রেখে যাননি। সবকিছুই ছিল শ্রুতিতে। লেখ্যকাল তার মহাপরিনির্বাণের পরবর্তী।) তাই নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূচৈত্যের চারিদিকে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির আছে। পূর্বদিকে অক্ষোভ্য, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্নসম্ভব ও উত্তরদিকে অমােঘসিদ্ধি, আর প্রথম ধ্যানীবুদ্ধ বৈরােচন বসলেন স্তূপের ঠিক মাঝখানে। সেখানে তিনি বুদ্ধদেব, চৈত্যের চারিদিকে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের দ্বারপাল। তাই মহাযানে বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্মই বড় আর সেখানে স্তুপ বা চৈত্যই হল ধর্ম। সংঘ বলতে এক বিহারে যতজন ভিক্ষু থাকে তাদেরকেই বােঝায়, কিন্তু ক্রমে তা বােধিসত্ত্বে পরিণত হয়েছে। আবার গােড়ায় যা ছিল ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ, মহাযানের যখন খুবই বাড়-বাড়ন্ত তখন তা হল – প্রজ্ঞা (ধর্ম), উপায় (বুদ্ধ) ও বােধিসত্ত্ব (সংঘ)।

-
দেখতে দেখতে প্রজ্ঞাঠাকুরানি বুদ্ধের শক্তি হয়ে দাঁড়ালেন, কারণ উপায় পুংলিঙ্গ আর প্রজ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ। এদের সংযােগে বােধিসত্ত্বের উৎপত্তি হল। কিন্তু প্রজ্ঞা নিষ্কাম ও নিষ্ক্রিয়, উপায়ও নিষ্কাম ও নিষ্ক্রিয়। সুতরাং সৃষ্টি স্থিতি লয় চলে না। তাই বুদ্ধ ও ধর্মের চেয়ে বােধিসত্ত্বের পূজা বেশি বেশি করে হতে লাগল। কারণ নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়ের উপাসনা করে সাধারণ মানুষের কী লাভ হবে? তখন সকাম সক্রিয় শক্তির উপাসনা শুরু হয়ে গেল। অনেকজন বােধিসত্ত্ব ঠাকুরের আবির্ভাব হল। এদের মধ্যে অবলােকিতেশ্বরই (অমিতাভ ও তার শক্তি পাণ্ডরার সংযােগেই অবলােকিতেশ্বরের উৎপত্তি) প্রধান।
হীনযানীরা ধর্মনীতি আর সমাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। তাই তারা মনে করেন স্বভাব-চরিত্রে শুদ্ধিকরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পার্থিব কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙক্ষা ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে। তখন তা কোনও উচ্চতর আকাঙক্ষা বা মহতের দিকে ধাবিত হয়। আর একবার তা স্রোতে পড়ে গেলে সে আর ফেরে না। ক্রমাগত স্রোতের অভিমুখেই (অর্হত্বের দিকে) ভেসে চলে (স্রোতাপন্ন সকৃদাগামী অনাগামী) এরপরে অর্হৎ হয়েও কিন্তু তখনই তারা নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করেন না। ভবিষ্যবুদ্ধের কাছে উপদেশিত হয়ে নির্বাণ লাভের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। অর্থাৎ তারা কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় ভাবতেন।
মহাসাংঘিকরা মনে করতেন বিনয়-নিয়ম-পালন প্রাথমিক ভাবে দরকার। কিন্তু একটা সময়ের পরে কর্ম-চরিত্র-বিনয় নিয়ম পালনের দ্বারা আর অগ্রসর হওয়া যায় না, তখন চাই জ্ঞান। তার উপকরণ হল আলাদা। তাই তারা দার্শনিক মত ও পারমিতা নিয়ে ব্যস্ত। তারা মানুষকে জ্ঞানময়, কর্মময় ও সর্বনিয়ন্তা করার চেষ্টা করতেন, এদের জীবনীশক্তি বড় বেশি, তাই (এদের) এক পারমিতার নামই ‘বীর্য’ অর্থাৎ বীরত্ব বা উৎসাহ। এ শুধু সামান্য উৎসাহ নয়, এ এমনই এক উৎসাহ যার থেকে বেশি আর কল্পনা করা যায়। না। তাই এরা দর্শনে শূন্যবাদী, নীতিতে করুণাবাদী, সকল জীবে করুণা করাে। এই হল মহাযানের সারাৎসার। মহাসাংঘিকরাই বুদ্ধর উপর দেবত্ব আরােপ করে তার বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের পূজা (রিক্তআসন, ধর্মচক্র, বােধিপত্র, পদ্ম, পাদুকা, পূতাস্থি ইত্যাদি) শুরু করেন, পরবর্তীকালে বুদ্ধমূর্তি তৈরি করে তার পূজা ব্যবস্থারও প্রচলন করেন। তখন থেকেই বিহারগুলােতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও বলা হল তিনি ত্রিকায় (নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্মকায়) চিরন্তন, শাশ্বত ও অক্ষর (উৎপত্তি ও ক্ষয় রহিত), তিনি সত্য সুন্দর ও সৃষ্টির শেষ, অবর্ণনীয় ও অনির্বচনীয়।
এই সব আলােচনা থেকে বলা যায় হীনযানীরা ছিলেন দুঃখবাদী নিরানন্দময় (বৌদ্ধ ধর্মের মূলসূত্র ঐকান্তিক দুঃখবাদ-এ বলা হয় জগৎ দুঃখময়, জন্ম দুঃখময়, দুঃখময় জরা-ব্যাধি ইত্যাদি জীবনের প্রায় সবই দুঃখময়)। কিন্তু মহাযানীরা ছিলেন আশাবাদী। তাই বলা হয়, হীনযান মতবাদ হল নীতিসর্বস্ব। আর মহাযান মতবাদ হল ভাবাবেগ জড়িত ও প্রধানত দর্শনমূলক। তাই সাধারণ মানুষ মহাযান মতের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল ও এই মতবাদ সমাজে বিশেষভাবে আলােড়ন তুলেছিল, যার পরিণামে চিন, জাপান ও কোরিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান মতবাদ বিপুল ভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করে। আর হীনযান ধর্ম শুধুমাত্র শ্রীলঙ্কায়ই অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায় বৌদ্ধ ধর্মের দুই সম্প্রদায়ই এক সময়ে মােট (১০+৭) আঠারােটা উপ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সংঘ বিভাজনের পরে এরা এদের নিজস্বতা হারিয়ে মূলে ফিরে আসে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হীনযান সম্প্রদায় ভারতবর্ষ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু মহাযান সম্প্রদায় কালের প্রবাহে বিবর্তিত হতে থাকে মহাযান→মন্ত্রযান→বজ্রযান→সহজযান→কালচক্রযান-এ। কিন্তু তারা সগৌরবে নিজেদের মূল যে মহাযান একথা স্বীকার করতেন, অর্থাৎ তারা যে মহাযানী সম্প্রদায়েরই বিবর্তিত রূপ একথা গর্বের সঙ্গেই উল্লেখ করতেন।
মহাসাংঘিক থেকে মহাযানে পরিণত হতে তিনশাে বছর সময় লেগে গিয়েছিল এ কথা আগেও বলা হয়েছে। মহাসাংঘিকদের মাত্র একখানা ‘মহাবস্তু অবদান’ গ্রন্থ আজ অবধি পাওয়া গিয়েছে। এর আগেও ‘লঙ্কাবতার’ ইত্যাদি নামে তিনখানা মহাযান সূত্র প্রচলিত ছিল। এর পরবর্তী কালে অশ্বঘােষ-এর ‘মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র’ ছাড়াও তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বুদ্ধচরিত’ এবং ‘সৌন্দরানন্দ’ মহাযান মতবাদে ভরপুর। এর পরই আসেন দক্ষিণ ভারতের সন্তান, নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ আচার্য নাগার্জুন (২য় শতক)। একেই মহাযান মতের প্রবক্তা বলে অনেকেই ধারণা করেন। ‘মাধ্যমিকবৃত্তি’ ও ‘প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র’ এই দুই বিখ্যাত গ্রন্থই মহাযানের স্তম্ভস্বরূপ। তিনি বুদ্ধদেবের ‘মধ্যমপন্থা’ দিয়েই শূন্যতা বা শূন্যবাদকে (Indescribable absolute) মুখ্যরূপে উপস্থাপন করে তার দার্শনিক মতবাদের প্রচলন করেন। সে যুগে ভারতবর্ষে শূন্যবাদ যথেষ্ট আলােড়ন তুলেছিল। এ ছাড়া তিনি দার্শনিক বিরােধিতা অর্থাৎ সমস্ত কিছুকেই ‘অস্তিনাস্তি’ (Dialectic) পরিপ্রেক্ষিতে চারভাবে বিচার করে সমস্ত প্রশ্নকে খণ্ডন করার পদ্ধতির প্রবর্তক (হাঁ; না; ও না হ্যাঁ দুটোই; হাও নয় নাও নয়)। যদিও এই অস্তিনাস্তি বিচারের (Dialectic) উৎপত্তি বুদ্ধদেবের থেকেই, কারণ তিনি চোদ্দোটা প্রশ্নকে অব্যাকৃত বা ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে বলে ঘােষণা করেছিলেন।
নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শনের মূল সূত্রই হল শূন্যতা। এই শূন্যতা, সংসার ও নির্বাণ একই সূত্রেই গ্রথিত, সবাস্তিবাদের আপােসহীন বাস্তববাদ বা যােগাচারের আদর্শবাদ এই দুইয়ের কোনওটাকেই তিনি গ্রহণ করেননি। তার প্রচলিত শূন্যতা বা শূন্যবাদ এক উন্নততর অবস্থা। যেখানে অস্তি অর্থে শাশ্বত, নাস্তি অর্থে অশাশ্বত, নিত্য অনিত্য বা আত্মা অনাত্মাকে স্বীকার না করে—এক আপেক্ষিক সম্বন্ধমাত্র (relative) বলেছেন। এখানে সত্য এক নয় দুই, সংবৃতি বা ব্যাবহারিক, অজ্ঞান বা মােহ, আর পরমার্থ হল লােকোত্তর বা পরমার্থিক ছাড়াও শূন্য, বা শূন্যতা বা নির্বাণ। তাই সংবৃতি হল উপায় আর পরমার্থ হল পরিণাম। নাগার্জুনের পরবর্তী মাধ্যমিক আচার্য হলেন তাঁর শিষ্য আর্যদেব (৩য় শতাব্দী)। তিনি ওই মতবাদকে দেশেবিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন, তাই একে অধ্যাত্মবিদ্যার চূড়ান্ত বলা হয়। এরা দুজনেই মহাযানের দুই আদি স্তম্ভ বিশেষ। এরপরে বুদ্ধপালিত ভাববিবেক (৫ম শতাব্দী), চন্দ্রকীর্তি (৬ষ্ঠ শতাব্দী), এর লেখা ‘প্রসন্নপদা’ টীকাগ্রন্থ বিপুল জনপ্রিয়তা পায় ও শান্তিদেব (৭ম শতাব্দী)।
আচার্য নাগার্জুন যখন নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তার সঙ্গে অন্যান্যদের কতগুলাে বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। যার ফলে মহাযান সম্প্রদায় দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, মাধ্যমিক (নাগার্জুন) ও যােগাচার বা বিজ্ঞানবাদ (মৈত্রেয়নাথ ৩য় শতাব্দী)। তবে এই দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা ছিলেন অসঙ্গ (৪র্থ শতাব্দী) ও তার ভাই বসুবন্ধু (ইনি দীর্ঘকাল নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন, ‘বিজ্ঞপ্তিমাত্ৰতা সিদ্ধি’ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা)। বােধিলাভের জন্যে যােগমার্গকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করেন বলেই এঁদের যানকে মার্গ যােগাচার দর্শন বলে। অসঙ্গই বৌদ্ধ ধর্মে সর্বপ্রথম তান্ত্রিকতা বা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপকে অনুপ্রবেশ করান। তার সংস্কৃত রচনা ‘মহাযান-সূত্রালংকার’ ও ‘বােধিসত্ত্বভূমি’তে বােধিজ্ঞানলাভের জন্যে যে দশটা স্তর (দশভূমি) অতিক্রম করতে হয় তারই বর্ণনা আছে। দশভূমি হল— প্রমুদিতা (আনন্দ পূর্ণমূল), বিমলা (অকলঙ্ক, বিশুদ্ধমূল), প্রভাবরী (পবিত্র প্রভাযুক্তস্থান), অর্চিষ্মতী (বীর্যযুক্ত উজ্জ্বল স্থান), সুদুৰ্যয়া (দুয়ে অভিমুখী), (প্রতীতসম্পন্নের দিকে অভিমুখী স্থান), দুরঙ্গমা (ধ্যানযােগে দূরে গমন করার জায়গা), অচলা (স্থিরাবস্থানের জায়গা), সাধুমতী (কুশল চিন্তার স্থান) ও ধর্মমেঘা (ধর্ম বা জ্ঞানের মেঘযুক্ত স্থান)। এ ছাড়াও তাঁর গ্রন্থে গুপ্ত প্রভাবপূর্ণ গূঢ় মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়ােগ সম্পর্কেও যথেষ্ট আলােচনা আছে। দর্শনের ব্যাবহারিক দিকটাই এখানে দেখানাে হয়েছে তাই এই যােগাচারদর্শনকে বিজ্ঞানবাদও বলা হয়। এই দর্শন একান্তভাবে আদর্শবাদী। এদের মতে সমস্ত কিছুরই যথার্থ অস্তিত্ব নেই, একমাত্র বিজ্ঞান, চিত্ত বা মনই একমাত্র সত্য আর বাকি সব মিথ্যা। এককথায় বলা যায় বিজ্ঞানমাত্রই এই দর্শনের পারমার্থিক সত্য। এখানে বিজ্ঞানও দুইভাবে স্বীকৃত-প্রকৃতি বিজ্ঞান (প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াই প্রকৃতি বিজ্ঞান) ও আলয় বিজ্ঞান বা জ্ঞানসমষ্টি (যা সমস্ত ধর্মের বীজম্বরূপ)। আবার আলয় অর্থাৎ যা স্রোতের মতােই পরিবর্তিত হচ্ছে, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সঙ্গেই এর পরিসমাপ্তি। এ ছাড়াও বলা হয় আলয় ভালমন্দ সমস্ত ধর্মেরই বীজ বহন করে (টীকা—স্থিরমতি)।
যােগাচার মতে এই বিশ্ব স্বপ্নের মতাে অলীক, তথতা বা ধর্মধাতু; নাগার্জুন একে শূন্যতা বলেছেন, যা একমাত্র সত্য। এখানে নৈরাত্ম্যও দুই ধরনের আত্মার অনস্তিত্ব ও পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর অনস্তিত্ব। আর সত্য তিন প্রকার—পরিকল্পিত (কল্পনাপ্রসূত), পরতন্ত্র (পরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত) ও পরিনিষ্পন্ন (সর্বোত্তম বা পরমার্থিক সত্য)।
অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর পরে যােগাচার দর্শন শাখার বিখ্যাত দার্শনিক ও তর্কশাস্ত্রবিদেরা হলেন—স্থিরমতি, দিগ (৫ম শতাব্দী), ধর্মপাল (৭ম শতাব্দী), ধর্মকীর্তি (৭ম শতাব্দী), শান্তরক্ষিত (৮ম শতাব্দী) (ইনি নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন ও আচার্য শীলভদ্রের গুরু। এই শীলভদ্রের কাছেই হিউ-এন সাং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।) ও কমলশীল (৮ম শতাব্দী) ইত্যাদি।
বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে সংঘে মনান্তর-মন্তর দলাদলি-ঠেলাঠেলির পরিশেষে, সংঘভেদ ছাড়াও, সম্রাট অশােকের পৃষ্ঠপােষণায়, তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ও দেশে-বিদেশে ধর্মদূত প্রেরণের ফলে, এক সুবিশাল ভৌগােলিক অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা, বহু বৈচিত্র্যময় সামাজিক মানসিক মানব গােষ্ঠীর কাছে বৌদ্ধ ধর্মকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিঘাতে, এই ধর্ম অনিবার্যভাবে ক্রমবিবর্তিত হতে থাকে। তাই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর ক্রমবিকাশের ধারায় তিন তিনটে স্তর বা পর্ব রয়েছে। যদিও এই স্তরায়ণ খুব একটা কালানুক্রমিক নয়, মূলত দার্শনিক তবুও কালকে স্থানকে ও পাত্রকে (বহু বহু বৈচিত্র্যময়) কখনওই অস্বীকার করা যায় না। তাই এর প্রাথমিক স্তর হল—আভিধার্মিক স্তর অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর থেকে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত এই সময়কাল তার গুঢ় শিক্ষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশের স্তর (যা প্রধানত ২য় শতাব্দী থেকে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত)। আর সবশেষে মন্ত্রতন্ত্র সংবলিত বৌদ্ধ ধর্মের স্তর, যার বিকাশ ঘটেছিল ৫ম শতাব্দী থেকে হাজার শতাব্দী পর্যন্ত।
প্রাথমিক স্তরে বৌদ্ধ ধর্মের আদিরূপ অক্ষুন্নই ছিল। যা প্রধানত মনােবিদ্যাগত বা বাস্তববাদী সাধারণের মানসিকতার বিশ্লেষণ আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধ্যানযােগ। ওই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের সমস্ত কিছুই ছিল পালি ভাষায় লেখা।
দ্বিতীয় পর্বে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। ধর্ম সংক্রান্ত বিধানগুলাের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার প্রবণতা। যেমন বােধিসত্ত্বের ধারণা (যিনি বুদ্ধত্ব বা বােধিজ্ঞানের পথে এগিয়ে গিয়েছেন) আদর্শযুক্ত হয়েছিল। এই আদর্শানুসারে যে-কোনও মানুষ (গৃহী বা সন্ন্যাসী) পুণ্য কাজের ফলে, যােগ্যতা অর্জন করে বুদ্ধত্বলাভ করতে পারেন। প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের চর্চা করে বস্তুর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করাই ছিল এ যুগের বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ। এই সময়কালের গ্রন্থগুলাে সংস্কৃত ভাষা বা বৌদ্ধ সংস্কৃত (মিশ্র) ভাষায় লেখা হয়।
বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমপরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্ম তন্ত্রযানে বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই সময়ে বেশ কয়েকটা তান্ত্রিকশাখা (মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান ইত্যাদি) গড়ে উঠেছিল। ফলে গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মমতে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সেখানে হিন্দুদের মতাে বৌদ্ধ ধর্মেও দেব-দেবীর ঘনঘটা দেখা যায়, তখন তা এক সম্পূর্ণ নতুন ধর্মের রূপ নেয়; যেখানে মন্ত্র, তন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস, মণ্ডল ইত্যাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যােগবিধি, মায়াবিদ্যা, যৌন অতীন্দ্রিয়বাদ, আদি বুদ্ধ, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, বােধিসত্ত্ব ও এঁদের প্রত্যেকের (শক্তি) স্ত্রী-রা ছাড়াও পিশাচী, মাতঙ্গী, ডাকিনী, যােগিনী ইত্যাদিরাও মহাসমাদরে স্থান পায়। এরা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতালাভ করার জন্যেই এই (মার্গ) যানকে বেছে নেন।
ধর্মের এই ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-শিষ্য সম্পর্কেরও আমূল পরিবর্তন ঘটে। যেমন বুদ্ধদেব যখন নন্দকে ‘প্রবজ্যা’ দিয়েছিলেন তখন তিনি তাকে বৈদেহ মুনির হাতে সমর্পণ করেছিলেন। বৈদেহ মুনিও নন্দকে বন্ধুর মতােই দেখতেন, তাকে পরামর্শ ও শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধদেব মাঝেমধ্যে খবর নিতেন, যেখানে বৈদেহ মুনি অক্ষম হতেন তিনি নিজে তা বুঝিয়ে দিতেন। অর্থাৎ বুদ্ধদেব, বৈদেহ মুনি ও নন্দের মধ্যে সম্পর্ক ‘উপাধ্যায়’ হলেও সকলেই সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। মহাযান সম্প্রদায়ে উপাধ্যায়কে কল্যাণমিত্র বলত। এই শব্দ থেকেই বােঝা যায় দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কী রকম ছিল। মহাযানীরা খুবই দর্শন চর্চা করতেন। তাই দু’জনের মধ্যে উপলব্ধির স্তরে ফারাক যতই বেশি থাকুক না কেন, সংঘে দু’জনের অধিকারই ছিল সমান। সমান—মিত্ৰতামূলক।
ক্রমে (সাধারণ স্তরের) ভিক্ষুরা যারা সংখ্যায় বেশি, তারা এত দর্শন, যােগ ও ধ্যানকে ভীষণ কঠিন বলে ভাবতে লাগল। আবার ভিক্ষুরা বিয়ে করে বিশাল এক গৃহস্থ ভিক্ষু শ্রেণির সৃষ্টি করল। তারা বলল প্রজ্ঞাপারমিতা পড়তে অনেক সময় লাগে, বুঝতে আরও বেশি দিন সময় লাগে। এসব সকলের জন্যে নয়, তাই মন্ত্র জপ করাে। তা হলেই পাঠ, স্বাধ্যায়, জপ ইত্যাদি সমস্ত ধর্মকর্মেরই ফল পাওয়া যাবে। ধর্মের এই অবস্থায় গুরু শিষ্যের সম্পর্কটা বেশ আঁটসাঁট হয়ে উঠল, তখন বলা হল গুরুপ্রসাদ (গুরুকে ভক্তি), শিষ্যপ্রসাদ (শিষ্যকে স্নেহ) ও মন্ত্রপ্রসাদ (মন্ত্রের প্রতি আস্থা)। এই সময়েই বৌদ্ধ ধর্মে মন্ত্রযানের উদ্ভব হয়। এরপরে বজ্রযানে গুরু আরও বড় হয়ে উঠলেন। কারণ তিনি স্বয়ং বজ্রধারী বা বজ্রাচার্য। তাই একজন বড় ও অন্যজন ছােট হয়ে গেল। তখন আর সমান সমান ভাবটা থাকল না। এরপরে সহজযানে গুরুর উপদেশই সব। তাই গুরুর কথায় মহাপাপ করলেও তাতে মহাপুণ্য হবে। এমনকী বলা হয় যে, পঞ্চকাম উপভােগের ফলে মুর্খলােক বদ্ধ হয়, তাও নাকি গুরুর উপদেশ নিয়ে করলে সে মুক্ত হয়। গুরুর উপদেশই এখানে অমৃতরস। এর পরে কালচক্রযান-এ গুরুর স্থান কোথায় তা বােঝাতে গেলে বলতে হয় ‘লঘুকালচক্রতন্ত্র’-এর’ টীকা ‘বিমলপ্রভা’র লেখক পুণ্ডরীক নিজেকে অবলােকিতেশ্বরের নির্মাণকায় বা অবতার বলে মনে করতেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং অবলােকিতেশ্বর ছাড়া আর কেউ নন। এরপরে লামাযানের সবাই কোনও-না-কোনও অবলােকিতেশ্বরের অবতার। সুতরাং তিনি সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ ও সাক্ষাৎ বােধিসত্ত্ব। সব শেষে লামাযান ক্রমে দলাইলামাযানে পরিণত হল। এরা সবাই অবলােকিতেশ্বরের অবতার, তাই মৃত্যুহীন, তবে মধ্যে মধ্যে এক কায় ত্যাগ করে কায়ান্তর ধারণ করেন।
এখন মূল প্রশ্নটা এসে দাঁড়াল বৌদ্ধ ধর্মে তন্ত্রের প্রভাব কোন সময় থেকে শুরু হয়। এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলের বিভিন্ন মতামত আছে, যেমন অসঙ্গই সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটান। কথিত আছে তিনি এই গুহ্যবিদ্যা তুষিত স্বর্গে অবস্থিত ভবিষ্যৎ বুদ্ধের (মৈত্রেয়) কাছ থেকে দীক্ষিত হয়ে সংগ্রহ করেন। আবার অন্য মতে মাধ্যমিক দর্শনের স্তম্ভ আচার্য নাগার্জুনই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা। তিনিও নাকি ওই গুহ্যবিদ্যা স্বর্গীয় বুদ্ধ বৈরােচনের বােধিসত্ত্ব বজ্রসত্ত্বের কাছ থেকে দক্ষিণ ভারতে শিক্ষালাভ করেন। আবার অন্য মতে নাগার্জুন ওই বিদ্যা সহরপাদ নামে এক বিখ্যাত সিদ্ধাচার্যের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন। অসঙ্গের একখানা মহাযান গ্রন্থ ‘সূত্রালংকার’-এ তান্ত্রিক যৌনাচারযুক্ত যােগসাধনার(পরাবৃত্তি—মৈথুনস্য পরাবৃত্তি) বর্ণনা আছে। এই গুহ্য পরম ও চরম সুখকর (একে মহাসুখ বলে) মিলনের মর্মার্থই ‘সূত্রালংকার’-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা তান্ত্রিক ধর্মে (অতীন্দ্রিয়বাদ) এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, আর এর মাধ্যমে (পরাবৃত্তি) যােগবিধিতে সর্বোত্তম স্থান লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস। এ ছাড়াও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে যৌনাচারের পরাবৃত্তি বলতে বুদ্ধ ও বােধিসত্ত্বদের গুহ্যশক্তি যুক্ত মিলনকেই বােঝায়।
‘তন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ’ আলােচনা প্রসঙ্গে একথা বিস্তারিত ভাবেই আলােচিত হয়েছে যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতে কীভাবে কৃষি→মাতৃকা শক্তি→নারী পুরুষের প্রাকৃতিক স্বাভাবিক সম্পর্ককে স্বীকার করে তাকে ধর্মে স্থান দেওয়া→বিভিন্ন নেশার জিনিসে নারীপুরুষের স্বাভাবিক আসক্তিকে ধর্মে স্থান দেওয়া→দেহকে কেন্দ্র করে যােগাচারের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয়তা লাভের প্রচেষ্টা→বহু বহু পরবর্তীকালের আগম শাস্ত্র→পরিণত রূপে তন্ত্রশাস্ত্র। কথিত আছে ধর্ম-দর্শন জগতে এই সনাতন অতি প্রভাবশালী ধারার কথা বুদ্ধদেবেরও মােটেই অজানা ছিল না, তিনি (নাকি) স্বয়ং তার উচ্চমননশীল অনুগামীদের জন্যে এই মার্গের প্রবর্তন করেন। তবে তা খুবই মুষ্টিমেয়ের জন্যে এবং অত্যন্ত সংগােপনে। এ বিষয়ে ড. বিনয়তােষ ভট্টাচার্যের মতামত হল —যদিও বুদ্ধদেব সবরকম যাগযজ্ঞ, পশুবলি, জাদুবিদ্যা, ডাইনি ও পিশাচতন্ত্র ইত্যাদির বিরােধী ছিলেন, তবুও তার দেশনায় মুদ্রা, মণ্ডল, তন্ত্র ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিল। কারণ তার সময়কালে ভারতবর্ষ এত বেশি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল যে, কোনও ধর্মের পক্ষেই কিছু কিছু অলৌকিকত্বের ব্যবহার দেখানাে ছাড়া অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন ছিল। তাই বুদ্ধদেবও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বহুজনকে সহজেই আকর্ষণ করার জন্যে তার ধর্মে অলৌকিক গুহ্য সাধনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। তার চারটে (ঋদ্ধিঃ) অলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্ত ছিল। সেগুলাে তার উচ্চমননশীল ভিক্ষুদেরও করায়ত্ত ছিল। আচার্য শান্তরক্ষিতের ‘তত্ত্ব সংগ্রহ’ ও কমলশীলের ‘টীকাগ্রন্থে’ আছে যে—মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ইত্যাদি বুদ্ধদেব স্বয়ং দেশনা করেছিলেন, তার উপাসকদের কল্যাণার্থে। আবার তার বিভিন্ন ধরনের দেহভঙ্গি বা অঙ্গবিন্যাসও অতীন্দ্রিয়বাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাই খুব সম্ভবত প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্র-তন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ইত্যাদি পরবর্তীকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের পথ প্রশস্তই করেছিল।
অসঙ্গকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক বলে চিহ্নিত করা হলেও, তার বহু বহু আগেকার কালে আগমশাস্ত্রে তান্ত্রিকতার মূল উপাদানগুলাে ছিল। এ সম্পর্কে অভিনবগুপ্তের ‘তন্ত্রালােক’ (১০ম শতাব্দী)-এ উল্লেখ আছে। তাই হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র পর্যালােচনা করলে দেখা যাবে যে এই দুইয়েরই অতীত সাংস্কৃতিক পটভূমি এক ও অভিন্ন।মন্ত্রযান
এই তত্ত্বকথা বাদ দিলেও বলা যায় বৌদ্ধ ধর্ম এই বিপুল সময়কালে (৯-১০ শাে বছরে) দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে যােগ দিতে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের আগে তারা তাে কোনও-না-কোনও ধর্মের মানুষ ছিল, সেখানে ছিল তাদের সমাজ-সংসার, সংস্কৃতি, আচার-বিচার ইত্যাদি। তারাই যখন বৌদ্ধ হল, তখন তারা তাে তাদের পূর্বাশ্রমের সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে আসেনি। যেগুলাে তাদের স্বাভাবিক ও সহজাত ছিল, সেগুলােকে তারা সঙ্গে নিয়ে এল। ফলে বৌদ্ধদের মধ্যে চিরকালই এক সাংস্কৃতিক মহাসমন্বয়ের রসায়ন ছিল। সাধারণ মানুষের সংখ্যা চিরকালই সবকিছুতেই বেশি তাই তাদের জীবনচর্চা, বােধ, বিশ্বাস, নারী-পুরুষের সহজ সরল প্রাকৃতিক সম্পর্ক সনাতন বৌদ্ধ ধর্মের উপরে ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকে। এ ছাড়াও সংঘে নারীর অধিকার বুদ্ধদেব দিতে চাননি। পরে বহু অনুরােধে নিমরাজি হলেও ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন—সংঘে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদ্ধর্মের আয়ুও অর্ধেক হয়ে গেল। ফলে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক অলঙ্ঘ্য আকর্ষণ সংঘকে বিভিন্ন সময়ে বিড়ম্বিত করেছে। পরবর্তীকালে ভিক্ষুরা বিবাহ করতে থাকে। তখন তাদের গৃহস্থ ভিক্ষু বলা হল। সমাজে এদের কদর আসল। ভিক্ষুদের থেকে অনেক কম হলেও ক্রমে এরা দলে ভারী হতে থাকে। এদের সন্তান-সন্ততিরা আপনা আপনিই ভিক্ষু হয়ে যেত। যেখানে প্রকৃত ভিক্ষুকে গৃহাশ্রম ছাড়ার পরে প্রথমে ত্রিশরণ গ্রহণ পরে পুণ্যানুমােদনা শিখতে হত। তারপরে পাপদেশনা শিখতে হত, এরপরে পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও দশশীল গ্রহণ করে পােষধব্রত ধারণ করা ছাড়াও আরও অনেক কিছুই করতে হত। এতে করে অনেক সময় লেগে যেত। কিন্তু গৃহী ভিক্ষুর সন্তানেরা গৃহেই এসব শিখে নিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হত। যখন এরা দলে ভারী হল তখন গৃহী ভিক্ষুর দলকে ‘জাত ভিক্ষু’ বলা হতে থাকল। এই জাত ভিক্ষুদের আর্থিক অবস্থা দিনে দিনে যত ভাল হতে থাকল, প্রকৃত ভিক্ষুদের অবস্থা ততই খারাপ ও নিম্নমানের হতে থাকল।
জাত ভিক্ষুরা বিভিন্ন পেশায় চিত্রকর, ভাস্কর, স্যাকরা ইত্যাদি কারিগরির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দু’পয়সা রােজগার করে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করল। কিন্তু বেশি লেখাপড়ার ধার ধারত না। কিন্তু মহাযান ধর্ম খুব উঁচু দরের দার্শনিক ধর্ম, তা বুঝতে গেলে বহুকাল ধরে পড়াশুনা, ভাবনাচিন্তা ও অধ্যবসায়ের দরকার কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সেই ক্ষমতা, সময় ও নিষ্ঠা নেই তাই এক সহজ রাস্তা বার হল—ধারণী মুখস্থ করাে, ধারণী জপ করাে ও ধারণীর পুথি পূজা করাে। — (ধারণী ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের সাহায্যে উচ্চারিত মন্ত্র বিশেষ)। তা হলে মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায় ও যােগের সমস্ত ফল পাওয়া যাবে। যেমন ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’ এক বিশাল গ্রন্থ তা পাঠ, আয়ত্ত ও অভ্যাস করতে বহুদিন লেগে যায়, তা ছাড়া এ কাজ সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়, তাই ‘প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়ধারণী’ মুখস্থ করাে, তা হলে তার সব ফল মিলবে। এভাবে কত যে ধারণী তৈরি হল তা গুনে শেষ করা যায় না। এক ‘বৃহদ্ধারণী সংগ্রহ’-এই চারশাে এগারােটা মন্ত্র আছে। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখন এক অক্ষর দুই অক্ষর (হুং, ফট, ক্রীং, স্বাহা) ইত্যাদি শব্দের (বীজমন্ত্রের) ব্যবহার হতে লাগল, বৌদ্ধেরা এতেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে লাগল। যে মহাযান ধর্ম এক সময়ে চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠেছিল মন্ত্রনে এসে তাইই হুং, ফট, ক্রীং, স্বাহায় এসে দাঁড়াল। বােধিসত্ত্বের ধারণী হল চার প্রকারের ধর্মধারণী (স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও বল-এর মন্ত্র), অর্থধারণী (ধর্মের অর্থের মন্ত্র), মন্ত্র ধারণী (পূর্ণতালাভের মন্ত্র) ও বােধিসত্ত্ব ধারণী (নিবৃত্তি লাভের ধারণী)। আবার প্রং এই বীজমন্ত্র কোনও দেব-দেবীর সাংকেতিক চিহ্ন বিশেষ। তারপরে ‘প্রজ্ঞাপারমিতা ধারণী’র মাধ্যমে তাই হল প্রজ্ঞাপারমিতা মন্ত্র। এইভাবে ‘অ’ বৈরােচনের, ‘য়’ অক্ষোভ্যর, ‘র’ রত্নসম্ভবের, ‘ব’ অমিতাভের, ‘ল’ অমােঘসিদ্ধির, ‘হুম’ বজ্রসত্ত্বের ও তথাগতের বীজমন্ত্র হল ‘ওম’ আঃ হুম কটু স্বাহা।
বৌদ্ধতন্ত্রে মন্ত্রের সঙ্গে মুদ্রার (হাতের ও আঙুলের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি বা চিহ্নের সাহায্যে মুদ্রাগুলাে দেখানাে হয়, একে সংকেতও বলা যেতে পারে।) যােগও গভীর। ‘অদ্বয়বজ্র সংগ্রহে’ চারটে মুদ্রার কথা বলা আছে যা মােক্ষলাভের উপায় স্বরূপ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে মুদ্রার যে পুথি আছে তাতে একশাে আটান্ন (১৫৮)টা মুদ্রার রঙিন ছবি আছে। তার কোনওটা বজ্র, পদ্ম, ঘণ্টা, শঙ্খ, পুষ্পগুচ্ছ, মালা ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন যন্ত্রসংগীত বাজাবার এমনকী তরােয়াল ইত্যাদির মুদ্রাও আছে। মােট কথা পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করে দুঃখ মুক্তির উপায়গুলােকেই মুদ্রাগুলােতে নির্দেশ করা আছে।
বজ্রযান
মন্ত্রতন্ত্রে শব্দের গােপনীয়তা আর মুদ্রাগুলােতে স্পর্শের গােপনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শের বিষয়টাও অনুষঙ্গ হিসাবে এসে গেল। তখন মন্ত্র ও মুদ্রার সঙ্গে মণ্ডল বা রহস্যময় বৃত্তেরও প্রচলন হল (এই মণ্ডল রচনা হল বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃঢ় সংঘবদ্ধতার প্রক্রিয়ার অনুশীলন। প্রতীকে বােধিমণ্ডল বা বােধিবৃক্ষের বৃত্ত; যেখানে অবস্থান করে স্বয়ং বুদ্ধদেব চরম ও পরম সত্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তাকে অবলম্বন করেই মণ্ডলের সূচনা)। আর যখনই গুঢ়বিদ্যার দ্বারােদঘাটন হল তখন অন্যান্য উপকরণগুলােও একে একে জুটে গেল যেমন— দেবতা, উপদেবতা ও তাদের শক্তি রূপে (স্ত্রী) নারীদেবতা, ভূত, প্রেত, পিশাচ, জাদুবিদ্যা, আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ। ও এর সঙ্গে যুক্ত হল যােগসাধনা (হঠযােগ, লয়যােগ, মন্ত্রযােগ ও রাজযােগ ইত্যাদি)। তখন ধর্মীয় তত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। এইভাবে ছয়টা পারমিতা (perfections) মণ্ডল রচনার প্রতি পদক্ষেপে পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে কুশল-অকুশল রূপে চিহ্নিত হল। আর এর সঙ্গে সুপ্রাচীন তন্ত্রের পঞ্চ ‘ম’-কার (মৎস্য, মদ্য, মাংস, মাৎসর্য, মুদ্রা বা মৈথুন) পরিণামে অনিবার্যভাবে বৌদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হল গুহ্যপূজা। আর ওই সব মূর্তির নাম ‘শম্বর।
বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে দেবতাদের সংস্রব ছিল না। হীনযানীরাও পূজা-আর্চা করতেন না। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চার-পাঁচশাে বছর পরে মহাযানীরাই প্রথম শাক্যসিংহের মূর্তি বিহারে বিহারে প্রতিষ্ঠা করেন। তারা একে নির্বাণের উপায় বলে গ্রহণ করেন। ক্রমে এক এক করে ধ্যানী বুদ্ধেরা এসে আসন পাতলেন। প্রথমে এলেন অমিতাভ, তারপরে অক্ষোভ্য, তারপরে বৈরােচন, তারপরে রত্নসম্ভব, আর সব শেষে এলেন অমােঘসিদ্ধি। ক্রমে এই পঞ্চ তথাগতের পাঁচজন শক্তিরা (স্ত্রী বা সাধন সঙ্গিনী) আবির্ভূত (লােচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা ও আর্যতারিকা) হলেন। বহুকাল অবধি তাদের কোনও মূর্তি ছিল না, যন্ত্রে পূজা চলত। ক্রমে তাদেরও মূর্তি হল। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চশক্তিতে পাঁচজন বােধিসত্ত্ব হলেন, তাদের মধ্যে আবার মঞ্জুশ্রী ও অবলােকিতেশ্বর প্রধান। বর্তমান ভদ্রকল্পে বা কল্পে অমিতাভই প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ আর তার বােধিসত্ত্ব (প্রধান) হলেন—অবলােকিতেশ্বর। তিনি করুণার মূর্তি তাই মহা উৎসাহে জীব উদ্ধার করে চলেছেন। সুতরাং তার পূজা মহাধুমধামের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। ভক্তের উৎসাহে তার হাত, পা ও মাথার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল, তার পূজাও এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তার কারণ এই কল্পে কাউকে বুদ্ধ হতে হলে তার (অবলােকিতেশ্বর) কৃপা ভিন্ন হওয়ার জো নেই। এর সঙ্গে তারাদেবীও নানা রূপ ধারণ করে বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করতে থাকলেন, এরপরে অনেক ডাকিনী, যােগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব ইত্যাদিরা উপাস্য হয়ে দাঁড়াল। ভৈরব ও যােগিনী পূজা পদ্ধতি আছে। আছে বােধিসত্ত্ব ও যােগিনীদের ধ্যান। একে সাধন বলে। এই সাধন পদ্ধতি ও ধ্যান মন্ত্রের সংকলনকে বলে সাধনমালা। এতে দুশাে ছাপ্পান্নটা (২৫৬) সাধন আছে।
এই সব সাধনমূর্তি (গুহ্য মূর্তি বা শম্বর) তৈরিতে বৌদ্ধ কারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখিয়েছেন। একে তাে অশ্লীল মূর্তি, তা আবার ভাল কারিগরের হাতের গুণে তার অশ্লীলতার মাত্রা বহু গুণ চড়ে গেল। যা বিদ্বজ্জনের ভাষায় কামশাস্ত্রের যেখানে শেষ, গুহ্যপূজা সেখান থেকেই শুরু (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। আবার—যত জঘন্য স্বভাবেরই মানুষ হােক না কেন, এই সব গুহ্যপূজার ক্রিয়াকর্ম তার পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। (রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র)। “গুহ্যসমাজ’ বা তথাগত গুহ্যক, চণ্ডমহারােষণ তন্ত্র’, ‘চতুষ্পীঠ তন্ত্র’, ‘সৰ্ব্ববুদ্ধসমাযােগ’, ‘ডাকিনীজাল’, ‘সম্বরতন্ত্র’ ইত্যাদি ইত্যাদি শত শত পুস্তক রচিত হল, আবার এই সব পুস্তকের টীকা টিপ্পনী, পঞ্জিকা ব্যাখ্যা বিবরণ এমনকী প্রয়ােগ পদ্ধতি প্রকরণও তৈরি হল। মূলগ্রন্থ যদি বিশখানা হয় তবে তাদের টীকা-টিপ্পনী পাঁচশত ছিল।
এখানেই শেষ নয়, গুহ্যসিদ্ধি লাভ করতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্রকেও ঘৃণা করা যাবে না। তাও নাকি খেতে হয় সিদ্ধিলাভের জন্যে।
বুদ্ধদেব দেবতা মানতেন না। তার মতে মানুষ নিজের চেষ্টায় চরিত্রশুদ্ধি করে, লােকে যাদের দেবতা বলে, তাদের থেকেও উঁচু যে পরমপদ, যে পদে গেলে জন্ম-জরা-মরণের ভয় থাকে না, সংসারের কোনও চিন্তা থাকে না, যে পদে গেলে মহাশান্তি লাভ করা যায়, সেই পদে মানুষ উঠতে পারবে। এর জন্যে তিনি সাধনায় মধ্যপন্থাকেই (চরম কষ্টকর কৃচ্ছ সাধন ও ভােগবাদ, এই দুইকেই বাদ দিয়ে) বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শিষ্যদের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মালাগন্ধ বিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদির উপদেশ দিয়েছিলেন আর তারই শিষ্যেরা (কালের প্রবাহে ক্রমবিবর্তিত হতে হতে মহাযান → মন্ত্রযান → বজ্রযান→ সহজযান→ কালচক্রযান→ লামাযান বা বােধিসত্ত্বে অবতার ও দলাই লামাযান) শেষে ডাক, ডাকিনী, যােগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপুতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী ইত্যাদির উপাসনা করে। বলা হল—দুষ্কর কঠোর নিয়ম করে সেবা-পূজা করলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ করা যায় না, তারজন্যে চাই সর্বপ্রকার কামােপভােগ, তা হলে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ হবে।
এ ছাড়াও মন্ত্রকে আশ্রয় করে সাধনার যে পথ বা মার্গ তাই—মন্ত্রযান। এখানেও মনুষ্যত্বের বিকাশ, উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভ করা ছিল লক্ষ্য। তাই দেখা যায় মহাযানের দুটো স্পষ্ট বিভাজন—পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়। পারমিতানয়-এর গ্রন্থগুলাে সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতে রচিত, আর মন্ত্রনয়-এর তত্ত্ব অত্যন্ত সুগভীর ও সূক্ষ্ম যা সাধারণ মানুষের কাছে সহজবােধ্য নয়। এই গ্রন্থগুলাে কিন্তু সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এমনকী স্থানীয় শবর, পুলিন্দ ইত্যাদি অমার্জিত ভাষাতেও রচনা করা হয়েছে।
বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে যা আলােচনা করা হয়েছে তা সবই যে মন্ত্রযানেই ঘটেছিল তা ভাবাও ভুল। তন্ত্রের যে বীজ মন্ত্রযানে উপ্ত হয়েছিল, বজ্রযানে তাইই পরিণত রূপে পেয়ে থাকে। এ এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, যার কোন খণ্ডাংশ ঠিক কোন যানের তা নিয়ে তর্ক করা বৃথা, তাই সামগ্রিক ধারাস্রোতে আলােচনাই উপজীব্য।
(মহাযানের) বােধিসত্ত্ব যান ধারণাই বজ্রযানের পূর্বসূরি আর (মহাযানের) যােগবিধি সংবলিত যােগাচার শাখা বজ্রযানের জনক (ড. বিনয়তােষ ভট্টাচার্য)। বজ্রযানীদের ধারণানুসারে আদিবুদ্ধই হলেন— সর্ব সৃষ্টির মূল। কারণ তিনি সর্বব্যাপী। সৃষ্টির প্রত্যেক অণু-পরমাণুতেই তিনি বিদ্যমান। তাই সৃষ্টির প্রত্যেকটা বস্তুই স্বভাবসিদ্ধ শূন্যরূপ, নিঃস্বভাব ও বুদ্বুদ স্বরূপ। কেবল শূন্যই নিত্য, যা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, অবিভাজ্য, অভেদ্য ও ধ্বংসের অতীত—তাই বজ্ৰ৷ এই শূন্যতা পরিবর্তনাতীত, কঠিন ও দুর্ভেদ্য—তাই বজ্র, আর এই শূন্যের রূপকল্পনাই হলেন—আদি বুদ্ধ। তাই তাকে (দেবতা হিসাবে) বলা হয়—বজ্রধর। তার শক্তি—প্রজ্ঞাপারমিতা। তাই তাকে প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগনদ্ধ অবস্থায় (মূর্তিরূপে) দেখতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় তিনি বােধিচিত্ত (শুন্যতা ও করুণা) আর একক অবস্থায়—শূন্য। বজ্রযানীদের সাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে– বােধিচিত্ত লাভ করা। এই অবস্থায় কেবল মহাসুখের অনুভূতি ছাড়া আর কোনও অনুভূতি থাকে না। এই মহাসুখের মধ্যে চিত্তের নিমজ্জনই হচ্ছে (প্রাচীন) বৌদ্ধ ধর্মের পরম নির্বাণ অবস্থার সমার্থক বা তন্ত্রমতে সর্বদা সুখময় অবস্থা। দেহই হচ্ছে এই সাধনার এক ও একমাত্র অবলম্বন। তাই বােধিচিত্ত উৎপাদনে আনন্দের উৎপত্তিস্থল হল—মণিমূল (ষঢ়চক্রের প্রথম স্থান) এ আনন্দ সবরকম প্রকৃতিদোষমুক্ত; আর তার ঊর্ধ্বায়ণই বােধিচিত্ত বা পরমার্থ লাভ। যৌনাচারযুক্ত যােগসাধনার মৈথুন যােগে চিত্তের যে চরম আনন্দঘন ভাব—তাই-ই বােধিচিত্ত (মহাযানের বােধিচিত্ত ধারণা আর তন্ত্রযানে বােধিচিত্তের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন)। এই অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তখন বীজ ও ভ্রূণের মিলনে শুধুই এক অনির্বচনীয় মহাসুখ। –আনন্দ আনন্দ আনন্দ।
বজ্রযানের তন্ত্র সাধনাকেও কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়। যার মধ্যে নিম্নস্তরের তান্ত্রিক আচার যা অভিচার ক্রিয়া নামে বিখ্যাত যথা –মারণ (মৃত্যু ঘটানাে), মােহন (উচ্চারণ করা), স্তম্ভন (অবশ করা), বিদ্বেষণ (বিদ্বেষবশত ক্ষতি করা), উচাটন (তাড়ানাে) এবং বশীকরণ। আর অপর ভাগ হল পরমার্থিক (সম্পূর্ণভাবে সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব)। এ ছাড়াও আছে পঞ্চবােধিসত্ত্ব কুলের বর্ণনা। যেমন— মােহ (বৈরােচন ও তাঁর শক্তি রােচনা বা লােচনা), দ্বেষ (অক্ষোভ্য ও লােচনা), রাগ (অমিতাভ ও পাণ্ডরা) ইত্যাদি। বজ্রযানের সর্বোচ্চ দেবতা হলেন বজ্রসত্ত্ব (বজ্র = শূন্যতা, সত্ত্ব = কেন্দ্রীভূত বিশুদ্ধ সারাংশ)। অর্থাৎ যিনি আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দুই দিক থেকেই শূন্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এদের দেশনা ও গুপ্ত গাথাগুলাে হেঁয়ালিপূর্ণ সংগীতের মাধ্যমেই প্রচারিত হত। একথা চিনা পরিব্রাজকদের (ফা-হিয়েন, হিউ-এন সাং ও ইৎ সিং) ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়। এ ছাড়াও, বজ্রযানে মূল দুই উপাদান—মন্ত্র ও যন্ত্র। মন্ত্র যদি সঠিকভাবে উচ্চারণ করা যায় আর যন্ত্র (মােহিনী প্রতীক) যদি সঠিক ভাবে আঁকা যায়, তা হলে (পূজারিকে) দেবতারা মােহিনী শক্তি দিতে বাধ্য হন। তাই তান্ত্রিক বৌদ্ধ মন্ত্রগুলাের মধ্যে ‘ওম, মণিপদ্মে হুম’ (আহা! মণিই প্রকৃত পদ্ম) অত্যন্ত জনপ্রিয়। সম্ভবত এখানে বুদ্ধের সঙ্গে প্রজ্ঞাপারমিতার, বােধিসত্ত্ব অবলােকিতেশ্বরের সঙ্গে তারার যৌনমিলনের ইঙ্গিত বহন করছে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।
৭ম-৮ম শতাব্দী থেকে শুরু করে ১২শ শতাব্দী অবধি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা ও রাজ-অনুগ্রহ পেয়ে প্রচার প্রসার লাভ করে। তন্ত্রসাধনায় ভারতের বিখ্যাত জায়গাগুলাে হল নালন্দা (এখানে শান্তরক্ষিত তন্ত্রের অধ্যাপক রূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন), ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও জগদ্দল বিহার।
সহজযান
আগেই আলােচনা করা হয়েছে যে, বজ্রযান বিপুল রাজ-অনুগ্রহ ও জনসমর্থন পেয়েছিল। তাই বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ এই ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণের কাছে শূন্য, বজ্র, করুণা, উপায় ইত্যাদি তত্ত্বমূলক কথাগুলো ঠিকমত অনুভূত হত না। তাই তারা এই সব কথাগুলােকে নিজেদের ভাষায় নিজেদের মতাে করে গড়ে নিল; যেমন শূন্যতা হল প্রকৃতি আর করুণা হল পুরুষ। শূন্যতা ও করুণার মিলনে হয় বােধিচিত্ত যা প্রকৃতি ও পুরুষের বা নারী-পুরুষের মিলনে যােগমার্গের এক অনির্বচনীয় সুখকর অবস্থা মহাসুখ।
মহাযানে ‘সাবৃত সত্য’ বা সংসারকে একেবারে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি আর পরমার্থে সত্যকে শূন্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার নিবার্ণও তাে সেই শূন্য, যা অস্তিও নয়, আবার নাস্তিও নয়। তা হলে তা কী? এক অনির্বচনীয় রূপ, যার ধারণা ভাবরূপে হয়, অভাবরূপে হয় না। অর্থাৎ পজিটিভ বা নেগেটিভ রূপেও নয়। ওই অবস্থায় (যােগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা বলেন) শূন্য বিজ্ঞানমাত্র। সহজবাদীরা বলেন, সংসার ও মিথ্যা আবার নির্বাণ ও মিথ্যা। মানুষ নিত্যমুক্ত। পাপ-পুণ্য বলে কিছুই নেই।
আবার নির্বাণ লাভ করা ভীষণ কঠিন, জন্ম-জন্মান্তর ধরে ধ্যান-ধারণা সমাধি করে দশভূমি অতিক্রম করে শূন্যের উপর শূন্য, তার উপরেও শূন্য অতিক্রম করতে হয়। এ তাে সাধারণের কাজ নয়, সহজ কাজ তাে নয়ই।
ভারতবর্ষের পূর্ব দিকেই এই মতবাদের প্রবল প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দেখা যায় (৮ম থেকে ১২শ শতাব্দী অবধি, পাল রাজাদের আমলে)। প্রাকবৈদিক আমলে কৃষি সভ্যতায় যে মাতৃ-সাধনার সূচনা, বৈদিক যুগে ব্রাত্যধর্মের সঙ্গে তা জারিত হয়ে তন্ত্রে এসে পূর্ণতা পায়। তখন তা ছিল একান্তভাবে সম্প্রদায়গত গুহ্যতার অন্তরালে, তারপরে এক সময়ে তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে প্রবেশ করে হিন্দু ধর্মে ও বৌদ্ধ ধর্মে। বৌদ্ধ ধর্মে তন্ত্র চর্চা চরমােৎকর্ষতা লাভ করে।
সহজযানে প্রধান ও শেষ ভূমিকা হল গুরু বা আচার্যের। এরা সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য বলে খ্যাত। চুরাশিজন (৮৪) সিদ্ধাচার্যের কথা ‘কৌলজ্ঞান নির্ণয়’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সহজের’ আক্ষরিক অর্থ হল—সহজাত যা একত্রে জন্মায়। তাই সহজযানের শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত নয়। এ হল স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তির (Intuition) বাস্তব পরিচালন। এখানে একমাত্র গুরুসর্বস্ব মতবাদের সাহায্যেই চরম কাম্যবস্তু লাভ করা যায়। এ ছাড়া সাধনার প্রণালী ও সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।
বৌদ্ধতন্ত্রের শূন্যতা ও করুণার অদ্বয়ভাব যুগনদ্ধ বা সমরস, হিন্দুতন্ত্রে মৈথুন বা কামকলারীতি বা কামকলাবিলাস একই। এই অদ্বয় (হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই তন্ত্রেই) একমাত্র যৌনাচার যুক্ত যােগবিধি দ্বারাই লভ্য। তাই এই সময় থেকেই বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ কমতে থাকে ও পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবিতও হতে থাকে। যােগাচার মতে—বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; তেমনই সহজমতে শুধু মাত্র আনন্দ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই আনন্দই সুখ বা মহাসুখ। সে সুখ নারী ও পুরুষের সংযােগজনিত সুখ। এঁদের মতে চারটে শূন্য আছে। নীচের তিনটে কিছুই নয়, শুধুই আলােকমাত্র; কিন্তু চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর (আপনিই উজ্জ্বল) সেই শূন্যে চিত্তরাজ গিয়ে উঠলেন, তারপরে নিরাত্মা দেবীর সঙ্গে মহাসুখে মগ্ন হয়ে নিঃস্বভাব হয়ে গেলেন। সিদ্ধাই বা সিদ্ধাচার্যেরা সহজের টানে সংস্কৃত নয় প্রাচীন বাংলা ভাষাতেই গান শিখলেন, কাব্য রচনা করলেন। এগুলােকে বলে পদ বা চর্যাপদ, যা প্রাচীন বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম নিদর্শন বলে বিখ্যাত। এদের মধ্যে উল্লেখযােগ্য কয়েকজন হলেন—সরহ, নাগার্জুন, তিল্লোপাদ, নারােপাদ, অদ্বয়বজ্র ও কাহ্নপাদ ছাড়াও লুইপাদ, শবর, ভুসুকু ও কুক্করীপা নামও পাওয়া যায়। সিদ্ধাচার্যেরা যে পদ রচনা করে ধর্মের তত্ত্বকথা প্রচার করতেন তাকে বলে ‘সন্ধ্যাভাষা’, অর্থাৎ আলাে-আঁধারির ভাষা, কখনও রূপকে আবার কখনও বা ঠারেঠোরে বলা। উপর উপর শুনলে এক রকম মনে হয়। কিন্তু গূঢ় অর্থ অন্যরকম, সেখানে দুই অর্থেরই প্রকাশ থাকে; যেমন বােধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখনও তরুলতা সাজানাে আবার কখনও হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলা হয়েছে, আবার শূন্য ও করুণার মিলন গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকার উপমাও দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে, নানা অলংকারে তারা তাদের সহজ মত দিকে দিকে প্রচার করে বেড়াতেন। তখন বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাদুর্ভাব ছিল না। বৈষ্ণবদের মতাে সিদ্ধাচার্যেরাও ছিলেন আখড়াধারী। তাই আখড়াতে তাদের অনেক চেলা থাকত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তারাই ছিলেন দেশের এক রকম কর্তা (সহজ ও জনপ্রিয়তার নিরিখে)। একে তাে তাদের ধর্ম অতি সহজ, তায় সাধারণ মানুষ যা চায় তাই তাঁরা দিতেন, বক্তৃতার ভাষায় নয়। শাস্ত্র বচনে নয়, সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশে নয়, গানে গানে নানা সুরে-ছন্দে বাদ্যের তালে তালে—“বাপুহে সবই তাে শূন্য— সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য, আমি আমি ভাব কেবল এক ধোঁকা মাত্র। তাই ধোঁকার পশরা সরিয়ে ফেল, তখন দেখবে কিছুই কিছু নয়, তাই আনন্দ কর। আনন্দই শেষে থাকবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, আবার শেষেও আনন্দ।’\

-
আবার, গুরুর উপদেশে যা লাভ হয় তা শত সহস্র সমাধিতেও হয় না। তাই (সহজযানে) গুরুর উপদেশ নিতে হয়, ইন্দ্রিয় দমনের চেষ্টা বৃথা, পাপ পরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর ব্রত বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়ম পালনও বৃথা। এতে শরীর শুষ্ক হয় ও নানারকম দুঃখ হয়। তাই দুঃখ হলে মন স্থির থাকে না, আর মন স্থির না থাকলে কখনওই সিদ্ধিলাভ হয় না।
তাই (সহজিয়ারা বলে) পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা বিষয়। বিষয়কেই ভােগ বলে, বিষয়কেই কাম বলে; একে (পঞ্চভােগকে) ত্যাগ করে তপস্যায় নিজেকে পীড়া দিয়াে না। যােগতন্ত্রানুসারে মহাসুখভােগ করতে করতে বােধির সাধনা করবে।
তাই বলা হল— পঞ্চকাম উপভােগ তাে সকলেই করে। তা হলে আবার শাস্ত্র কেন, তার জন্যে আবার ধর্ম কেন? সে তাে সকলে আপনা থেকেই করে। তা হলে আবার গুরু কেন? একটু আছে, তাতে তারা পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু বজ্রগুরু যখন বুঝিয়ে দেন যে, সবই শূন্য, কোনও কিছুরই স্বভাব নেই, তখনই (সহজিয়ারা) পঞ্চকামােপভােগ করেও পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হন না। পরমার্থ সত্যের সঙ্গে মহাসুখলীলাকে এক করে পরম প্রাপ্ত হয়ে সংসারে বিচরণ করাে। তখন আর আত্মপর বােধ থাকবে না।
এইরকম বহু বহু পদ রচনা হতে থাকল শুধুমাত্র বাংলা ভাষাতেই নয়, এ ছাড়াও অসম, ওড়িয়ায় ও মৈথিলিতেও। এঁদের গানের অনেকগুলাে রাগরাগিণী এখন সংকীর্তনে ও অন্যান্য সংগীতে ব্যবহার হতে দেখা যায় যেমন— পটমঞ্জরী, বাড়ী, গুঞ্জরী, শীবরী, কামােদ, মল্লারি, দেশখ, ভৈরবী, মালসী, গবুডা, রামক্রী ও বঙ্গাল রাগ ইত্যাদি। এর ফলে তারা বাংলা ভাষাকে সজীব, সতেজ সরল ও মধুর করে যান। ড. বিধুশেখর ভট্টাচার্য এই সন্ধ্যাভাষায় পদ রচনাগুলােকে আশ্চর্যচর্যা বলে অভিহিত করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে বৌদ্ধ দোহা বা গাথাগুলাে ৮ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়ে প্রচারপ্রসার লাভ করে। তিনি তার গ্রন্থে সিদ্ধাচার্যদের ধারাবাহিক তালিকাও তৈরি করেছেন। তার মতে সরহপাদ ও লুইপাদ দু’জনেই শবরপাদের শিষ্য ছিলেন। আবার সরহপাদ ছিলেন হরিভদ্রের শিষ্য, আর হরিভদ্র ছিলেন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মগ্রন্থের লেখক শান্তরক্ষিতের শিষ্য। সিদ্ধাচার্যেরা বেশিরভাগই নালন্দার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর-এর নাম সকলের কাছে পরিচিত। তিনি তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিব্বত যান। বস্তুত সহজযানের সবকিছুই বর্তমানে তিব্বতীয় অনুবাদে সংরক্ষিত রয়েছে, প্রবােধচন্দ্র বাগচী, রাহুলজি তা থেকেই সম্পাদনা করেছেন। তিব্বতি সংগ্রহে এ রকম তিপ্পান্নটা (৫৩) গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। আগেও আলােচনা করা হয়েছে যে, সহজযানের বৈশিষ্ট্য হল –গুরুবাদ। একমাত্র, যােগ্য গুরুই শিষ্যকে সহজের শিক্ষা দিতে পারেন, তখন তার আর অপ্রাপ্য বলে কিছুই থাকে না। বরং শিষ্যকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়াই গুরুর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। সহজযান গুরুরা মনে করেন প্রত্যেক শিষ্যেরই এক বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রবণতা থাকে। সেই মতাে তারা প্রত্যেক শিষ্যের প্রবণতানুসারে পঞ্চকুলের অন্তর্ভুক্ত করে দেন যেমন— ডােম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। জীবদেহের পাঁচটা মূল উপাদান ও মহাভূত অনুযায়ী প্রত্যেক কুলের স্বরূপ নির্দিষ্ট হয়। আবার এই পাঁচটা কুলই—প্রজ্ঞা বা শক্তির পাঁচটা দিক। তাই সাধক তার সাধনার সময় নিজের (কুলের) বিশেষ শক্তিকে অনুসরণ করেন। এ ছাড়াও (সহজযানে) সাধকের পাঁচটা শ্রেণি বিভাগের কথাও বলা আছে। সহজযান মতে মহাসুখের স্থান হল মস্তিষ্কের একেবারে উপরের দিকে। দেহের ভিতরের বত্রিশটা নাড়ির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শক্তি সেই মহাসুখকর স্থানে পৌঁছায়। এই নাড়িগুলাের বিভিন্ন নাম আছে যেমন ললনা, রসনা, অবধূতী, প্রবণা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণরূপিণী সামান্যা, সুমনা, কামিনী ইত্যাদি। এর মধ্যে আবার ললনা, রসনা ও অবধূতী নাড়িগুলাে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত বৌদ্ধতন্ত্রের অবধূতী ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুষুম্না একই। আবার দেহের ভিতরে পদ্মের পাঁপড়ি বা চক্রের মতাে এদের বিভিন্ন স্থিতিকাল আছে, উর্ধ্বগামী শক্তি সেগুলােকে অতিক্রম করে মহাসুখকর স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। যখন সিদ্ধাচার্যদের গানের কথায়, সুরের টানে, বাজনার তালে-তালে দার্শনিকতার পর্বত ভেঙে সাধারণ মানুষের জীবনছন্দ ‘সহজ’ পথে কলকল্লোলিনী হল, তখন পূর্বভারতীয় সমাজ জীবনের সব ধর্মেই গিয়ে তার অভিঘাত লাগল। মুকুলিত হল—বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেম বা রাধাকৃষ্ণের সহজিয়া প্রেম। যা যুগল প্রেমরূপে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের মুখ্য বস্তু। সহজযানের শেষ পর্যায় হল মহাসুখ; বৈষ্ণবদেরও সর্বোচ্চ প্রেমের (রাধাকৃষ্ণের মিলন) রূপ হল—সহজযান, আবার শাক্তসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে সৃষ্টি হল যােগেরই এক বিশেষ শাখা—হঠযােগ। আবার শাক্ত ও গূঢ় রহস্যময় যােগের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হল— কৌল ও কুলধর্ম (এই সাহিত্যগুলাে নেপালে পাওয়া গিয়েছে)। বৌদ্ধ রহস্যবাদ প্রভাবিত শাক্তধর্মে ‘কুল’ বলতে শক্তি বা নারীকে বােঝায় আর ‘অকুল’ বলতে বােঝায়—শিবকে। আর এর অন্তর্নিহিত শক্তি হল—কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাই কৌল গ্রন্থগুলাের মূল উপজীব্যই হল বৌদ্ধ রহস্যবাদ। এ ছাড়াও নাথ সাহিত্য বা ধর্ম, অবধূত, সহজিয়া ও বাউল ধর্ম সাহিত্যের মধ্যেও গূঢ় বৌদ্ধ ধর্ম মিশে গেল। কিন্তু নাথ সম্প্রদায় ক্রমশ হিন্দু সমাজভুক্ত হয়েও এক আলাদা ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মৎস্যেন্দ্রনাথই সিদ্ধাই লুইপাদ। এ ছাড়াও গােরক্ষনাথ, মীননাথ, ভর্তৃহরি, চৌরঙ্গীনাথ (এর নামানুসারেই কলকাতার চৌরঙ্গী বা ধর্মতলা) ছাড়াও নয়জন নাথ আচার্যের নাম সাহিত্যে পাওয়া যায়। এক সময়ে উত্তর ও পূর্ব বাংলায় নাথধর্মের প্রাবল্যও ছিল। এদের জনপ্রিয় গাথাগুলােকে কেন্দ্র করে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাথ সম্প্রদায়কে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মেরই আর এক শাখা বলে মনে করেন, যদিও তাদের মধ্যে গােরক্ষনাথ ভর্তৃহরি এঁরা শুদ্ধশৈব ছিলেন। আর আজও এঁদের (যােগী অপভ্রংশে যুগী) গােত্র শিব। ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে বাংলার নাথেরা প্রাচীন আজীবক সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও ছিল অবধূত সম্প্রদায়। এরাও সিদ্ধাচার্যদের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য নিত্যানন্দ মহাপ্রভুও একজন অবধূত ছিলেন। সহজিয়ারা বাংলায় চৈতন্যদেবের অনেক আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই চৈতন্যদেব সহজিয়াদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেমন বুদ্ধদেব প্রভাবিত হয়েছিলেন সাংখ্য দর্শনের। আবার শ্রীশ্ৰীশঙ্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে পণ্ডিতমহলের অভিমত। তাই সহজযানই পরবর্তীকালে বাংলায় সহজিয়া ধর্মের রূপ নেয়। সহজিয়া ধর্মের আদি কবি হলেন বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁর লেখা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ বৌদ্ধ সহজযানের মূল সূত্রগুলাে দেখতে পাওয়া যায়।
প্রসঙ্গত বলা যায় সহজযানের সিদ্ধাচার্যেরা প্রচার করতেন যে, ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং নাকি তার স্ত্রী গােপার সঙ্গে সহজসাধনা করতেন; তেমনই আবার সহজিয়া মতে—শ্রীচৈতন্যদেবও স্বয়ং তার স্ত্রী (শক্তি)-র সঙ্গে সহজ সাধনা করেছিলেন।
পরিশেষে বলা প্রয়ােজন যে, সিদ্ধাচার্যের ক্ষমতার প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে, আকর্ষণে ও প্রচার চমৎকারিত্বে দেশসুদ্ধ লােক আনন্দময়তার স্রোতের প্লাবনে ভেসেছিল, পরবর্তীকালে সে মাতনের ফল যে ভাল হয়নি—ইতিহাসই তার একমাত্র সাক্ষী। যে বুদ্ধদেব ও তার ধর্ম একদিন পূর্ব ভারত থেকে উদিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলােকিত করেছিল, সেই পূর্বদিগন্তেই তা অস্তমিত হল।
সহজযান অস্তমিত হলেও তারা যে সহজধর্মের সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন সে ধর্ম আজও (প্রবহমান) চলছে, তবে তার রং রূপ একেবারেই বদলে গিয়েছে। তখন সহজযানীরা নিজেরাই সহজভাবের মহাসুখে (যুগনদ্ধ ক্রীড়ায়) মত্ত থাকতেন, আর এখন সহজিয়ারা দেবতাদের সহজভাবের (যুগনদ্ধক্রীড়া) মূর্তি দেখেই আনন্দে বিভাের হয়ে অশ্রুসিক্ত হন।
কালচক্রযান
বিশ্বে মহাবিশ্বে বা পৃথিবীতে কোনও কিছুই স্থির নিশ্চল বা অপরিবর্তনীয় নয়, সবকিছুই পরিবর্তনশীল। বৌদ্ধ ধর্মও সেই একই নিয়মে কালের প্রভাবে ক্রমপরিবর্তিত হয়ে চলে কালচক্রযানে। খুব সম্ভবত এই শাখার উদ্ভব ভারতবর্ষের বাইরে শম্ভল নামে কোনও এক জায়গায়। কথিত আছে দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে মধ্যভারতে শ্রীকালচক্রতন্ত্রের প্রবর্তন হয়ে একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে তিব্বতে পৌঁছায়। বাংলায় তা প্রচারপ্রসার লাভ করে পাল যুগে। প্রসঙ্গত বলা যায়, যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম এক সময়ে ভারতের মাটিতে জন্ম নেয় তা নেপাল ও কাশ্মীরে ভয়াল-ভয়ংকর রূপ নেয়। আর সেই সময়েই বহু দানবীয় কালচক্র মূর্তির প্রচলন হয়। এমনকী বুদ্ধদেবেরও দানবীয় রূপ ও তার সাধনার সৃষ্টি হয়। বিদেশি পণ্ডিতদের মতে কালচক্র হল ধ্বংসের চক্র, কালচক্রযান এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, কাল হল সময়। বৌদ্ধ গ্রন্থসূত্রে জানা যায় স্বয়ং বুদ্ধদেব এই কালচক্রের দেশনা করেছিলেন। তার মতে জগৎসংসার দেহের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছে, সময় বা কালের বিভাজন বা পুনর্বিভাজন (দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস ও বছর ইত্যাদি) যা প্রাণবায়ুর দ্বারা আবর্তিত। বলা হল সবকিছুর উৎপত্তি এই কালচক্রে যেমন ত্রিকাল (বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ), ত্রিকায় (সদভােগকায়, নির্মাণকায় ও ধর্মকায়) কালচক্রেই নিহিত। এ হল শূন্যতা ও করুণার প্রতীক, যার উৎপত্তি লয় বা ক্ষয় নেই। এখানে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মিলন ঘটেছে তাই সব কিছুর উদ্ভব এই কালচক্রে। তাই কালচক্রানীদের উদ্দেশ্য হল এই সতত পরিবর্তনশীল কালচক্রকে প্রতিরুদ্ধ করে নিজেদের তারও উপরে স্থাপন করা। তাই এখানে প্রাণ অপানের নিয়ন্ত্রণের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে ও ফলাফলের কথাও বলা হয়েছে। এদের মতে যােগসাধনার দ্বারা শরীরের পঞ্চবায়ুকে আয়ত্তে আনতে পারলে প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ হয় ও কালকে জয় করা যায়। তাই এদের সাধনবিধিতে জ্যোতিঃশাস্ত্র বা জ্যোর্তিবিদ্যার বহু তথ্য রয়েছে।
কালচক্রতন্ত্রে আদিবুদ্ধের ধারণারও উদ্ভব ঘটে। একে শিখার সাহায্যে পূজা করা হয়। কারণ আগুন যেমন শাশ্বত, ঔপপাতিক ও স্বঅস্তিত্বশীল— আদিবুদ্ধও তাই। নেপালে আদিবুদ্ধের ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। অগ্নিশিখারূপে আর বৌদ্ধদেবী মঞ্জুশ্রী সেই শিখাকে সংরক্ষণ করেন এক মন্দিরে যা বর্তমানে নেপালে স্বয়ম্ভু চৈত্য বলে পরিচিত।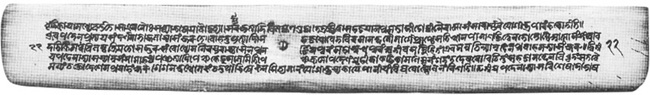
-
আদিবুদ্ধের ধারণার উদ্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশগুলাে থেকে। থেরবাদীরা মনে করেন বুদ্ধদেব ইচ্ছা করলেই এক পূর্ণ কল্প বেঁচে থাকতে পারতেন। মহাযানীরাও মনে করেন একজন বুদ্ধ কোটি কোটি কল্প জীবিত থাকতে পারেন। আবার লােকাত্তরবাদীরা মনে করেন শাক্যমুনি সশরীরে পৃথিবীতে আবির্ভূত না হলেও তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এ ছাড়াও বজ্রযান সম্প্রদায়ের মুখ্য দেবতা বজ্রধর-ই আদিবুদ্ধ, যিনি শুন্যের মূর্তরূপ। আর তার শক্তি থেকেই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের উদ্ভব। আদিবুদ্ধ যদিও সর্বজনপূজ্য কিন্তু তার কোনও প্রার্থনা মন্ত্র নেই। আদিবুদ্ধের মানুষী রূপই হল বজ্রধর। একে নানা রূপে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ভয়ংকর রূপে, ত্রিমুখবিশিষ্ট রূপে, শক্তিকে আলিঙ্গনাবদ্ধরূপে ও তিব্বতি মূর্তিতে বজ্রধর ও বজ্রসত্ত্ব একাত্ম রূপে। বজ্রধর যখন একা তখন বজ্র তার ডান হাতে ও বাম হাতে ঘণ্টা। আর তার দুই হাত বজ্রহুংকার মুদ্রায় বুকের দু’পাশে কোনাকুনি ভাবে থাকে, আর তিনি তার শক্তি বা সঙ্গিনীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবস্থায়—প্রজ্ঞাপারমিতা। বজ্ৰধর হলেন শূন্যের প্রতিমূর্তি, আর প্রজ্ঞাপারমিতা হলেন—করুণার।
মহাপণ্ডিত অভয়াকর গুপ্ত কালচক্রযানের অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এতে বােধিসত্ত্ব ছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীদের যেমন দশ দিকপাল ও তাদের শক্তিরা, বিভিন্ন জীবজন্তু ও পাখির মুখবিশিষ্ট দেব-দেবীরা ছাড়াও ডাকিনী, লামা, খণ্ডরােজা ও রূপিণীদের তান্ত্রিক ক্রিয়া-আচার ছাড়াও হিন্দু দেবদেবী যেমন সরস্বতী, গণপতি ইত্যাদিদের স্থানও সাধনমালায় নির্দিষ্ট আছে। এ ছাড়াও আছে দ্বাদশ পারমিতা ও বৌদ্ধ ধর্মে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রজ্ঞাপারমিতা।
ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের ধারা কালচক্রযানে এসেই পরিসমাপ্ত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে পূর্ব ভারতে একদিন স্বয়ং বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন ও তার জ্ঞানের আলােকবর্তিকায় সমগ্র পৃথিবী আলােকিত হয়েছিল, সেই পূর্ব ভারতেই বৌদ্ধ ধর্ম (ভারতবর্ষে) অস্তমিত হল। ৮ম শতাব্দী থেকেই এর সূচনা হয়ে মধ্যযুগে অর্থাৎ ত্রয়ােদশ শতাব্দীর প্রথমেই এর (বৌদ্ধ ধর্মের) প্রায় অবলুপ্তি ঘটে। এর কারণ ও সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত আছে। তবে একথা সত্যি যে, শেষ অবস্থায় বৌদ্ধরা বড়ই কদর্যচারী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়েছিল, এমনকী তারা ধর্মের যে ব্যাখ্যা করেছিল তাও অতি কদর্য। যে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে সারা পৃথিবী আলােড়িত হয় তার সূতিকাগারেই সেই ধর্মের রং রূপ সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়ে সিদ্ধিলাভের নামে উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্ত, অকর্মণ্য ও নিবীর্য হয়ে নিজেরা তাে বটেই দেশটা সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়েছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের ঘৃণা করত। রাজঅনুগ্রহ বন্ধ হয়ে গেল। মুসলমান আক্রমণে পূর্ব ভারতের বৌদ্ধবিহারগুলাে নিশ্চিহ্ন হল ও শত শত বৌদ্ধভিক্ষুর প্রাণ গেল। বাংলায় শৈব-যােগীদের সঙ্গে বৌদ্ধদের শত্রুতা ও শৈব-যােগীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার। তবে সারা ভারতে একই সঙ্গে এই ধর্মীয় অবলুপ্তি ঘটেছিল কখনওই একথা বলা যায় না। তবে এই অবলুপ্তির কারণ হিসাবে পণ্ডিতমহল যে ক’টা বিষয়ের কথা বলে থাকেন তা হল ১) হিন্দুধর্মের নবশক্তিলাভ, ২) অবৌদ্ধ শাসকদের প্রতিকুলতা, ৩) মুসলমানি আক্রমণ, ৪) বৌদ্ধসংঘে অনৈক্য, ৫) ধর্মবিশ্বাসের অধঃপতন (degradation), ৬) বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতিকরণ, ৭) বৌদ্ধ ধর্মে দুঃখবাদ, ৮) নৃপতিদের পৃষ্ঠপােষকতা হ্রাস ও বন্ধ হয়ে যাওয়া ও ৯) পরিশেষে হিন্দুদের সঙ্গে একাত্মতা (ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ) ও মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরকরণ।
লামাযান বা লামাধর্ম
ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তন কালচক্রযানে এসেই স্তব্ধ হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ হল পাল যুগের অবসানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মও প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে যায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের সজীবতা প্রবাহমান দেখা যায় তিব্বতে; তবে এ দেশের বৌদ্ধ ধর্মের ধারা এই সময়কাল থেকে শুরু করে আজও ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ধারা থেকে অনেকটাই আলাদা। তাই হেঁয়ালি-কথা না বাড়িয়ে বরং তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের সূচনাকাল থেকে বর্তমানের লামাযানে পরিণতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের পরিচয়টা একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।
পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি ও বরফের দেশ বলা হয় তিব্বতকে, যার পূর্বদিকে (পর্বতের অপর পারে) সুপ্রাচীন চিন সভ্যতা আবার হিমালয়ের অপর দিকে সিন্ধু সভ্যতা। নৃতত্ত্ববিদদের মতে বহু বহু প্রাচীন কাল থেকেই এখানে মানুষের বসবাস। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে অবধি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এদেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসও প্রায় তমসাচ্ছন্ন। সম্ভবত তিব্বতের দুরধিগম্যতা ও প্রতিকূল আবহাওয়াই এরজন্যে মূলত দায়ী।
৭ম শতাব্দীতে নম্-রি-স্রোঙ্-সন মধ্য তিব্বতে এক শক্তিশালী শাসকরূপে অর্ধসভ্য জনজাতি ও গােষ্ঠীগুলােকে একত্রিত করে এক পরাক্রমশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরে তার ছেলে স্রোঙ-সন-গম-পাে রাজা হয়ে আজকের সমগ্র তিব্বতকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসেন। তারপরে সুসভ্য নেপাল দেশ আক্রমণ করলে সেখানকার রাজা নিজের মেয়ের সঙ্গে তিব্বতরাজের বিয়ে দিয়ে সীমান্ত বিরােধ চিরকালের জন্যে মেটান। এর দু’বছর বাদে (তিব্বতরাজ) তিনি আবার চিনদেশ আক্রমণ করলে সেখানকার রাজাও কন্যাদান করেন। এই দুই রানিই নিজেদের বৌদ্ধ ধর্মে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। যখন তারা তিব্বতে আসেন তখন ও দেশ থেকে সঙ্গে করে বুদ্ধমূর্তি ও মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আসেন (এই মূর্তিগুলাে আজও লাসায় সংরক্ষিত আছে)। এই দুই রানির প্রভাবেই রাজার বৌদ্ধ ধর্মে মতি আসে। বর্তমানে লাসায় এই রাজা ও তার দুই রানিকে অবলােকিতেশ্বর (রাজাকে) সবুজ তারাদেবী (নেপালি রানিকে) ও শ্বেততারাদেবী (চিনা রানিকে) জ্ঞানে পূজা করা হয়। তিব্বতের সভ্যতার সূচনা এই সময়কাল থেকে বলেই ধরা হয়। এতদিন অবধি তিব্বতের কোনও নিজস্ব বর্ণমালা ছিল না। রাজঅনুগ্রহে থােঙ-মি সম্ভোট নামে এক প্রাজ্ঞকে কাশ্মীরে পাঠিয়ে সে দেশ থেকে তিব্বতি ভাষার জন্যে লিখিত বর্ণমালার ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তিত রূপ (৩৪ অক্ষরের বর্ণমালা) প্রবর্তন করেন, আর ভারত, নেপাল ও চিন দেশ থেকে বহু জ্ঞানগ্রন্থ ও জ্ঞানীলােককে তিব্বতে নিয়ে আসেন ও দেশের বহু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লােককে এই তিন দেশে পাঠিয়ে শিক্ষিত করে তােলেন। এ ছাড়াও লাসায় এগারােতলা বিশিষ্ট সুবিখ্যাত পােটালা বা পােতালা প্রাসাদ তৈরি করান। তখন বৌদ্ধ ধর্ম জাতীয় ধর্মের রূপ নেয় ও জাতিটাও এক ঝটকায় এক সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়। একটানা কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর (৬৫০ খ্রি.) তিনি মারা যান।
এর পরে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ও সামগ্রিক সভ্যতা আদিম ‘বােন’ বা বােন-পা ধর্মের প্রভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বেশ মলিন হয়ে পড়ে। কোনও ধর্মে সমস্ত প্রাকৃতিক (নদী, পাহাড়, হ্রদ, ভূমি ইত্যাদি) জিনিসের অধিদেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে জীববলি, নরবলি ইত্যাদি বীভৎস প্রথা প্রচলিত ছিল। তা না হলে এই সব দেবতারা খুব সহজেই কুপিত হয়ে ঝড়ঝঞা, খরা, বন্যা ও মহামারীর সৃষ্টি করেন। এ ছাড়া তাে দেবতারা বিদেশি ব্যক্তি বস্তু বা ভাবধারাকেও সহ্য করতে পারেন না। তাই বহু বৌদ্ধ দেশ থেকে বিতাড়িত হন।

-
এরপরে একসময়ে বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিত (৮ম শতাব্দী) ও তার ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভবকে (ইনি নালন্দার আচার্য ছিলেন) তিব্বতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে শুরু হয় তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের নবজাগরণ। প্রতিষ্ঠিত হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম বা তন্ত্রযান। আজও শান্তরক্ষিত, বােধিসত্ত্বরূপে ও পদ্মসম্ভব বুদ্ধদেবের সমকক্ষরূপে ‘অমূল্য গুরু’ নামে পূজিত হন। এ ছাড়াও আচার্য কমলশীলকেও তিব্বতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরা নেপাল, চিন ও ভারতবর্ষ থেকে বিপুল বৌদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিব্বতে গিয়ে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করান। এই কাজের জন্যে ভারতবর্ষ থেকে বহু বৌদ্ধাচার্য তিব্বতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে জিনমিত্র, শীলেন্দ্রবােধি, সুরেন্দ্রবােধি, প্রজ্ঞাবর্মণ ও বােধিমিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা নাগার্জুন, বসুবন্ধু ইত্যাদি বৌদ্ধ দার্শনিকদের গ্রন্থগুলােকে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন।
এরপরে ১০ম শতাব্দীতে এক বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা এসে তিব্বত থেকে বৌদ্ধ ধর্মের মূলােচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার রাজত্বকাল বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এক লামা গুপ্তঘাতকের হাতে তিনি নিহত হলে তিব্বতে আবার বৌদ্ধ ধর্মের সুদিন ফিরে আসে। একাদশ শতাব্দীতে এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে বৌদ্ধাচার্যদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়, এরমধ্যে ভারতবর্ষের অতীশ দীপঙ্কর বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন অন্যতম। তার পৃষ্ঠপােষকতায় তিব্বতে কালচক্রযান (সময় ও কালবিভাগ গণনার মতবাদ) প্রসারলাভ করে। এইসময়ে কালচক্রযান তিব্বতে বিশেষ সমাদর পায়। এর পরে মন্ত্রযান ও কালচক্রযানের সংমিশ্রণে বজ্রযানের উদ্ভব হয়। বজ্রাচার্যদের লক্ষ্য ছিল কৃচ্ছসাধন ও তান্ত্রিক বামাচারের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করা ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী বা সিদ্ধাই হওয়া। এ ছাড়াও মন্ত্রযান ও কালচক্রযানের সংমিশ্রণে তিব্বতে লামাধর্মের উৎপত্তি হয়। তিব্বতি ভিক্ষুর নাম লামা। তিব্বতের জনসংখ্যার প্রায় একের পাঁচ ভাগই এই লামা শ্রেণির। এর মধ্যে আবার প্রাচীন বা আদিম বােন-পা ধর্ম ছাড়াও বহু পৌরাণিক কাহিনি, প্রাচীন মতবাদ ও বিশ্বাস ও দেশের কুসংস্কার মূলক ভৌতিক ক্রিয়াকলাপও এসে মিশেছে। তাই তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্ম বা লামাধর্ম কিন্তু মূল বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারী নয়। মূলত এই ধর্ম ৭ম থেকে ১২শ শতাব্দী কাল অবধি উত্তর ভারতে প্রচলিত যে বৌদ্ধ ধর্ম তারই তিব্বতি রূপ। এদের পৌরােহিত্য-প্রধান জনসমাজও আলাদা ভাবে গঠিত। আবার এই লামাধর্মও বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাই তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতিতে পার্থক্য থাকলেও মূল ধর্মকে জনপ্রিয় করার জন্যে উপকরণগুলাে কিন্তু প্রায় একই। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিহার আছে, আছে পােশাক-পরিচ্ছদ। তবে এদের আলাদা করে চেনা যায় মাথার টুপির রং দিয়ে। যেমন নিঙ-মা-পা হল ‘লাল টুপি’ সম্প্রদায় আর গেলুপা হল ‘হলদে টুপি’ সম্প্রদায়। তিব্বতে এই দুই সম্প্রদায়ই সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান। আচার্য পদ্মসম্ভব থেকেই এই দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। এ ছাড়াও শাক্য-পা, গুরু-গৎ-পা, বাহু-দম-পা (অতীশ দীপঙ্কর প্রতিষ্ঠিত), দিকুংপা ছাড়াও করমাপা (সিকিম, দার্জিলিং ও তিব্বত), দুগপা (ভুটান ও লাদাখে) অস্তিত্বশীল। বর্তমানে তিব্বতিদের প্রধান দলাই লামা বা দলৈলামা ও পাঞ্চেনলামা বা পঞ্চনলামা। এদের একজনের রাজধানী লাসায়। আর অন্যজনের ভারতের প্রান্তসীমার কাছে তাসি-লুপাে শহরে। দলাই লামা আদিবুদ্ধের প্রতিনিধি। তাকে বৌদ্ধ ধর্ম জগতের পােপ বলাও অসঙ্গত হবে না। দলাই শব্দটা মােঙ্গলীয়, যার অর্থ মহাসমুদ্র অর্থাৎ যিনি মহাসমুদ্রের মতাে প্রশান্ত ও জ্ঞানগম্ভীর। জনমানসের বিশ্বাস এরা বুদ্ধাবতার তাই এরা মৃত্যুহীন, এদের আত্মা ‘অবতার পারম্পর্যবাদ’-এর মাধ্যমে কোনও শিশু বা বালকের শরীরে প্রবেশ করে, তখন এই বালককে চিনে নেওয়াটাই হয় এক প্রধান সমস্যা। এ ছাড়াও কখনও কখনও মৃত লামা মৃত্যুর আগে বলে যান কোন কুলে তিনি আবার জন্মাবেন বা কখনও দুই লামার (দলাই ও পঞ্চন) মধ্যে যিনি জীবিত তিনি মৃত লামার উত্তরাধিকারী নির্দেশ করে দেন। আবার কখনও বা দৈবজ্ঞের পরামর্শও নেওয়া হয়। শাস্ত্রের বিধান ও অন্যান্য লক্ষণ দিয়ে ভবিষ্যৎ মঠাধিকারী লামা নিরূপণ করা হয়ে থাকে। নব-অবতার আবিষ্কৃত হলে লামা মণ্ডলীর কাছে তার পরীক্ষা হয়, তিনি মৃত লামার গ্রন্থ, বস্ত্র চিনতে পারেন কি না বা তার পূর্ব জীবনের ঘটনা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন কি না। এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই তিনি মহালামারূপে মহাধুমধামের সঙ্গে অমিতাভ বুদ্ধের অবতার রূপে পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। এরাই তিব্বতের যাজকতান্ত্রিক পুরােহিত প্রধান ও রাষ্ট্রনায়ক রূপে ‘রিনপােচে’ বা প্রভুত্বের মধ্যমণি।
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ‘ছােঙ-থা-পা’-র নেতৃত্বে লামাধর্মের সংস্কারের প্রচেষ্টা শুরু হয় (ভূত-প্রেত, তন্ত্রমন্ত্র, জাদুবিদ্যা, আচার-সংস্কার ও বহু বহু দিনের জমে থাকা নানা ধরনের কুসংস্কারকে ধীরে ধীরে সংস্কৃত করে)। অন্যান্য সম্প্রদায়ের শত্রুতা ও কলহ-বিবাদ মিটিয়ে গেলু-পা (লাল টুপি) সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহের পরে ১৪১৯ খ্রি. তিব্বতে দলাই লামার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতে পুরােহিত রাজের নাম ও পদবি—দলাই লামা (গেলু-পা সম্প্রদায়ের, আজও গেলু-পা সম্প্রদায়ের লামারাই সর্বপ্রধান)।
এ ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্ম প্রধান বিভিন্ন দেশে, অগ্রগণ্য লামা বা মহালাম আছেন যেমন—মঙ্গোলিয়ায় কুরূণ, তাতারে কুকু, পেকিনে মহালামা ও ভােটদেশে ধর্মরাজ।
তিব্বতের ধর্মীয় ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মের ও সাহিত্যের যে চরম উন্নতি হয়েছিল সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়ােজন। আগেই আলােচনা করা হয়েছে যে, লামাধর্ম এ দেশে বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে শাক্যপা সম্প্রদায় ছিল ১৩শ শতাব্দীতে সর্বপ্রধান সম্প্রদায়। চিনদেশের মােঙ্গলজাতীয় সম্রাট কুবলাই খান (ইনি চেঙ্গিস খানের বংশধর) তিব্বত অধিকার করেন। এরপর তিনি তার অনুগামীদের নিয়ে সবাই মিলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন ও শাক্যপা সম্প্রদায়ভুক্ত হন। তখন রাজপ্রভাব ও পৃষ্ঠপােষণায় শাক্য মঠাচার্যকে লামাধর্মীয় সম্প্রদায়গুলাের মধ্যে সর্বপ্রধান গুরু বলে ঘােষণা করে, তাকে তিব্বতের প্রধান শাসক বলে নির্বাচন করা হয়। যার ফলে পরবর্তী পঞ্চাশ বছর শাক্যবিহারের অধ্যক্ষরাই তিব্বতের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান পুরুষ বা রাষ্ট্রগুরু ছিলেন। ফলে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়গুলােকে যেমন যথেচ্ছ নির্যাতন করেছিলেন; তেমনই আবার লামাধর্মের যে প্রধান মহাগ্রন্থ তা বহু পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে মােঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ ও সংকলনও করেছিলেন। এ ছাড়াও তিব্বতি লিপিতে মােঙ্গলীয় ভাষার লেখ্য রূপও দিয়েছিলেন।
১৪শ শতাব্দীতে মিঙবংশীয় চিনা সম্রাটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তারই মদতে অন্যান্য লামা সম্প্রদায়গুলাে শাক্যপা সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অরাজকতার সৃষ্টি করেন। পরিণামে লামাধর্মের নৈতিক অধােগতি তলানিতে এসে ঠেকে।
তিব্বতের রাজনৈতিক ইতিহাস যতই অস্থির হােক না কেন, সেখানকার ধর্মীয় সাহিত্যগত ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে চরমােৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল তা সত্যিই বিস্ময়ের কথা। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শাক্যপা সম্প্রদায়ের মহাপণ্ডিত Bu-Ston-এর কথা দিয়ে। তিনি তিব্বতীয় ইতিহাস সম্পর্কে নির্ভরযােগ্য তথ্য লিখে রেখে গেছেন। এ ছাড়াও সুসংবদ্ধভাবে ভারতীয়, প্রধানত বৌদ্ধ, এ ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থাবলির তিব্বতি ভাষায় অনূদিত দুটো বিশাল-মহাবিশাল সংগ্রহ সংকলন করেছেন Kanjur ও Tanjur। এই দুই কথার তিব্বতি ভাষায় অর্থ হল Kanjur বুদ্ধবাণী সম্ভার বা অন্য গ্রন্থাবলি আর Tanjur—অনূদিত ধর্ম বা বৌদ্ধাচার্যদের নির্ধারিত মার্গ।

-
বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যা গ্রন্থবিশেষ। বৌদ্ধ ধর্মের সর্বস্ব নিয়ে এই দুই সংকলন (অনুবাদ) গ্রন্থমালায় Kanjur -এর গ্রন্থ সংখ্যা ১১৮০টা ও Tanjur -এর গ্রন্থ সংখ্যা তিনহাজার চারশাে আটান্ন (৩৪৫৮) খানা। এই দুইয়ে মিলে মহা-মহা গ্রন্থমালার গ্রন্থ সংখ্যা চার হাজার ছ’শাে চৌত্রিশটি (৪৬৩৪)। এ ছাড়াও আছে আরও দুটো বিষয়ের গ্রন্থ—মন্ত্রগাথা বা প্রার্থনা ও বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থের বিষয়সুচি, এই সব মিলে হয় চার হাজার পাঁচশাে ছেষটি (৪৫৬৬) গ্রন্থ।
এইসব গ্রন্থগুলাে কেবলমাত্র বৌদ্ধসাহিত্যেরই অনুবাদ নয়, এর মধ্যে আছে সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, ব্যাকরণ, বিভিন্ন কোষগ্রন্থ কাব্য, অলংকার, ছন্দ, আয়ুর্বেদ, মূর্তিশিল্প বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি। এ ছাড়াও দেখা যায় বহু ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ, যা এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তিব্বতে তার অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে। তিব্বতি গ্রন্থের অনুবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এগুলাে অত্যন্ত মূলানুগত। তাই ভারতীয় পণ্ডিতমহল তিব্বতি অনুবাদ থেকে বহু মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। তাই মনে হয় এই মহাসংকলন গ্রন্থমালা সংগ্রহ ভারতবর্ষের কাছে তাে বটেই, সারা পৃথিবীর বৌদ্ধসাহিত্য ও শাস্ত্রপ্রেমী মানুষদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

